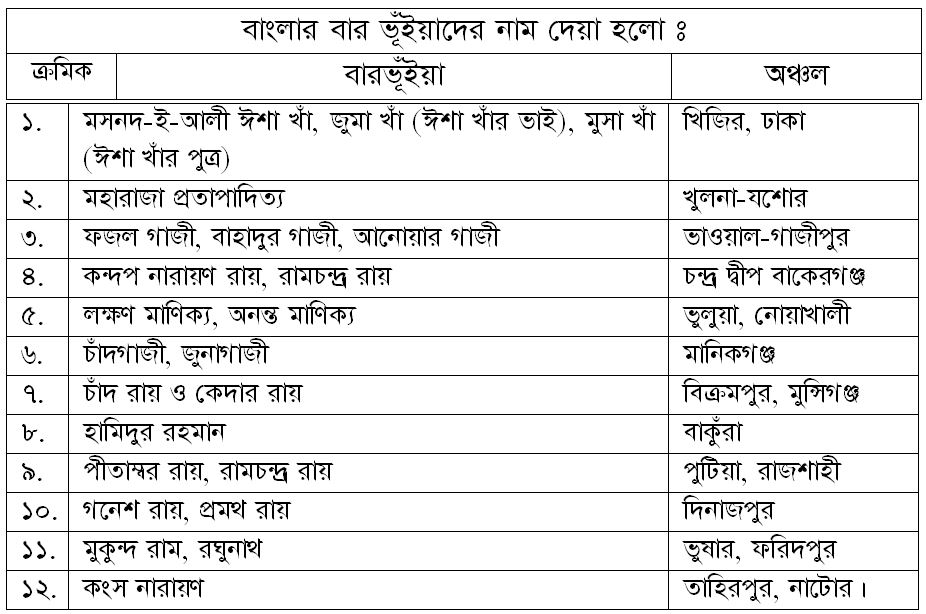৪০(চল্লিশ) লক্ষ বছর আগের মানুষ। বিবিসি ঃ জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা ইথিওপিয়ার মনুষ্য প্রজাতির একটি অংশের কিছু হাড়ের যে অংশ আবিস্কার করেছেন তা প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ বছরের পুরানো বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর আগে ১৯৭৪ সালে যে মানুষের জীবাশ্ম আবিস্কৃত হয়েছিল এতদিন পর্যন্ত সেটিকেই প্রাচীনতম বলে মনে করা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাদের অনুমান সদ্য আবিস্কৃত এ প্রজাতির মানুষ দু’পায়ে সোজা হাঁটতে সক্ষম ছিল। ৩০(ত্রিশ) লক্ষ বছর আগে মানুষ আসছে পৃথিবীতে এবং আজকের মানুষ প্রায় ৭৫(পঁচাত্তর) হাজার বছর আগে। কেমব্রিজের অ্যাংলিয়া রাসকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিও জেনেটিকসের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক ড. পিটার ফরস্টার বলেন, পূর্ব আফ্রিকায় এক লাখ ৯৫ হাজার বছর আগে হোমোস্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানবের উদ্ভব ঘটে। আর জায়গাটি ছিল সম্ভবত বর্তমান ইথিওপিয়ার ওমো নদীর তীরবর্তী কোনো অঞ্চল। ৩১,৭০০ বছর আগে পৃথিবীতে কুকুর ছিল ২০০৮ সালের ২৮ অক্টোবর, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল দাবি করেছে। এরা তখন ঘোড়া, হরিণ খেয়ে বেঁচে থাকত। ১০,০০০ হাজার খৃষ্টপূর্বে পৃথিবীতে কৃষি-কাজের প্রচলন শুরু হয়। পৃথিবীর কৃষি নির্র্ভর আদিম জীবনের যুগ অতিবাহিত হয় ১০(দশ) হাজার বছর ধরে। ১০,০০০(দশ হাজার) বছর পূর্বে সোমালিয়া, বেবীলন-ইরাক সভ্যতা আরম্ভ।
বিশ্বের প্রথম ধান কবে কখন কোথায় মানুষ সর্বপ্রথম ধান বা চালের ব্যবহার শুরু করে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া দায়। ধারণা করা হয়, সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই চালের ব্যবহার শুরু হয়। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগে উত্তর থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ চীন উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রথম ধান চাষ হয়-বিভিন্ন গবেষণায় এ রকম তথ্যই পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রথম ফুটবল কোথায় সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা হয় তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। তবে বলা হয়ে থাকে, ফুটবলের সূতিকাগার হলো প্রাচীন চীন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ফুটবল খেলার প্রবর্তন হয়। প্রাচীনকালে মূলত দুই দল লোক একে অন্যকে আক্রমণের মহড়া হিসেবে ফুটবল খেলত। প্রাচীন ফুটবলে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতাব্দীর কিছু আগে বিনোদন হিসেবে বর্তমান ধারার ফুটবল খেলার সূত্রপাত হয়। ৭(সাত) হাজার বছরের ইতিহাস জানি মাত্র আমরা, যখন থেকে মানুষ তার ইতিহাস লেখে। গাছের বয়স ৭(সাত) হাজার বছর।
খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ সালে ইউরোপ মহাদেশের গ্রীসে প্রথম রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাফেরা শুরু করে। ৫(পাঁচ) হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর সভ্যতা আরম্ভ। ৪৬০০-৪৮০০ খৃষ্টপূর্ব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লাভ। (সাড়ে ৬ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লাভ।) জানাগেছে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও শ্লোভাকিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিদর্শনগুলো আবিস্কৃত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে ১৫০টির বেশি বিশালায়তনের উপাসনালয়। ধর্মীয় প্রয়োজন থেকে কোন জনগোষ্ঠী উপাসনালয়গুলো নির্মাণ করে থাকবেন, যাদের পেশা ছিল পশুপালন। উপাসনালয়সমূহের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। পূর্ব জার্মানীর লেইপনিং এলাকার আইথরা গ্রামে আবিস্কৃত উপাসনালয়ের চাঁরপাশে অন্ততঃ ২০টি ভবন পাওয়া গেছে। এসব ভবনে ৩শ’ লোক বাস করতো বলে ধারণা করা হয়। সদ্য আবিস্কৃত এ জনপদের এখনও কোন নামকরণ করা হয়নি। টানা ৩-বছর খননকার্য চালিয়ে স¤প্রতি প্রাচীন-এ সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রথম দাবা বর্তমান পাকিস্তানের ইন্দাস উপত্যকায় প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে দাবা খেলার সূত্রপাত হয়। সেকালে দাবাডূরা আজকের মতোই ৬৪ বর্গের ছক কাটা সিরামিক বোর্ডে দাবা খেলতেন। তাতে থাকত হাতি, রাজা, নৌকা ও ঘোড়া। হরপ্পার কিছু প্রতœতাত্তি¡ক ক্ষেত্রে এসবের নমুনা পাওয়া গেছে।
খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে প্রায় যতদূর জানা যায়, বিশ্বের প্রথম নগর পারস্য উপকুলে ইরিডু নামক একটি নগর গড়ে ওঠে। সুমেরিয়ান ভাষায় রচিত ইতিহাসে-এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও এর আগে কিছু ছোট শহরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; কিন্তু ইরিডুই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ নগরের মর্যাদা পায়, যেখান থেকে রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও শাসননীতি পরিচালিত হতো। খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ হাজার সালে বিশ্বের প্রথম উন্মুক্ত খনন ভূগর্ভস্থ মূল্যবান পাথর অনুসন্ধানের জন্য প্রাচীন মিসর ও মেসোপটেমিয়ায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনন করা হতো। বেঁচে থাকার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, প্রকৃতির বিশাল ভান্ডার থেকে খুঁজে নিয়েছে তার প্রয়োজনের জিনিসটি। ৪০০০-৩০০০ খৃষ্টপূর্ব মিশরের সভ্যতার উম্মেষ। মানুষ কিসের জোরে টিকল হাতিয়ারের জোরে পশুকে বশ করল এবং পরে আগুন আবিস্কার করে মানুষ নিজে এ জোর আবিস্কার করেছে। সভ্যতার দিকে এগিয়ে গেল মানুষ। কাঠের চাকা আবিস্কারের ৬২০০ বছর পরে স্টীম ইঞ্জিন ও সংযুক্তিযানের যুগ শুরু হয়। বিশ্বের প্রথম চাকা গুহাবাসী মানুষ চাকা তৈরীর পদ্ধতি জানত না। স্বাভাবিক ধারণার চেয়ে অনেক পরে আবিস্কৃত হয়েছে চাকা। প্রতœতাত্তি¡ক গবেষণায় সর্বপ্রথম এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ায় (আজকের ইরাক)। তার মানে যানবাহনে চাকার ব্যবহার শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি। আজও আমরা এর কোনো বিকল্প খুঁজে পাইনি।
৩৫০০ খৃষ্টপূর্বে ইতিহাস ঘাটিলে দেখা যায়, মেসোপটেমিয়ায় লাইব্রেরীর প্রচলন ছিল। ৩৫০০ খৃষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে এসে পালতোলা নৌকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ৩০০০ হাজার খৃষ্টপূর্বের অনেক আগেই গাধাকে পোষ মানানো হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ের যে সুমেরীয় যুদ্ধরথের ছবি পাওয়া যায় তা দেখে মনে হতে পারে যুদ্ধরথটি টানছে ঘোড়া-কিন্তু এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের ধারণা-ঘোড়া নয় গাধা। বিশ্বের প্রথম নীতিগল্প খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ হাজার সালে সুমেরীয় সাহিত্যে ছোটগল্প খুবই জনপ্রিয় ছিল। নৈতিকথার শিক্ষাদানের লক্ষ্যেই প্রধানত ওই সব গল্প লেখা হতো। ঈশপের গল্পে এ ধরনের নীতিকথার সন্ধান মেলে। কুকুর, শেয়াল, বাঁদর, গরু, হাতি, শূকর প্রভৃতি প্রাণী সেসব গল্পের চরিত্র হিসেবে উঠে আসত। বিশ্বের প্রথম কালি মানবসভ্যতার প্রথমদিককার দিনগুলোয় শক্ত তলে দাগ কেটে কিংবা কাদামাটিকে নানা আকার দিয়ে লেখা হতো। মিসরীয়রা প্যাপিরাস কাগজ আবিস্কারের আগেই ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কালি তৈরী করে। পরবর্তী কালে প্যাপিরাস উদ্ভাবনের পর কালিই হয়ে ওঠে লেখার জন্য আদর্শ মাধ্যম। তখনকার দিনে মূলত মৃৃত মানুষ ও পশুপাখির হাড় শুকিয়ে-পুড়িয়ে তরল কালি তৈরী করা হতো। বিশ্বের প্রথম প্লাইউড প্রাচীন মিসরে সর্বপ্রথম প্লাইউড আবিস্কৃত হয়। সঠিক দিনক্ষণ জানা না গেলেও প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সময়ে পালাইউডের প্রচলন ছিল। তখনকার প্লাইউড অবশ্য বর্তমান সময়ের প্লাইউডের মতো মসৃণ ও সুন্দর ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন ছয় ধরনের কাঠের সংমিশ্রণে ওই প্লাইউড তৈরী করা হতো।
খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ হাজার বছর আগে মিসর সরকার বিশেষ ধরনের পুলিশ বাহিনী নিয়োগ দেয়। প্রাচীন মিসরে বিশ্বের প্রথম পুলিশ বাহিনীর প্রচলন ছিল-এমন তথ্য জানা গেছে। সমগ্র মিসরের বিভিন্ন অঞ্চল ছিল তাদের কর্মক্ষেত্র। প্রত্যেক জেলা প্রশাসনে একজন করে পুলিশ কমিশনার নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং কিছু আইনগত দিকও ওই পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ৩০০০ হাজার খৃষ্টপূর্বের অনেক আগেই প্রতœবিদদের মতে সিরিয়ার বা মেসোপটেমিয়ার রোদে শুকিয়ে নেওয়া মাটির ইটের প্রচলন হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে এসে নিশ্চিতভাবে বলা চলে, ভূমধ্যসাগর বা আরবসাগরের ওপর দিয়ে পালতোলা নৌকার রীতিমত যাতায়াত শুরু হয়েছে। ৩০০০ হাজার খৃষ্টপূর্ব প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় কাদা দিয়ে তৈরি আয়তাকার ব্লকে মানচিত্র আঁকা হতো। খ্রিষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেকার এমনই একটি মানচিত্র পাওয়া গেছে ইরাকের কিরকুক শহরে। তাতে ১২৭টি আলাদা ভূখন্ড, কিছু পাহাড় এবং একটি নদীর ছবি আছে। এর চারকোণায় আছে কম্পাসের দিকনির্দেশনা, তবে ওপরের দিকে ধরা হয়েছে পূর্ব। কাছাকাছি সময়ের আরেকটি মানচিত্রে নয়টি গ্রাম ও তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদী ও রাস্তার ছবি খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।
খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০(তিন হাজার) শতকে মানুষ দৈনন্দিন প্রক্ষালন-কর্মে ফ্লাশের ব্যবহার করেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। কী ভাবে এল ফ্লাশ টয়লেট ঃ আজ ফ্লাশের ব্যবস্থা ছাড়া আমরা টয়লেট কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু জানেন কি, পৃথিবীতে প্রথম ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহৃত হয়েছিল কবে? সিন্ধু সভ্যতা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা। পাকিস্তানের সিন্ধু নদের তীরে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা কিন্তু নিজেদের তুলে নিয়েছিল অন্য এক উচ্চতায়। সেই সিন্ধু সভ্যতার নগরী হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা নিজেদের বাড়িতে ব্যবস্থা করেছিল এই ফ্লাশ টয়লেট।
খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ ভারতবর্ষের মানুষ রাস্তা দিয়ে প্রথম চলাচল শুরু করে। বিশ্বের প্রথম চা প্রাচীন চীনের সমাজ-জীবনে চা একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পানীয় হিসেবেই প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন চীনের সাহিত্যে-বিশেষ করে কবিতায়-চায়ের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। টারং রাজবংশের শাসনামলে লু উও ‘দ্য টি ক্লাসিক’ নামে একটি বই রচনা করেন খ্রিষ্টপূর্ব আট শতাব্দীতে। বইটিতে চা-গাছের উৎপাদন, চা তৈরির পদ্ধতি, নানা ধরনের চায়ের স্বাদ ও গন্ধ ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ২৮০০ খৃষ্টপূর্ব পৃথিবীতে সম্ভবত বাগান করার কাজে প্রথম পথিকৃৎ চীন সম্রাট শেন নুঙ বিভিন্ন যায়গায় লোক পাঠিয়ে নানারকম গাছ সংগ্রহ করতেন। ২৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব আকুপাংচার প্রথম আবিস্কার করেন কিংবদন্তির চীনা সম্রাট সেন নাং। গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ ওষধগুলোর প্রথম তালিকাও প্র¯ত্তত করেন তিনি। ২৫০০ খৃষ্টপূর্ব বছর আগে পৃথিবীর আকার গোল, সকলের জানা মাত্র এ কথাটিও নতুন ও অভিনব শোনাত। ২৫০০ খৃষ্টপূর্ব মিশরে কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে বিশ্বের প্রথম পেশাজীবী নারীদের আয়মূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে। তবে সে সময় পুরুষের মতো পেশাজীবী নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে সব কাজ করার সুযোগ পেতেন না। বিশেষ করে নারীদের বিচারক পদে কাজ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা ছিল।
বিশ্বের প্রথম সুইমিং পুলের ধারণা সর্বপ্রথম মাথায় এসেছিল সিন্ধু নদীর তীরবর্তী মহেঞ্জোদারো সভ্যতার অধিবাসীদের মধ্যে। প্রকৃত দিন-তারিখ জানা না গেলেও ধারণা করা হয় তা খ্রিষ্টের জন্মেরও আড়াই হাজার বছর আগে তৈরী। ১২ মিটার লম্বা এবং ৭ মিটার চওড়া এ সুইমিংপুলের সর্বোচ্চ গভীরতা ৮ ফুট। আজকের পাকিস্তানে এর ধবংসাবশেষ আজও দর্শনার্থীরা ঘুরে দেখতে পারেন। বিশ্বের প্রথম ভিজিটিং কার্ড হান শাসকদের আলমে (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০৬ অব্দ থেকে ২২০ খ্রিষ্টাব্দ) চীনে ভিজিটিং কার্ড নতুন ফ্যাশন হিসেবে প্রচলন লাভ করে। সে সময় কাগজের মান যাচ্ছেতাই ছিল। তাই দুই থেকে তিন ইঞ্চি প্রস্থের ফালি করে কাটা কাঠের টুকরোতেই তৈরী হতো কার্ড। সাদা পটভূমিতে তাতে লেখা থাকত কার্ডধারীর নাম, পদবি আর ঠিকানা। ২০০০ খৃষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময় চীনে ধানের চাষ শুরু, তা ভারতবর্ষের কাছ থেকেই শেখা। বিশ্বের প্রথম পরিচয়পত্র নির্বাচিত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য পরিচয়পত্র প্রবর্তন করে অ্যাসেরিয়ান সরকার। সঠিক দিনক্ষণ জানা না থাকলেও ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে ওই ব্যবস্থা চালু করা হয়। ওই পরিচয়পত্র ছিল মূলত ছোট মাটির ফলকের ওপর কিলকাকার বর্ণ খোদাই করা। বিশ্বের প্রথম জলঘড়ি সময় মাপার জন্য খ্রিষ্টের জন্মের ২০০০ বছরেরও বেশি আগে জলঘড়ির ব্যবহার শুরু হয়। বিরাট এক পাত্রের গায়ে দাগ কাটা থাকত সময়ের হিসাব। আর পানিপূর্ণ সে পাত্রের ছিদ্র দিয়ে পানি বেরিয়ে এসে সময় নির্দেশ করত। মেসোপটেমিয়ায় এ ধরনের জলঘড়ির নির্মাণ পাওয়া গেলেও ঠিক কবে এর ব্যবহার শুরু হয় বা কে আবিস্কার করেন তা জানা যায়নি। ২০০০ খৃষ্টপূর্বের অনেক আগে থেকেই গৃহপালিত পশু হিসেবে ঘোড়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ২০০০ খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত মিশরের প্রায় সমস্ত প্রতœতাত্তি¡ক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে কবর থেকে। বিশ্বের প্রথম বক্সিং প্রাচীন মিসরে বক্সিং খেলার প্রচলন ছিল বলে জানা গেছে। মিসরীয় ১৮তম রাজবংশের আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৩৫০ সালে বিভিন্ন রাজার সমাধিগাত্রে যেসব চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, রাজা তৃতীয় এমেনোফিসের সিংহাসনে আরোহণের সময় বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই সমাধিগাত্রে বক্সিং খেলার বিভিন্ন কৌশলের উল্লেখ রয়েছে।
২০০০ খৃষ্টপূর্বে জুডাইজমের ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ১৫০০ খৃষ্টপূর্বে হিন্দুইজমের ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ৫২৫ খৃষ্টপূর্বে বুদ্ধইজমের ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর, যীশু খৃষ্ট্রের জন্ম, মৃত্যু-৩১ খ্রিষ্টাব্দে। ৬১০ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ(স.) মুসলিম ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৫০০ শতকে গুরু নানক দেব জি, সিকিইজমের ভিত্তিস্থাপন করেন। মিড ১৯ শতকে মির্জা হুসাইন আলী নুরী, বাহা ধর্মের প্রবর্তক। ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব বিশ্বের প্রথম বর্ণমালা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং সিনাই অঞ্চলের সেমাইট আদিবাসীরা সর্বপ্রথম বর্ণমালার একটি অখন্ড রূপ দেয়। এতে ছিল মোট ৩০টি বর্ণ। মিসরের খনি অঞ্চলে ব্যবহৃত হিরেটিক লিপি থেকে নেওয়া হয়েছিল এ বর্ণমালার অক্ষরগুলো। মজার ব্যাপার এতে কোনো স্বরবর্ণ ছিল না। পাঠক পড়ার সময় নিজেই সুবিধামতো স্বরবর্ণ যোগ করে নিত। ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম-‘বলত’ শব্দটিতে স্বরবর্ণ যোগে তাঁদের পড়তে হতো ‘বালতি’। খ্রিষ্টপূর্ব চৌদ্ধ শতকে বিশ্বের প্রথম কফি ওষুধ হিসেবে কফি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইয়েমেনবাসী কফিকে কোমল পানীয় হিসেবে পছন্দ করতে শুরু করেন। কফি ফল অনেকটা শিমের মতো। প্রথমদিকে, কফি ফলের খোসা ছাড়িয়ে গরম জলে মিশিয়ে কফি তৈরি করা হতো। পরবর্তী সময়ে পনেরো শতকে কফি ফল তাপে ঝলসিয়ে গরম জলে মিশিয়ে পান করার রীতি চালু হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রচলিত কফি প্রথম তৈরি হয় সিরিয়াতে।
বিশ্বের প্রথম চশমা খ্রিষ্টপূর্ব ১২৮০ সালে ইতালিতে সর্বপ্রথম চশমা আবিস্কৃত হয়। ওই চশমাটি ছিল উত্তল লেন্সের এবং তা দূরের জিনিস দেখতে সাহায্য করত। ফ্লোরেন্সের অ্যালমানডো ডেলা স্পিনাকে এর উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও কোনো অপেশাদার ব্যক্তি সেটি তৈরি করেছিলেন-এমন ভিন্ন মতও প্রচলিত রয়েছে। ১৪০০ খৃষ্টপূর্বের আগে পৃথিবীর কোনো অংশেই ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হয়নি। প্রাচীন মিশরে খৃষ্টপূর্ব ১০৫০ অব্দে বেনি হাসানে ১৭নং সমাধিতে একটি ভাস্কর্যে স্টিক হাতে দু’জন খেলোয়াড়ের দাঁড়ানো অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। হকি খেলার ইতিহাস খুব প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ হাজার বছরের আগে এমন কোনো স্পস্ট সাক্ষ্য নেই যা দেখে ঘোড়সওয়ার মানুষের কথা ভাবা যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে বিশ্বের প্রথম চিনি উত্তর ভারতে আখের ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই সময়ে আখ-নিস্কাশিত নানা ধরনের মিষ্টিজাত দ্রব্য খুবই জনপ্রিয় ছিল। তখনকার অধিবাসীরা ঘরোয়া পরিবেশে আখ থেকে গুড় তৈরি করতেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা আখ থেকে গুড়ের পাশাপাশি চিনিও তৈরি করেন। তবে বর্তমান সময়ে প্রচলিত দানাদার চিনি যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের ফল। বিশ্বের প্রথম ক্যালেন্ডার রোমান সম্রাট রোমূলাস খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ৩৬০ দিনে এক বছর ধরে ১০ মাসের বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার চালূ করেন। পরে রাজা নুমা পমপিলিয়াস খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে জানুয়ারি ও ফেব্রæয়ারি নামে দুটি মাস ক্যালেন্ডারের শুরুতে সংযোজন করেন। শাসক অগাষ্টাস ও জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর সেকটিলিস ও কুইনটিলিস মাসের নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে আগষ্ট ও জুলাই করা হয়। বর্তমান যুগের ক্যালেন্ডারে পৌঁছাতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে।
৭৭৬ খৃষ্টপূর্ব গ্রীসে অলিম্পিক খেলাধুলার প্রর্বতন। ৩৯৩ খৃষ্টপূর্ব রোমান বর্বতার মুখে বন্ধ হওয়ার পর পিয়ের ডি কুবার্তিনের প্রচেষ্টায় ১৮৯৬ সালে আবারও সে গ্রীসেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম আসর। এ প্রাচীন টুর্নামেন্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্ট-১০০ মিটার দৌড়। বিশ্বের প্রথম নারীদের খেলাধুলা ঃ প্রাচীন অলিম্পিক আসরে নারীদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। তবে সে সময় ‘হেরিণ গেমস’ নামের অন্য একটি খেলায় নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারতেন। প্রতি চার বছর পরপর ‘হেরিণ গেমসের’ আয়োজন করা হতো এবং লোকমুখে তা ‘সিক্সটিন ওমেন’ নামে পরিচিতি লাভ করে। সঠিক সময় না জানা গেলেও ধারণা করা হয়, প্রথম অলিম্পিকের সময় থেকেই ওই গেমস শুরু হয়। প্রত্যেক অবিবাহিত নারী এতে অংশগ্রহণ করতেন। ৭৫৩ খৃষ্টপূর্ব রোমের প্রতিষ্ঠা। খৃষ্টপূর্ব ৬৯৫ সালে অ্যাসিরিয়া সাম্রাজ্যের নিনেভাতে বিশ্বের প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল অ্যাসিরিয়া সাম্রাজ্যোর সমস্ত প্রজাতির গাছপালা এক আঙ্গিনায় রোপন করা। কিন্তু বাস্তবে তা প্রায় অসম্ভম হলেও জোর চেষ্টা চলেছিল সে সময়। কারণ বর্তমানের জর্ডান, ইসরায়েল, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, আরবের উত্তরাঞ্চল, কুয়েত, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল ও ইরানের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে অ্যাসিরিয়া গঠিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশ্বের প্রথম দেয়াশলাই প্রাচীন চীনে সর্বপ্রথম তৈরী হয়। পাইনগাছের ছোট ছোট কান্ডের ভেতর সালফার ঢুকিয়ে শলাকা বানানো হতো। যা আগুনের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে উঠত। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত অনেক ধরনের দেয়াশলাই তৈরী হয়েছিল কিন্তু কোনোটাই ঘর্ষণে আগুন উৎপন্ন করতে পারত না। ৬০৬ খৃষ্টপূর্ব মিডিস ও চালডিয়া কর্তৃক নিনেভে শহর জয়।
খৃষ্টপূর্ব ৬০৫-৫৬২ সময়ে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক ব্যাবিলনীয় এক সম্রাটের আমলে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম চালু ছিল। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পারস্য শাসকদের শাসনামলে ওই ব্যাংকের বিলুপ্তি ঘটে। ওই ব্যাংকের প্রায় সব নথিপত্র বিলুপ্ত হলেও বেশ কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করা গেছে, যা থেকে জানা যায় ওই ব্যাংকে অনেক কেরানি কর্মরত ছিলেন। ৬০০ খৃষ্টপূর্ব বিশ্বের প্রথম ঝুলন্ত উদ্যান রাজা নেবুচাদনেজার দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলন নগরে ঝুলন্ত উদ্যান স্থাপন করেন। যা ছিল বিশ্বের বিস্ময়কর স্থাপনার মধ্যে, অন্যতম। রাজা নেবুচাদনেজার ইচ্ছে ছিল উদ্যানটিতে পাহাড়ি অঞ্চলের অবস্থা বিরাজ করবে, যেখানে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যাতে করে সহজাতভাবে গাছপালার বৃদ্ধি ঘটে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তবে ধারণা করা হয়, গ্রিক নগরীতে বিশ্বের প্রথম রিলে দৌড় চালু করা হয় ঃ রিলেদৌড় শুরুর সঠিক দিনক্ষণ জানা যায় না। তখনকার রিলেদৌড় বর্তমান রিলেদৌড় থেকে কিছুটা ভিন্নতর ছিল। সে সময়ে দৌড়বিদেরা জ্বলন্ত মশাল বহন করত এবং প্রতিযোগিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা জ্বালিয়ে রাখত। বিশ্বের প্রথম খাবার মেনু প্রাচীন গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে নৈশভোজের ব্যবস্থা থাকত। নৈশভোজে যোগদানকারী প্রত্যেক সদস্যকে আসন গ্রহণ করার সময় খাবারের মেনু দেওয়া হতো, যেখানে উল্লেখ থাকত কী কী খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখান থেকে যে-কেউ তাঁর পছন্দের খাবারটি বেছে নেওয়ার সুযোগ পেতেন।
খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথেন্সে অ্যারিস্টোটলের শিক্ষাদান কেন্দ্র লাইসিয়ামই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে অ্যারিস্টোটলসহ কয়েকজন শিক্ষক, একটি গ্রন্থাগার ও বিপুল পরিমাণ ইতিহাসের প্রাকৃতিক নিদর্শন নিয়ে গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানসহ নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও গণিত বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু করে। ২৭১-২১৩ খ্রিষ্টপূর্ব যতদূর জানা যায়, গ্রিসের সিসায়ন বিশ্বের প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা হচ্ছেন। সিসায়ন দক্ষিণ গ্রিসের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, যোদ্ধা ও কূটনীতিক। প্রাণঘাতী বিষে তাঁর মৃত্যুর আগেই তিনি আত্মজীবনী লেখা শেষ করেছিলেন। অনেক অসংগতি সত্তে¡ও এটিই পৃথিবীর প্রথম আত্মজীবনী। তিনি তাঁর লেখায় অপ্রিয় মানুষের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। ২০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে বিশ্বের প্রথম আয়না ব্রোঞ্জের আয়না দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটিতে প্রতিফলনের জন্য টিনের প্রলেপ দেওয়া হতো। কাচের আয়না, সে তুলনায় বেশ নতুনই বলা চলে। ত্রয়োদশ শতকে এক ইতালীয় বিজ্ঞানী কাচের আয়না তৈরী করেন। তিনি কাচের পাতে পারদের (মারকারি) প্রলেপ দিয়ে তৈরি করেন আয়না। এটি সারা বিশ্বে দ্রæত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশ্বের প্রথম কাগজ প্রাচীন চীনে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে হার্ন রাজবংশের শাসনামলে সর্বপ্রথম কাগজ তৈরি হয়। ওই সময়ের উৎপাদিত কাগজ বর্তমান সময়ে প্রচলিত কাগজের মতো পাতলা ও মসৃণ ছিল না। ওই সময় কাগজ তৈরি হতো এক ধরনের শণ থেকে এবং তা ছিল বেশ পুরু ও অমসৃণ। বিশ্বের প্রথম মাস গণনা গ্রিক জ্যোতির্বিদ হিপার্কাস খৃষ্টপূর্ব ১৯৫-১২৫ সর্বপ্রথম সূ²ভাবে চান্দ্র মাসের ব্যাপ্তি গণনা করেন। তিনি রোডস এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। তাঁর গণনা থেকে প্রাপ্ত চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য ও এর প্রকৃত মাপের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক সেকেন্ডের। তিনি ত্রিকোণমিতির পথিকৃৎ হিসেবেও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।
৩২৩ খৃষ্টপূর্ব থেকে ৩০ খৃষ্টপূর্বের মধ্যে বিশ্বের প্রথম স্বাস্থ্য বীমা যত দুর জানা যায়, প্রাচীন মিসরে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য বীমার প্রচলন হয়। টলেমীয় রাজবংশের রাজত্বকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে সব নাগরিকের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসাসেবা প্রদান হতো এবং তালিকাভুক্ত সব নাগরিকই স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পেত। এ ক্ষেত্রে রাজকোষাগার থেকে সব চিকিৎসা-খরচ বহন করা হতো। ধারণা করা হয়, এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম স্বাস্থ্য বীমা। বিশ্বের প্রথম ছাত্র আন্দোলন খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০ অব্দে চীনের ইমপিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের আন্দোলনের ভাষা ছিল রাজপথে দেয়াল-লিখন আর ¯েøাগান। ছাত্রনেতা গও তাই এবং তাঁর সহযোগী জি বাইওর নেতৃত্বে ওই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে সিংহভাগ ওই আন্দোলনে শামিল হন। পরে সাধারণ জনতাও তাতে সহমত পোষণ করেন। ৬৪ খৃষ্টপূর্ব সম্রাট নিরোর আমলে রোমে ভয়াবহ এক অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। আট দিনব্যাপী এ অগ্নিকান্ডে ১৪টি প্রশাসনিক অঞ্চলের ১০টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বের প্রথম জন্মদিনের কেক-প্রাচীন গ্রিসের চাঁদের দেবী আর্তেমিসের উপাসকেরা দেবীর জন্মদিনে মধু দিয়ে তৈরি গোল কেক নিবেদন করত। প্রতি মাসে নতুন চাঁদ উঠলে পালিত হতো দেবীর জন্মদিনের উৎসব। কেকের ওপর মোমবাতি জ্বালানো হতো চাঁদের প্রতিরূপ হিসেবে পরবর্তীকালে এ আচারটিকেই সাধারণ মানুষ নিজেদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের এক অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে। নতুন পরিচয়ে দু‘হাজার বছরের প্রাচীন শহর ‘বন‘।
১০০ খিষ্টাব্দে বিশ্বের প্রথম অভিধান হিউ শেন নামে এক চীনা গবেষক সর্বপ্রথম অভিধান বের করেন। এতে ৯ হাজার ৩৫৩টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভুক্তি ছিল। অভিধানটিতে অন্তর্ভুক্তিগুলো ছিল অক্ষরের ক্রমানুসারে। প্রাচীন অভিধানগুলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের কাজে ব্যবহৃত হতো। সব ধরনের গুণাবলিসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ অভিধানের প্রচলন শুরু হয় অনেক পরে। প্রথম অভিধানের খবর মেলে চীনে। ৭ সালের ৭ জুলাই ছিল (০৭-০৭-০৭) প্রথম লাকী ট্রিপল সেভেনের দিন। সন গণনার পর থেকে এ ট্রিপল সেভেনের দিনটি ছিল অঙ্কের ৭ সংখ্যাটিকে সৌভাগ্য প্রতীক হিসাবে বলা হয় লাকী সেভেন। এক হাজার বছর পর আবার এ দিনটি ফিরে আসে ০৭-০৭-১০০৭ তারিখ। আবার এক হাজার বছর পর এ দিনটি ফিরে আসে ০৭-০৭-২০০৭ তারিখ। আবার এক হাজার বছর পর এ দিনটি ফিরে আসবে ০৭-০৭-৩০০৭ তারিখ। ০৭-০৭-২০০৭ তারিখ জাপানে ভালবাসা দিবস। জনকন্ঠ পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লাকী ট্রিপল সেভেনে ০৭-০৭-২০০৭ তারিখ ৮০,০০০ হাজার বিয়ে হচ্ছে। আবার এ দিনটি ফিরে আসবে ০৭-০৭-৩০০৭ তারিখ মানে ১,০০০(এক হাজার) বছর পর। চীনে দ্বিতীয় শতাব্দীতে যদ্দুর জানা যায়, বিশ্বের প্রথম মই আবিস্কৃত হয়। মই আবিস্কার চাষাবাদকে সহজতর করে তোলে। প্রচীনকালে চাষাবাদের প্রক্রিয়া সুসংগঠিত ছিল না। মাটির ঢেলা ভাঙার জন্য মই আবিস্কৃত হওয়ার পর চাষাবাদ আরও সহজ হয়ে যায়। ওই সময়ের মই ছিল ধাতব কাঁটাযুক্ত এবং প্রধানত কৃষিকাজের জন্য।
২৬৯ সালের ১৪ ফেব্রæয়ারি, প্রাচীন রোমান সম্রাট ক্লাডিয়াসের আমলে ভ্যালেন্টাইন এক ধর্মযাজক বিয়ের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তরুণ-তরুণীদের বিয়ের আয়োজন করায় তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। সেই ঘটনার স্মরণেই প্রতিবছর ১৪ ফেব্রæয়ারি, ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করা হয় পাশ্চাত্যে। ৪৯৪ সালের ১৪ ফেব্রæয়ারি, পোপ জেলাসিয়াস সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন ধর্মোৎসব ঘোষণা করেন। স¤প্রতি তার হাওয়া এদেশেও লেগেছে। আমাদের দেশে গত ২০০২ সাল থেকে এ দিবসটি নিয়ে তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এবং দিন দিন বাড়ছে। এ দিবসটির নাম করণ করা হয়েছে ভ্যালেন্টাইন ডে বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস। ৩৩০ সালের ১১ মে, কনষ্টান্টিনোপলকে রোম সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী করা হয়। ৪২৪ থেকে ৪৫২ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম তাই উয়ের শাসনামলে উত্তর উইয়ের রাজধানীতে সর্বপ্রথম স্থানান্তরযোগ্য কাচের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। এটি নির্মাণ করতে পশ্চিমা কাচ উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় এবং মধ্য এশিয়া থেকে প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে আসা হয়। কয়েক শ শ্রমিক এতে অংশ নেন। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে সেনাপতি মুসার অধিনস্থ সেনাপতি তারিক বিন রিয়াদ তার মাত্র ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে তৎকালীন স্পেনের শাসক রডরিক এবং তার ১ লাখ সদস্যের চৌকস বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে ইউরোপ তথা স্পেনের বুকে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল, স্পেনকে দখল করে নেয় পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা ফার্ডিন্যান্ড এক বিশাল খ্রিষ্টান বাহিনী গঠন করে অতর্কিতে স্পেনের মুসলমানদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ, এক ভয়াবহ ও নির্মম ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। প্রতারণার মাধ্যমে অসহায় মুসলিম নরনারীকে মসজিদে বন্ধী করে আগুন জ্বালিয়ে দেয় হাজারো নিস্পাপ মানুষকে-এরপর মুসলমানদেরকে ‘এপ্রিল ফুল’ বলে গালি দেয়। এপ্রিল ফুল হচ্ছে স্পেনে ৭ লাখ মুসলিম হত্যার কলঙ্কিত অধ্যায়।
১৭০০ বছর আগে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় গবেষণা কাজে রত থাকাকালে এ আবিস্কার করেন। বায়ু সংকোচনের এ নীতি তিনি এয়ারগানের পাশাপাশি পিস্টন, পাম্প ও আরও কিছু যন্ত্রে ব্যবহার করেন। বিশ্বের প্রথম এয়ার গান সংকুচিত বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পাথর ছুড়ে মারার অস্ত্র প্রথম তৈরি করেন গ্রিক বিজ্ঞানি টিসিবিয়াস। বিশ্বের প্রথম হাতঘড়ি আবিস্কৃত হয়েছিল প্রায় ১৩০০ বছর আগে। তবে তাকে ছোট করতে করতে হাতের কব্জিতে নিয়ে আসতে আরো অনেক সময় লেগে যায়। প্রায় ৫০০ বছর আগে প্রথম হাতঘড়ি তৈরী সম্ভব হয়। তবে ঠিক কোথায়, কে তা তৈরী করেছিল, তা জানা যায়নি। ধারণা করা হয় ফ্রান্সের বয়েস, জার্মানির নুরেমবার্গ কিংবা উত্তর ইতালিতে তৈরী হয়েছিল প্রথম হাতঘড়িটি। বিশ্বের প্রথম কাগজের নকশা কাগজ ভাঁজ করে নানান আকৃতি ও নকশা করার এক ধরনের জাপানি শিল্পকলার নাম ওরিগ্যামি। নানা ধরনের পশুপাখি, ফুল-ফল ইত্যাদি এমনকি মানুষেরও নিখুত আকৃতি দান করা যায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি জাপানে জনপ্রিয় হলেও সর্বপ্রথম এর প্রচলন শুরু হয়েছিল প্রাচীন চীনে টার্গ রাজবংশের (৬১৮-৯০৬) আমলে। বিশ্বের প্রথম মুদ্রণশিল্প প্রাচীন চীনে টারং রাজবংশের (৬১৮-৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে ছাপার কাজ হয়। সেখানে ছবি ও লেখা দুটোই একসঙ্গে ছাপানো হতো। সেরওয়ান স্রাং (৬০২-৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) চীন থেকে ভারতে আসেন বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা নিতে। চীনে তাঁর সংগৃহীত ছবি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে সর্বপ্রথম ছাপার কাজ হয় ৬৪৫ সালে। ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে জাপানের একই রাজপরিবারের সদস্য রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আসছেন। ১৯৯০ সালের ১১ নভেম্বর-জাপানের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে সম্রাট আকিহিতো ১২৫তম রাজা। বর্তমান রাজা আকিহিতো হলেন এ পরিবারের ১২৫তম রাজা। ৭৫৬ সালের ৮ মার্চ, স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
বিশ্বের প্রথম জীবনীগ্রন্থ আরব পন্ডিত ইবনে সাদ (মৃত্যু-৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। সংকলনগ্রন্থটির নাম ছিল কিতাব আল তাবাকাত আল-কবির। ওই জীবনীগ্রন্থ ছিল কয়েক খন্ডে লিখিত। মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান সহস্রাধিক ব্যক্তির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে এ গ্রন্থে। ইবনে সাদ আরব ও ইরাকে গবেষণার মাধ্যমে এ গ্রন্থ রচনা করেন। ১০০৮ সালের মধ্যে লেখা শেষ হয়েছিল জাপানি উপন্যাস মুরাসাকি শিকিবুর গেনজি কাহিনী। গেনজি কাহিনী হাজার বছরের প্রাচীন উপন্যাস। ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে এ প্রাচীন উপন্যাসের সহস্র বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। বিশ্বসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয় গেনজি কাহিনীকে। এ কাহিনী নিছক প্রেমের কাহিনী আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। ১০২৪ সালে চীনারা পৃথিবীতে প্রথম কাগুজে টাকা চালু করেছিল। টাকার একটাই রং। ১০৪৪ সালে সাং রাজবংর্শের আমলে সর্বপ্রথম বিশ্বের প্রথম আর্মি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয় চীনে। শিক্ষানবিশ সেনা কর্মকর্তাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ওই একাডেমি গঠন করা হয়। তৎকালীন উই চেন মন্দিরের পার্শ্ববর্তী জায়গা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু এলাকাজুড়ে একাডেমি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। ১০৯৬ সালে ইংল্যান্ডে-অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত ১১৬৭ সাল থেকে সারা বিশ্বে পরিচিতি পেতে শুরু করে। ১২১৫ সালে বিশ্বের প্রথম পৌরসভা গঠিত হয় “লন্ডন শহর’’। বিশ্বে প্রথম বন্ধুক তৈরী হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনে।
১২১৫ সালের ১৫ জুন, ম্যাগনা কার্টা বা মহাসনদে স্বাক্ষর করেন রাজা জন। ওই সনদে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ও মুক্ত মানুষের গ্যারান্টি দেয়া হয়। ২০১৫ সালের ১৫ জুন, ম্যাগনা কার্টা স্বাক্ষরের ৮০০তম বার্ষিকী পূর্ণ হবে। যুক্তরাজ্য ম্যাগনা কার্টা বা মহাসনদের ৮০০তম বার্ষিকী উদযাপন শুরু করেছে। পাঁচ বছর ধরে এ উৎসব চলবে। যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথভূক্ত দেশগুলোতে ম্যাগনা কার্টার প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১২৯৭ সালে ম্যাগনা কার্টা দলিলটিতে মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণা ও সংবিধানেরও মূল ভিত্তি। এ দলিলটি মানব-প্রগতির ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ৭১০ বছরের পুরোনো দলিল ম্যাগনা কার্টা গত মঙ্গলবার (১৮-১২-২০০৭) তারিখ নিউইয়ার্কে দুই কোটি ১৩ লাখ ডলারে নিলামে বিক্রি হয়েছে। এ ম্যাগনা কার্টাকে অনেকে মুক্তির সনদ বলে অভিহিত করে থাকে। এ দলিলটি যুক্তরাষ্ট্রে থাকবে এবং ন্যাশনাল আর্কাইভেই প্রদর্শিত হবে। এ পর্যন্ত ম্যাগনা কার্টার ১৭টি দলিলের খোঁজ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার যেটি বিক্রি হয়েছে, সেটি ব্যক্তিমালিকানায় ও যুক্তরাষ্ট্রে থাকা একমাত্র কপি। আধুনিক যুগে অনেক আইনের ভিত্তি হলো এ ম্যাগনা কার্টা। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে চীনের বেজিং নগরী থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গবেষকদের মতে বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদপত্রের নাম ‘পিকিং গ্যাজেট’। আবার কোন কোন পন্ডিতজনের মতে এটি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। সমাজের কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্র পরিবার ছিল-এর পাঠক। তাই এটিকে তারা সংবাদপত্রের মর্যাদা দিতে উৎসাহী নন। ১৩৭৯ সালের ২৬ নভেম্বর, ইংল্যান্ডে অক্সেফোর্ড মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৪৫২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, ইংল্যান্ডে খৃষ্টান ধর্ম গ্রন্থ বাইবেল প্রথম ছাপানো হয়। ১৫০০ সালে মানবদেহ চিত্র মানুষের প্রথম নির্ভুল এবং বিস্তারিত এনাটমিক্যাল ড্রইং করেন শিল্পী এবং উদ্ভাবক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। আর এটা করার জন্য তাঁকে আগে বেশ কিছু শবদেহ কেটে পরীক্ষা করতে হয়েছে। তাঁর আঁকা হৃদপিন্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রগুলোতে বাল্বের কাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে মস্তিস্কের গহবরগুলো সম্পর্কে একটি পরিস্কার চিত্র দেয় ভিঞ্চির ড্রইং। ১৫৩০ সালে বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বের সর্বপ্রথম কফির দোকান চালু হয় পঞ্চদশ শতকে আরবের কিছু নগরীতে। ১৫৩০ সালে কফি শপ দামেস্ক, আলেপ্লোতে শুরু হয় কফির বাণিজ্যিক বিপণন। পরে তা আরব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫৩৯ সালে কায়রোতে কফির দোকান ও কফি বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৫৩৮ সালের পূর্বে ফ্রান্সে মেয়েদের মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। তারা ছিল শুধু পুরুষের সেবাদাসী। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়ে টাকা খাটানো তার জন্য ১৯৩৮ সাল পর্যন্তও নিষিদ্ধ ছিল। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় মেয়েদের অবস্থাও সামগ্রিকভাবে-এর চেয়ে উন্নত ছিল না। বিংশ শতাব্দীতেই তারা ভোটাধিকার তথা রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। ফ্রান্সে এ অধিকার তারা পায় ১৯৪৪ সালে। ইংল্যান্ডে ১৯২৮ সালে, ইউরোপের কিছু কিছু দেশ সত্তরের দশকে এ অধিকার অর্জন করে। ১৫৭৯ সালের ১৭ জুন, ক্যালিফোর্নিয়ার ইংরেজদের উপর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা। ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম চার চাকার গাড়ী চলাচল করে। ১৬০১ সাল থেকে পৃথিবীতে তামাক ব্যবহার হয়ে আসছে। ১৯০১ সালের দিকে পৃথিবীতে প্রথম সিগারেট উৎপাদন হয়।
১৬০৭ সালের ৩ মে, ১০৪ জন ইংরেজ প্রথমবারের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর আমেরিকার জেমসটাউনে প্রথম স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ২০০৭ সালের ৩ মে, এএফপি ঃ উত্তর আমেরিকার জেমসটাউনে প্রথম স্থায়ী ইংরেজ বসতি স্থাপনের ৪শ’ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (০৩-০৫-২০০৭ তারিখ) ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ১৬ বছর পর প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। এটা ৮১ বছর বয়সী রাণীর চতুর্থ যুক্তরাষ্ট সফর। ১৯৫৭ সালে জেমসটাউনে ইংরেজ বসতি স্থাপনের ৩৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি প্রথম যুক্তরাষ্ট সফর করেন। ১৬০৯ সালের ২ জানুয়ারি, টেলিস্কোপ আবিস্কার করে গ্যালিলিও প্রথম দেখেছিলেন চাঁদ। টেলিস্কোপ আবিস্কারের ৪০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করা হয় ০২-০১-২০০৯ তারিখ। বিশ্বের প্রথম থার্মোমিটার ষোড়শ শতকে ইতালিতে ১৬১২ সালে ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সেন্টোরিয়াস থার্মোমিটার ব্যবহার করে মানবদেহের তাপমাত্রা পরিমাপের কথা উল্লেখ করেন। তবে তিনি নিজেকে এর আবিস্কারক হিসেবে দাবি করেননি। রোম থেকে পাওয়া ১৬১১ সালের কিছু নথিতে দুটো থার্মোমিটারের নকশা পাওয়া গেছে। কিন্তু এর আবিস্কারকের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। ১৬২১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে পালিত হয়ে আসছে। ১৮৬৩ সাল থেকে সরকারী ছুটির দিনে পরিণত হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারকে থ্যাঙ্কসগিভিং ডে হিসেবে ঘোষণা দেন। এছাড়া বাসায়ও অনেকে বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারে মিলে টার্কি ভোজের আয়োজন করে থাকেন। সেনসাস ব্যুরো জানিয়েছে, চলতি বছর (২০০৬ সালে) যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে ২৫ কোটি ৬০ লাখ টার্কি রয়েছে বিভিন্ন খামারে। এর ৯০% জবাই করা হয়েছে থ্যাঙ্কসগিভিং ডে’তে।
১৬৩৩ সালে জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গ্যালিলির ধর্মীয় বিশ্বাসের পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল এবং এরপর তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছিল। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। ১৬৩৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় ক্যামব্রীজে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়। ১৬৩৮ সালে জন হাভার্ডের উদ্যোগে আমেরিকার সবচাইতে পুরাতন লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত কোনো কোনো গবেষকদের মতে বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদপত্রটি ‘পোষ্ট অফ ইনরিফেস টিভলিনগার’ পত্রিকাটি। কিন্তু মনে রাখা দরকার ওটি দৈনিক সংবাদপত্র নয়, ‘সংবাদ সাময়িকী’। ১৬৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্বের প্রথম সংবাদ ম্যাগাজিন বের হয় ফ্রান্সের প্যারিস থেকে। ম্যাগাজিনটির নাম ছিল জার্নাল ডি স্কেভানস। ওই ম্যাগাজিনে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয় ছিল নতুন বইয়ের খবর, মানবাধিকার ও বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতির খবরাখবর। এ ছাড়া থাকত আদালতের খবর ও মৃত্যুসংবাদ। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায়, দৈনিক প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ‘ফ্রাঙ্কফুটার জাইচুঙ’। এটি প্রকাশিত হয়েছিল জার্মানির অন্তর্গত ‘ফ্রাঙ্কফুট’ নামক শহর থেকে। এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম দৈনিক প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রকৃত দাবিদার। ১৬৬৬ সালে স্যার আইজাক নিউটন আলোর বিচ্ছুরণ আবিস্কার করেন।
১৬৬৮ সালে সুইডিশ সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে এসে সুইডিশ সেন্ট্রাল ব্যাংকের তিনশ’ বছর বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এ পুরস্কার প্রবর্তন করে। ১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে প্রথম নোভেল পুরস্কার দেয়া হয়। সুইডিশ ব্যাংকই এ পুরস্কারের অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। সুইডিশ সেন্ট্রাল ব্যাংকই পৃথিবীর প্রথম ব্যাংক। ১৬৭৮ সালের ২৫ জুন, ইতালির গণিতবিদ মিসেস এলিনা পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বের প্রথম মহিলা হিসেবে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৬৮০ সালের পর থেকে মাত্র বিজ্ঞানিরা ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন। ১৭৫৪ সালে চেনা গিয়েছিল কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে, ১৭৭২ সালে চেনা গিয়েছিল নাইট্রোজেনকে ও ১৭৭৩ সালে চেনা গিয়েছিল অক্সিজেনকে। ১৭৮০ সালে প্রথম ভার্সাই চুক্তি (ভার্সাই, ফ্রান্স) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষায় সমঝোতা সাধন, এ চুক্তির মাধ্যমে ৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ। ১৭৮৮ সালের ২৬ জানুয়ারি, অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ১৬৯০ সালে দুনিয়ার দ্বিতীয় ব্যাংক-ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯৭ সালে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে বিশ্বের সর্বপ্রথম ১১ জন করে খেলোয়ার নিয়ে গঠিত দু‘টি দলের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৭০৯ সালে ইংল্যান্ডের কেন্ট ও সারে সর্বপ্রথম। ১৭৮৭ সালে লন্ডনে ম্যারিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের জন্ম হয়েছিল। ১৭৮৮ সালে ক্লাব খেলার নিয়ম-কানুন চালু করে। মেয়েরা খেলে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে ১৮৮৭ সালে। ১৭৯২ সালের ১ অক্টোবর, বিশ্বের প্রথম মানি অর্ডার প্রচলন বৃটেনে শুরু হয়।
১৭৯২ সালের ১৩ অক্টোবর হোয়াইট হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৮০০ সালে নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। হোয়াইট হাউস হোয়াইট কেন? হোয়াইট হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন। এটি ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্তিত। এটি ধূসর রঙের প্রস্তর দিয়ে তৈরী করা হয়। ১৮১৪ সালের ২৪ আগষ্ট, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এটিকে জ্বালিয়ে দেয়। তখন স্থপতি জেমস হোবানের নির্দেশমতো বিল্ডিংটিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয় এবং ধোঁয়া ও আগুনের দাগ মুছতে সাদা প্রলেপ লাগানো হয়। তখন থেকেই এটিকে ‘হোয়াইট হাউস’ বলে। ১৭৯৭ সালে পৃথিবীর ওজন ছিল ৬(ছয়) কোটি কোটি কোটি টন। ১৭৯৭ সালে বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু ছিল-২৫-বছর; ১৮৯৭ সালে গড় আয়ু ৪৮-বছর; ১৯৪৭ সালে ৬৫.১-বছর; ১৯৯৭ সালে ৭৬.৪-বছর। ২০ জুলাই, ১৯৯৯ সালের হিসেব ৭৭ বছর এবং ২০৪৭ সালে বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু হবে প্রায় ১০০/১২০ বছর। ১৮০২ সালের ১০ এপ্রিল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জরিপ কাজের সূচনা হয়। ১৮০৮ সালের আগে কেউই কৃত্রিম আলোর উৎস তৈরীতে সাফল্য অর্জন করেননি। সে বছরই হামফ্রে ডেভি নামের এক ইংরেজ বিজ্ঞানী বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক আর্ক বাতি তৈরী করেন। দুই টুকরো কার্বনকে একটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে যুক্ত করা হয়। পরে এর মধ্যকার ফাঁকা জায়গা দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে কার্বনের টুকরো দুটি উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে। এটাই ছিল তাঁর আবিস্কৃত বাতির মূলনীতি। ১৮১৭ সালে বিশ্বের প্রথম কেলিডস্কোপ স্যার ডেভিড ব্রিস্টার স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় সর্বপ্রথম কেলিডস্কোপ আবিস্কার করেন। কেলিডস্কোপ হলো রঙিন কাচের টুকরো ও দুটি আয়না সংবলিত নলবিশেষ, যা ঘোরালে ভেতরে পরিবর্তনশীল রং ও আকার দেখা যায়। ১৮৩০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, রকেট দিয়ে লিভারপুল থেকে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত রেলগাড়ি চলাচলের মাধ্যমে লিভারপুল অ্যান্ড ম্যানচেস্টার রেলওয়ের যাত্রা শুরু হয়। পৃথিবীর প্রথম এ আধুনিক রেলগাড়িটি উদ্বোধনী দিনেই দুর্ঘটনাকবলিত হয়। রকেট দুর্ঘটনায় সেদিন ব্রিটেনের এক সাংসদ নিহত হন। তবু সেই দিনটিকে আধুনিক পরিবহন যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন করে রেখেছে স্টিফেনসনের রকেট।
১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে চালর্স হ্যাবোস বিশ্বের প্রথম বার্তা সংস্থার কার্যক্রম শুরু করেন। মি. হ্যাবোস তাঁর বার্তা সংস্থার প্রতিবেদকের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ফরাসি সংবাদপত্রগুলোয় নিয়মিত সরবরাহ করতেন। আসলে হ্যাবোস এ কাজটি করতেন সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার জন্য এবং গোয়েন্দা সংস্থার মতামতের পরই কেবল সেসব খবর বার্তা সংস্থার মাধ্যমে সংবাদপত্রে পৌঁছাত। ১৮৩৫ সালে ‘নেগেটিব’ আবিস্কার করে ব্রিটিশ আবিস্কারক ট্যালবট ছবি তোলার প্রযুক্তিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন। আধুনিক ফটোগ্রাফির জনক হেনরি ফক্স ট্যালবট। অষ্টাদশ শতকের ত্রিশের দশকে পৃথিবীর প্রথমদিককার ছবিগুলো তাঁরই তোলা। ১৮৩৯ সালে ফ্রান্সে প্রথম ফটোগ্রাফি আবিস্কার হয়। ১৮৩৫ সালের ২৯ আগষ্ট, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন নগরী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞান (ঝড়পরড়ষড়মু) শব্দটি প্রবর্তন করেন-আগাস্ট কোৎ। সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ঘটনাবলির বিজ্ঞান। এ সংজ্ঞাটি হলো-এল. এফ. ওয়ার্ড ও গ্রাহাম সামনার। সমাজবিজ্ঞান হলো প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান-এ উক্তিটি হলো-ডুর্খেইম। কোনটি ছাড়া মানুষ নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না-সমাজ। সাধারণ সমাজ বলতে কোনটি বুঝায়-সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি। ১৮৪০ সালের ৬ মে, ইংল্যান্ডে বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়। ১৮৪০ সালে প্রথম ইলেক্ট্রিসিটি জার্নাল প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ সালে বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিস্কৃত ইলেকট্রিসিটি। ১৮৪৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, বৃটেন প্রথম অস্ত্রোপচারের জন্য এ্যানেসথেতিক্স ব্যবহার করে। ১৮৪৮ সালে সংবাদপত্রে প্রথম আবহাওয়া বার্তা ছাপা শুরু হয়।
১৮৪৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, কার্ল-মার্কস কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো ঘোষণা করেন। ১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রæয়ারি, কার্ল-মার্কস ও ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৮৫০ সালে বিশ্বের প্রথম রেফ্রিজারেটর জেমস হ্যারিসন গিলং নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য রেফ্রিজারেটর নির্মাণ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিকভাবে বরফ বিক্রি করা। গৃহস্থালির কাজে, অর্থাৎ রান্নাঘরে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য রেফ্রিজারেটর তৈরী করে ফ্রান্সের কারে অ্যান্ড কোং। তারা সেটি বাণিজ্যিকভাবে ফ্রান্স ও ইউরোপীয় দেশে বিক্রি শুরু করে অষ্টাদশ শতকের ষাটের দশকে। ১৮৫১ সালের মে-অক্টোবর মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব বাণিজ্য-শিল্প প্রদর্শীর কথা বলা হচ্ছে। ১৮৫৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর, উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে বিশ্বের প্রথম ত্রিকোণ ডাকটিকিট ইস্যু হয়। ১৮৫৫ সালের ‘‘মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন’’ শ্রমিকের মৃত্যুর ফলে তার পরিবারের যে আর্থিক ক্ষতি হয়, এর সঙ্গে আণুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ আইন দিয়ে উনিশ শতকের ৪৫টি বছর চলেছে, বিশ শতক চলে গেছে এবং একুশ শতক চলিতেছে। শ্রমিকের জন্য আইনের পরিবর্তন হয়নি।
১৮৫৬ সালে ‘‘বিশ্বের প্রথম ব্যালট পেপার’’ রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে সর্বপ্রথম নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার ব্যবহৃত হয়। মেলবোর্নের আইনজ্ঞ হেনরি চ্যাপম্যান ১৮৫৬ সালের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের পরিকল্পনা করেন। ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে তাঁদের পছন্দের প্রার্থীর নাম কাগজের ¯িøপে লিখে দেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থীদের ছাপানো নামসহ ব্যালট পেপার ব্যবহৃত হয়। ১৮৭২ সালের ১৫ আগষ্ট, ইংল্যান্ডে প্রথম গোপন ব্যালটে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ সালের আগষ্ট মাসে জার্মানীর ডুসেলডর্ফের একটি পাহাড়ী উপত্যকায় প্রথম নিয়ানডারথাল যুগের মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকেই তৈরী করা হয় প্রাচীন পৃথিবীর মানুষের এ আকৃতি। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মান ব্যবসায়ী ফিলিপ রেইস বিশ্বের প্রথম টেলিফোন নামের কিছু যন্ত্রের প্রদর্শনী করেন। এ যন্ত্রগুলো মানুষের স্বরকে তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে ট্রান্সমিট করতে পারত। যদিও শোনার পর সে শব্দ থেকে প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মূলত রিসিভারের কিছু ত্রæটির কারণে এ সমস্যা হতো। তবুও টেলিফোনের প্রথম বাস্তব প্রয়োগের কারণে রেইসই এর আবিস্কারক হিসেবে স্বরণীয়। ১৮৬১ সালের ২৩ মার্চ, লন্ডনে প্রথম ট্রাম সার্ভিস চালু হয়। ১৮৬৪ সালের ২২ আগষ্ট, আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৬৬ সালে সর্বপ্রথম টেলিগ্রামের তার বসানো হয় আটলান্টিকের তলদেশ দিয়ে। এ কাজে সাহায্য নেয়া হয়েছিল ওই সময়ের বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজ দ্য ইষ্টার্নের। পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর মধ্যে আটলান্টিক বয়সে সবচেয়ে নবীন। ভূতাত্তি¡কেরা ধারণা করেন, এর গঠন শুরু হয় জুরাসিক আমলে। মহাসাগরটির আয়তন প্রায় ১০৬ দশমিক ৪ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার। এটি পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ এলাকাজুড়ে অবস্থিত। প্রথম যে মহাসাগর জাহাজ ও বিমানে পাড়ি দেওয়া হয়, সেটি আটলান্টিক। পুয়ের্তোরিকো ট্রেঞ্চ আটলান্টিকের গভীরতম এলাকা। এর গভীরতা প্রায় সাড়ে আট হাজার মিটার। আটলান্টিক মহাসাগরের বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড। ১৮৬৮ সালে লন্ডনে বিশ্বের প্রথম ট্রাফিক লাইট রেলওয়ের সিগনাল ব্যবস্থা দেখেই ট্রাফিক লাইট ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এতে দুটি বাহু ছিল, যা ওঠানামা করিয়ে চলাচলের দিকনির্দেশ করা হতো। রাতে ব্যবহারের জন্য ছিল লাল আর সবুজ গ্যাসলাইট। পথচারী রাস্তা পার হওয়ার আগে নিজেই সিগনাল পরিবর্তন করে নিত। তবে পুরো ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। বাতির গ্যাস শেষ হয়ে গেলে পুরো ব্যবস্থা পড়ত অকার্যকর। একবার তো গ্যাসে আগুন ধরে এক পুলিশ সদস্য মারাই গিয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালের ৯ অক্টোবর, বিশ্ব ডাক ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৭৫ সালের মধ্যেই দেখা যায়-নদীর ক্ষয়, হিমবাহ নেমে আসা, জমি গড়ে ওটা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে মোটামোটি মতের মিল হয়েছে।
১৮৭৫ সালে লন্ডনে প্রথম হকি অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ সালের ১৫ মার্চ, সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ১১ জন করে খেলোয়ার নিয়ে প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয়। প্রতিদ্ব›দ্বী দল দুটি ছিল ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ওই খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে হারায় ইংল্যান্ডকে। অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটসম্যান চার্লস ১৬৫ রান করেন; এটাই টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম শত রান। ১৮৭৬ সালে ইংল্যান্ডে স্থাপিত সবচেয়ে প্রাচীন হকি ক্লাবের নাম টেডিংটন হকি ক্লাব। ১৮৯৫ সালের ২৬ জানুয়ারি, ইংল্যান্ডে পুরুষদের প্রথম আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচঃ ওয়েলস এবং আয়ারল্যান্ড দলের মধ্যে। ১৮৭৭ সালের ৯ জুলাই, প্রথম উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় সোলার গোর বিজয়ী হন। ১৮৭৮ সালে ব্রিটেনের অধ্যাপক ডেভিড হিউজ বিশ্বের সর্বপ্রথম ‘‘মাইক্রোফোন’’ আবিস্কার করেন। তিনি শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গে কার্বনের তার সংযুক্ত করে তাতে ব্যাটারি থেকে প্রবাহিত বিদ্যুৎ চালনা করেন। তিনি অতি উত্তম পারদের সঙ্গে উইলো কাঠের টুকরো মিশিয়ে একটি পরিবাহক তার তৈরি করেছিলেন, যা ছিল এ আবিস্কারের মূল চালিকাশক্তি। ১৮৭৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। ১৮৮১ সালের ১৬ মে, বার্লিনে বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম সার্ভিস চালু হয়। ১৮৮২ সালে লন্ডনে প্রথম ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ সালে ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার্সের (আইইই) প্রতিষ্ঠিত হয়-তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের ২০০৯ সালে ১২৫ বছর পূর্তিতে আইইইর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। ১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশে আইইই বাংলাদেশ শাখা কাজ করে যাচ্ছে।
১৮৮৫ সালের ২০ ডিসেম্বর, রাস্তায় প্রথম মোটরগাড়ী চলাচল শুরু করে এবং গত ২০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে ১০০(একশত) বছর পালিত হয়। বিশ্বের প্রথম এ্যাসপিরিন জার্মান রসায়নবিদ ফেলিক্স হফম্যানের বাবা ১৮৯০ সাল থেকে বাতজ্বরে ভুগছিলেন। বাবার কষ্ট দেখে বিজ্ঞানী পুত্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন একটি ব্যাথানাশক ওষুধ তৈরীর চেষ্টা চালান। অবশেষে ১৮৯৭ সালে উইলো গাছের বাকল থেকে নিস্কাশিত স্যালিসাইলিক এসিড থেকে তৈরী করেন অ্যাসপিরিন নামের ব্যাথানাশক। অবশ্য দুই হাজার বছর ধরে ব্যথা নিবারণের জন্য উইলো আর বার্চ গাছের বাকলের সুনাম ছিল। তবে প্রথম বিশুদ্ধ স্যালিসাইলিক এসিড নিস্কাশন করেন ইতালির বিজ্ঞানি পিরিয়া, ১৮৩৮ সালে। ১৮৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর, নিউইয়র্ক সিটির লিবার্টি দ্বীপে স্ট্যাচু অব লিবার্টি স্থাপন করা হয়। প্রকৌশলী ঃ ফ্রেডেরিক অগাষ্ট বার্থোন্ডি। কাঠামো প্রকৌশলী ঃ গুস্তাভ আইফেল। পাদমূলের প্রকৌশলী ঃ রিচার্ড মরিচ হান্ট। অবস্থান ঃ লিবার্টি দ্বীপ, নিউইয়র্ক সিটি। বিস্তৃতি ঃ ১২ একর। তদারককারী প্রতিষ্ঠান ঃ যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্ক সার্ভিস। ফ্রান্সে নির্মাণ শুরু ঃ ১৮৭৫। নির্মাণ শেষ ঃ জুন, ১৮৮৪। পরিবহন সম্পন্ন ঃ ১৮৮৫। পরিবহনকারী জাহাজ ঃ ফরাসি ফ্রিগেট ইসেরে। পরিবহনের সময়ে টুকরোর সংখ্যা ঃ ৩৫০। স্থাপন ঃ ২৮ অক্টোবর, ১৮৮৬। জাতীয় সৌধ হিসেবে স্বীকৃতি ঃ ১৫ অক্টোবর, ১৯২৪। পাদমূলের উচ্চতা ঃ ৮৯ ফুট। পাদমূল থেকে টর্চের উচ্চতা ঃ ১৫১ ফুট ১ ইঞ্চি। ভিত্তি ঃ ৬৫ ফুট। মাটি থেকে টর্চের উচ্চতা ঃ ৩০৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। গোড়ালি থেকে মাথার উচ্চতা ঃ ১১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। হাতের দৈর্ঘ্য ঃ ১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। তর্জনী ঃ ৮ফুট ১ ইঞ্চি। এক কান থেকে আরেক কান ঃ ১০ ফুট। দুই চোখের দূরত্ব ঃ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। নাক ঃ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। কোমর ঃ ৩৫ ফুট। মুখ ঃ ৩ ফুট। মুর্তিতে ব্যবহৃত তামা ঃ ২৭.২২ মেট্রিক টন। ব্যবহৃত স্টিল ঃ ১১৩.৪ মেট্রিক টন। মোট ওজন ঃ ২০৪.১ মেট্রিক টন। হাতে ধরা বই ঃ দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ৭ ইঞ্চি, চওড়া ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চি, পুরুত্ব ২ ফুট। বইয়ে লেখা ঃ ৪ জুলাই, ১৭৭৬। মুকুটে জানালার সংখ্যা ঃ ২৫। মুকুটে কাঁটার সংখ্যা ঃ ৭। সাত কাঁটার অর্থ ঃ সাত মহাদেশ (মতান্তরে সাত সাগর)।
১৮৮৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, আমেরিকায় জার্মান অভিবাসী এমিল বার্লিনার গ্রামোফোন আবিস্কার করেন। ১৮৯৪ সালের ২৩ জুন, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৪ সালে ইংল্যান্ডের রানি মেরি এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। বাবা রাজা পঞ্চম জর্জ। শিশুটির নাম রাখা হলো এডওয়ার্ড। ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা। সেভাবেই বড় হচ্ছিলেন তিনি। সব ওলট-পালট হয়ে গেল ১৯৩০ সালে দুইবারের বিবাহিত মার্কিন মহিলা মিসেস সিম্পসনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। তাঁর মধ্যেই এডওয়ার্ড আবিস্কার করেন নিজের চূড়ান্ত গন্তব্য। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে এ মহিলাকেই তিনি বিয়ে করবেন। বাধা হয়ে দাঁড়ান গির্জা। বলা হলো, বিবাহিত মিসেস সিম্পসনকে বিয়ে করতে হলে এডওয়ার্ডকে সিংহাসনের মায়া ছাড়তে হবে। এডওয়ার্ড জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন, একদিকে সূর্য অস্ত যায় না এমন সাম্রাজ্য, আর অন্যদিকে সাধারণ এক নারী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁকে একটি বেছে নিতে হবে। তিনি সাধারণ নারীটিকেই বেছে নিলেন এবং ১৯৩৬ সালে লেডি সিম্পসনের হাত ধরে বাকিংহাম প্রাসাদ ছেড়ে সাধারণ মানুষের মতো রাস্তায় নেমে এলেন। ১৮৯৫ সালের ৮ নভেম্বর, দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এবং গণিত আর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক উইলিয়াম রন্টজেন ক্যাথড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময় এক্স-রে মেশিন আবিস্কার করেন। তিনি এর নাম দেন এক্স-রে বা এক্স-রশ্মি দেন। ১৮৯৬ সালের ৫ জানুয়ারি, সর্বপ্রথম এক্সরে মেশিন প্রদর্শণ করেন।
১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর, বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল তার সকল সম্পত্তি উইলের মাধ্যমে ‘নোবেলম্ব’ পুরস্কারের জন্য দান করে যান। ১৯০১ সালের ১০ ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের অন্তিম ইচ্ছে অনুযায়ী নোবেল পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর, ফ্রান্সের দুইভাই সিনেমা আবিস্কার করে। ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর, প্যারিসে বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র জনসম্মুখে প্রদর্শিত হয়। ১৯০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর, বিশ্বের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি ‘দি স্টোরি অব দি কেলিং গ্যাং’ সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে প্রদর্শিত হয়। ১৮৯৬ সালে গ্রীসে প্রথম বিশ্ব অলিমúিক শুরু হয়। ১ম অলিম্পিক ঃ ১৮৯৬ (এথেন্স, ৬ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত)। ১৮৯৬ সালে ১৩টি দেশের ৩০০ অ্যাথলিট অংশ নিয়েছিলেন ৯টি ইভেন্টে। ২০০৪ সালের ১৩ আগষ্ট, আবার ১০৮ বছর পর এথেন্সে ২৮তম অলিম্পিকের আসর শুরু হচ্ছে। এখন দেশের সংখ্যা বেড়ে ২০২টি, ৩৭টি ইভেন্টে-এ ৩০১টি স্বর্ণ পদকের জন্য লড়াইয়ের সংখ্যা ১২(বার) হাজারেরও বেশি অ্যাথলেট। ম্যারাথন দৌঁড়ের অর্থ ৪২.১৯৫ কিলোমিটার দূরত্বকে বুঝায়। ৪২.১৯৫ কিলোমিটার সমান ২৬.৩৭ মাইল। ১৮৯৭ সালের ৮ জুলাই, আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে প্রথমবারের মতো অপরাধী শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৯৭ সালের ২২ মে, টেমস নদীর তলদেশে ব্ল্যাকওয়াল টানেল আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়া হয়। ১৮৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর, পিয়েরে কুরি ও মেরি কুরি রেডিয়াম আবিস্কার করেন। বিশ্বের প্রথম তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা প্রথম তেজস্ক্রিয় মৌল পোলোনিয়ামের আবিস্কারক মেরি কুরি (১৮৬৭-১৯৩৪)। তাঁর দেশ পোল্যান্ডের নাম অনুসারেই এ মৌলটির নামকরণ করা হয়েছে। তিনি এবং তাঁর ফরাসি স্বামী পিয়েরে কুরি ১৮৯৮ সালে প্যারিসে খনিজ পিচবেøন্ড থেকে পোলোনিয়াম নিস্কাশন করেন। পরে, একই বছর, তিনি রেডিয়াম নামের আরেকটি তেজস্ক্রিয় মৌল আবিস্কার করেন। ১৮৯৯ সালের ৯ অক্টোবর, লন্ডনে প্রথম পেট্রোলচালিত মোটর যান চলাচল শুরু।
১৯০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লিভারমুরে একটি ফায়ার হাউসে (দমকলবাহিনীর কার্যালয়) গেলে এ বাল্বের দেখা মিলবে। ওই ফায়ার হাউসের ইঞ্জিনঘরে প্রায় ১৮ ফুট উঁচুতে ১৯০১ সাল থেকে জ্বলছে এ বাল্ব। শতবর্ষী মানুষ. শতবর্ষী গাছ, শতবর্ষী ভবনের কথা শোনা যায়। কিন্তু শতবর্ষী বৈদ্যুতিক বাল্ব আছে কি, যা দিনের পর দিন জ্বলছে? আছে। শতবর্ষী এক বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে তো জ্বলছেই। এ বাল্বটি ১৯৭৬ সালে মাত্র ১০ মিনিটের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। ২২-০৬-২০১১ তারিখও বাল্বটি জ্বলছে। ১৯০২ সালে বিশ্বের প্রথম ফ্যাক্স জার্মানির আর্থার কর্ন এক ধরনের ফটোটাইপ পদ্ধতির আবিস্কার করেন এবং দুই বছরের চেষ্টার পর ১৯০৪ সালে মিউনিখ থেকে নুরেমবার্গে ছবি পাঠাতে সফল হন। এর মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের গ্রাহক যন্ত্রে বর্ণ কিংবা ছবি পাঠানো যেত। আন্তর্জাতিকভাবে সর্বপ্রথম ফ্যাক্স ব্যবহার করে লন্ডনের দৈনিক মিরর পত্রিকা। পত্রিকাটি প্যারিস থেকে ফ্যাক্সযোগে প্রাপ্ত ছবি ছাপে ১৯০৭ সালে। ১৯০৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের নির্মিত উড়োজাহাজের সফল উড্ডয়ন ঘটান। এরা দুই-ভাই বিমান উৎপাদন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। ১৯০৪ সালের ২২ জুন, আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) জন্ম। ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে, স্কাউট আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালের আগষ্ট মাসে স্কাউটের শতবর্ষ পূর্তি পালিত হয়। ১৯০৯ সালের ১১ আগষ্ট, বেতারে বিপদ বার্তা এসওএস-এর ব্যবহার শুরু। ১৯১১ সালের ১৮ ফেব্রæয়ারি, ফরাসী বৈমানিকের পরিচালনায় বিশ্বে প্রথম বিমানে ডাক পরিবহন শুরু। ১৯১১ সালে রোয়াল্ড আমাগুসেন কর্তৃক দক্ষিণ মেরু আবিস্কার। ১৯১২ সালের ২৯ মার্চ, সুমেরু অভিযাত্রী রবার্ট স্কটের মৃত্যু।
১৯১২ সালের ১০ এপ্রিল, সাউদাম্পটন থেকে নিউইয়র্কে যাওয়ার সময় সবচেয়ে বড় ‘টাইটানিক’ জাহাজটি ১৫ এপ্রিল, মধ্যরাতে ২,২০০ জন যাত্রী নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি হিমশৈলে ধাক্কা লাগার পর ‘টাইটানিক’ ডুবে যায়। সে সময় বিলাশবহুল এ ব্রিটিশ জাহাজটির ২২শ’ যাত্রীর মধ্যে ৭শ’ ১১ জনের প্রাণরক্ষা পায়। ১৫০ জন যাত্রীকে স্কয়াড্রন সমুদ্র সৈকতে সমাধী করা হয়। নির্মাতা বিখ্যাত স্টার লাইন কো¤পানী দাম্ভিকতার সাথে বলেছিল-এ জাহাজ কোনদিন ডুববে না এবং এর কোন পরীক্ষামূলক কাজ স¤পন্ন করারও প্রয়োজন নেই। চলে গেলেন টাইটানিকের শেষ সাক্ষী মিলভিনা ডিন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। ৩১-০৫-২০০৯ তারিখ মিলভিনা ডিন ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ারে একটি বৃদ্ধাশ্রমে ঘুমের মধ্যে তিনি মারা গেছেন। ১৯১২ সালের ১৫ এপ্রিল, মিলভিনা ডিনের বয়স ছিল ৬৩ দিন। নাবিকদের ভুলেই টাইটানিক ডুবেছে। ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই, সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর যুদ্ধ ঘোষণা। ১৯১৪ সালের ৩০ জুলাই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু, শেষ হয় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। ১৯১৪ সালে প্রথমবারের মত পাসপোর্টে ছবির ব্যবহার শুরু হয়। ১৯১৪ সালে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ছিল ৫২টি; ১৯৪৬ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪টি; ২০১১ সালে ১৯৩টি। পৃথিবীর দেশের সংখ্যা ২৩৩টি। আর জাতির সংখ্যা হলো ২০০টি। ১৯১৪ সালের ২৭ নভেম্বর, বৃটেনে প্রথম বারের মতো মহিলা পুলিশ নিয়োগ।
১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রথম ট্যাংক এবং বিমানও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনো ক্যামেরা না থাকায় সেনারা নিজ হাতেই যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি আঁকত-কীভাবে কোন পথে তারা সেখানে জড়ো হবে সেটা ঠিক করার জন্য। ১৯১৯ সালের ৩ ফেব্রæয়ারি, লীগ অব নেশনসের প্রথম অধিবেশন শুরু। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ফরাসি উড়োজাহাজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফারমান বিশ্বের প্রথম বিমান যাত্রীসেবা উড়োজাহাজে করে সর্বপ্রথম আকাশ পথে যাত্রী পরিবহণ করে। কিন্তু এর আগে আকাশপথে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু জীবিকার তাগিদে ভ্রমণ কিংবা বাণিজ্যের প্রয়োজনে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছেন। ১৯১৯ সালের ২২ মার্চ, প্যারিস ও ব্রাসেলসে সাপ্তাহিক বিমান সার্ভিস উদ্ধোধনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম আন্তজার্তিক বিমান সার্ভিস চালু হয়। ১৯১৯ সালের ৬ জুলাই, বিশ্বের প্রথম বিমান-ব্রিটিশ আর-৩৪ এর আটলান্টিক অতিক্রম। ১৯১৯ সালে জন এলকক ও আর্থার ব্রাউন প্রথম বিরতিহীন বিমান চালিয়ে আটলান্টিক অতিক্রম করেন। এতে তাঁদের সময় লেগেছিল প্রায় সাড়ে ১৬ ঘন্টা। ১৯১৯ সালের ২৫ আগষ্ট, লন্ডন ও প্যারির মধ্যে প্রথম বিমান চলাচল শুরু হয়। ১৯১৯ সালের ১৯ এপ্রিল, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ২৮ এপ্রিল, লীগ অফ নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তির মধ্যে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
১৯২০ সালে পিটার্সবার্গ শহরে পৃথিবীর প্রথম নিয়মিত বেতার কেন্দ্র চালু হয়। ১৯২২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, ইংল্যান্ডে মার্কনির নিয়মিত বেতার স¤প্রচার শুরু। ১৯২৬ সালে বিশ্বের প্রথম হৃদযন্ত্রের পেসমেকার স্থাপন করা হয়েছিল। এর আবিস্কারক ছিলেন ক্রাউন স্ট্রিট ওমেনস হসপিটালের এক নাম না জানা ডাক্তার। মূলত এর প্রশ্নবিদ্ধ নৈতিকতা ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ভয়ে নাম প্রকাশ করেননি। আজও আমরা তাঁর আবিস্কারের সুফল ভোগ করছি। কিন্তু মূল আবিস্কারক তাঁর নাম প্রকাশ না করায় তিনি যন্ত্রটি আবিস্কারের স্বীকৃতিও পাননি। ১৯২৬ সালে বিশ্বের প্রথম টেলিভিশন আবিস্কার করেন স্কটিশ বিজ্ঞানী জন লুগি বেয়ার্ড ও তার দল সর্বপ্রথম লন্ডনে জনসমক্ষে টেলিভিশন স¤প্রচারে সফল হন। তখনকার ছবি ছিল সাদাকালো। তবে একই বছর তারা রঙিন ফিল্টার ব্যবহার করে টেলিভিশন রঙ্গিন ছবি স¤প্রচারেও সক্ষম হন। রাশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ, ব্রিটেন ও আমেরিকার বেশ কিছু বিজ্ঞানী একই সময় টেলিভিশন তৈরীর জন্য কাজ করছিলেন। তবে সর্বপ্রথম স্কটিশ উদ্ভাবক জন লুগি বেয়ার্ড ও তাঁর দল ১৯২৬ সালে টেলিভিশন আবিস্কার করেন। ১৯২৯ সালে বিবিসি‘র প্রথম পরীক্ষামূলক টেলিভিশন স¤প্রচার শুরু। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্ব কাপ ফুটবল খেলা শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের ৩০ জুলাই, বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘পেঙ্গুইন’ প্রথম বইয়ের প্রকাশনা উৎসব পালন করে। ১৯৩৬ সালের ২৫ মে, নিগ্রো ক্রীড়াবিদ জেসি ওয়েনস বার্লিন অলিম্পিকের ৫টি বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিনে টেলিভিশনে একটি ফুটবল ম্যাচ প্রথমবারের মত দেখায়।
১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ব হয় জার্মানীর পোলান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে; শেষ হয়-১৯৪৫ সালের ৯ মে, জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বিশ্বব্যাপী বিজয় উৎসব পালিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর, জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ৭০তম বার্ষিকীতে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল জার্মান টেলিভিশনে বলেন, ‘জার্মানি পোলান্ডে হামলা চালিয়েছে, জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছে। আমরা বিশ্বের অন্তহীন দুর্ভোগের কারণ ছিলাম। যার ফলাফল ছিল ছয় কোটি মানুষের মৃত্যু।’ বিবিসি ও এএফপি। ১৯৩৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু, শেষ হয় ০৯-০৮-১৯৪৫ তারিখ। ১৯৪১ সালের ১ জুলাই, সর্বপ্রথম টেলিভিশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় ২০ সেকেন্ডে নয় ডলার দরে। ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বিশেষত যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনকে সামনে রেখেই জাতিসংঘের প্রস্তাবে বিশ্বব্যাংক বা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এশিয়া এবং আফ্রিকান দেশগুলো বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন সহায়তা না পেলেও ১৯৬০-এর দশক থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন ঋণ সহায়তা স¤প্রসারিত হয় এবং আশির দশক থেকে বিশ্বব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের কথা বলে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক ঋণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৪ সাল থেকে বিবিসির খবর সারা পৃথিবীব্যাপী প্রচার করা হয়।
১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট, জাপানের হিরোশিমা নগরীতে ‘‘লিটল বয়’’ নামে ২০ হাজার টনের পারমাণবিক বোমার আঘাত হেনেছিল আমেরিকা। ৬ আগষ্ট, হিরোশিমা দিবস। হিরোশিমা-আক্রমণের আগে লোকসংখ্যা-দুই লাখ ৫৫ হাজার। আহত-৬৯ হাজার-তাৎক্ষণিক মৃত্যু-৬৬ হাজার-পরবর্তী সময়ে মৃতের সংখ্যা (১৯৪৫ সালের শেষ পর্যন্ত) ৭৪ হাজার। মোট মৃত্যু (১৯৫০ পর্যন্ত) প্রায় দুই লাখ। ১৯৪৫ সালের ৯ আগষ্ট, জাপানের নাগাসাকিতে ‘‘ফ্যাট ম্যান’’ আমেরিকার দ্বিতীয় আণবিক বোমা বর্ষণ। নাগাসাকি-আক্রমণের আগে লোকসংখ্যা-এক লাখ ৯৫ হাজার। আহত-২৫ হাজার। তাৎক্ষণিক মৃত্যু-৩৯ হাজার-পরবর্তী সময়ে মৃতের সংখ্যা (১৯৪৫ সালের শেষ পর্যন্ত) ৪১ হাজার। মোট মৃত্যু (১৯৫০ পর্যন্ত) প্রায় ৮০ হাজার। ১৯৪৫ সালে জাতিসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালের ৩ অক্টোবর, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর, জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর, ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ‘আই.এল.ও.’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সাল থেকে বিশ্বে প্রথম বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে, নেপালের শেরপা তেনজিং নোরগেকে নিয়ে ও নিউজিল্যান্ডের পর্বতারোহী স্যার এডমন্ড হিলারি সর্বপ্রথম পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেষ্ট জয় করেন। শুক্রবার (১১-০১-২০০৮ তারিখ) এভারেষ্ট প্রথম বিজয়ী স্যার এডমন্ড হিলারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকল্যান্ডের একটি হাসপাতালে মারা গেছেন।
১৯৫৫ সাল থেকে প্রতিবছর বার্ষিকী হিসেবে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবাদ সংকলণ করে যে বই সেটিই ‘‘গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস’’ নামে পরিচিতি। বিশ্ব রেকর্ড করেছে এমন রেকর্ড এ বইয়ে স্থান পায়। বিশ্বের ৩১টি ভাষায় গিনেস বুক অণুদিত হয়। গিনেস বুকের হেড অফিস লন্ডনে। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর প্রতিষ্ঠা। ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, দারিদ্র্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আসন্ন সিঙ্গাপুর সম্মেলনকে সামনে রেখে ০৪-০৯-২০০৬ তারিখ এক সেমিনারে বক্তারা দারিদ্র্য বিমোচনে এ দু’টি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার ভূমিকা ও কর্মকান্ডের কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯৬০ সালে বিশ্বের প্রথম মোবাইল ফোন সার্ভিস (প্রথমদিককার মোবাইল ফোনগুলো প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের কাজের একটা বিশেষ সহায়ক যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হতো) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সর্বসাধারণের জন্য সর্বপ্রথম-এর প্রচলন হয়। সেবারই প্রথম ফ্রান্সের সরকারি রেল পরিবহন সংস্থা তাদের এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোয় সম্ভান্ত যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন সরবরাহ শুরু করে। ১৯৬০ সালের ২০ জুলাই, সিংহলের মিসেস শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে বিশ্বের সর্বপ্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৬৩ সালের ১০ জানুয়ারি, লন্ডনে বিশ্বের প্রথম পাতাল রেল চালু হয়।
১৯৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ও স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ছোট ল্যাবে দুটো কমপিউটারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭০ সালে এর নাম দেয়া হয় ইন্টারনেট। ১৯৭২ সাল নাগাদ তা দাঁড়ায় ৩২টিতে। পরবর্তীতে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে নেটওয়ার্কটি পুর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব জুড়ে। ১৯৭১ সালের ১৩ জুন, অস্ট্রেলিয়ার জেরাতিন ব্রডরিক একসঙ্গে ৯টি শিশু জন্ম দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে ৫টি পুত্র ও ৪টি মেয়ে। ১৯৭৫ সালে বিশ্ব কাপ ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। ১৯৭৬ সালের ২০ জুলাই, মার্কিন নভোযান ভাইকিং মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করেন। ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে-মন্ট্রিল অলিম্পিকের আগ পর্যন্ত জিমনেস্টিকসে কোনো পুরুষ কিংবা মহিলা প্রতিযোগীই পূর্ণ দশ বা পারফেক্ট টেন স্কোর করতে পারেননি। তার পরই এল চার ফুট ১১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য আর ৮৬ পাউন্ড ওজনের এক বালিকা-নাদিয়া কোমানিচি। ১৪ বছরের এ রোমানিয়ান প্রতিযোগী বিচারকদের এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেললেন যে তাঁরা বাধ্য হলেন, অলিম্পিক ইতিহাসের প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে নাদিয়াকে পারফেক্ট টেন বা দশে দশ দিতে। এ আসরেই আরও ছয়বার পারফেক্ট টেন স্কোর করলেন এ বিস্ময় বালিকা। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই, মাতৃগর্ভের বাইরে প্রথম নবজাতক ভ্রণ শিশুর জন্ম। ১৯৭৮ সালে বিশ্বের প্রথম সিডি জাপানের সনি করপোরেশন ও হল্যান্ডের ফিলিপস কোম্পানি যৌথ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি উদ্ভাবিত হয়। সিডি তৈরির প্রযুক্তি উন্নয়ন ১৯৭৮ সালে সম্পন্ন হলেও ১৯৮২ সালে জাপানের খোলাবাজারে এটি বাণিজ্যিকভাবে বিপণন শুরু হয়। সিডিতে ধারণকৃত গান শোনার যন্ত্রও বাজারে ছাড়া হয় একই সময়ে। সিডি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ডের জায়গা দখল করে নেয়।
১৯৮১ সালে পৃথিবীতে প্রথম এইড্স বা এইচ. আই. ভি’র জীবানু ধরা পড়ে। ১৯৮২ সালে গিনেস রেকর্ড অনুযায়ী পৃথিবীর দীর্ঘজীবী প্রাণী ছিল ২২০ বছর বয়সী একটি ঝিনুক। অবশ্য বেসরকারিভাবে আইসল্যান্ডের জাদুঘরে আরও একটি ঝিনুকের সন্ধান পাওয়া যায়, যার বয়স ছিল ৩৭৪ বছর। তবে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বয়সী প্রাণী হচ্ছে মিং, যার বয়স আনুমানিক ৪০৫ থেকে ৪১০ বছর। ছোট্ট টেপ রেকর্ডার আকৃতির এ সামুদ্রিক ঝিনুকটির খোঁজ পাওয়া গেছে আইসল্যান্ডের সমুদ্র উপকুলে। ধারনা করা হয়, চীনে যখন রাজতন্ত্র, তখন এর জন্ম। রানি প্রথম এলিজাবেথের শাসন এবং শেক্সপিয়ারকে নাটক ওথেলো ও হ্যামলেট লিখতে দেখতে দেখতে কেটেছে তার শৈশব। তবে মিং’ই সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকার রেকর্ড অর্জন করেছে-এ পৃথিবীতে। ১৯৮৫ সালের ১৯ জুলাই, ইংল্যান্ডে একটি ঘোড়া ৩০-জন মানুষকে টেনেছিল। ১৯৮৫ সালের ৩০ জুলাই, ইত্তেফাক পত্রিকার রিপোর্ট-জাতিসংঘ তথ্য স্বীকৃতি, বিশ্বের যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় উহার অর্ধেক নারীর পরিশ্রমের ফসল। ১৯৮৭ সালের ৩ ডিসেম্বরের রিপোর্ট-পৃথিবীতে ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার প্রজাতির পাখি এবং ২ কোটি ৫০ হাজার প্রজাতির বৃক্ষের জন্ম হয়েছে। তারমধ্যে ৮,৫৮০ প্রজাতির পাখি এবং ১০,০০০ প্রজাতির বৃক্ষ বেঁচে আছে। ১৯৮৮ সালের ৫ জুনের রিপোট-বিশ্বে পুরুষ-স্ত্রীলোকের অনুপাত ৪৮ ঃ ৫২। ১৯৮৮ সালের ৫ আগষ্টের সংবাদ ঃ মহিলারা পৃথিবীতে ৬৭% কাজ করে এবং পুরুষরা বাকি ৩৩% কাজ করে। তবু পুরুষ বলে যে, মহিলারা কোন কাজই করে না। ১৯৯৮ সালের ২৭ জুনের তথ্য ঃ পারমাণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক বোমা দারিদ্র। ১৯৯৮ সালের ২২ অক্টোবরের তথ্য-বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দেয়, ৬৯(উনসত্তর) সন্তানের জননী মস্কোর বাসিন্দা। ২০০৩ সালের ৬ মে, হ্যালো ইন্ডিয়াতে দেখানো হয় যে, ভারতের মনিকা শর্মা ১১ মাসে ৮২ কেজি ওজন কমান। বিশ্বে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস আছে যে, ১১ মাসে ৫০ কেজি ওজন কমানোর রেকর্ড। সে বর্তমানে রোজ ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার রাস্তা হাটাহাটি করে। ২০০৬ সালের ১ আগষ্ট, ভারতের উত্তর প্রদেশের নীলাসর গ্রামের বিরমা রাম ৮৮ বছর বয়সে পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন।
২৫০০-২০০০ খৃষ্টপূর্ব ভারতে বৈদিক সাহিত্যের চর্চা। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে হিন্দু ধর্মের জন্ম। ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব আলেকজান্ডারের ভারত-অভিযান। ৩২২ খৃষ্টপূর্ব চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ। ২৭৩ খৃষ্টপূর্ব অশোকের সিংহাসনে আরোহণ। ৫৭ খৃষ্টপূর্বের ২৩ ফেব্রæয়ারি, রাজা বিক্রমাদিত্য শক রাজাকে পরাজিত করেন। ৩১৯ সালের ২৬ ফেব্রæয়ারি, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাটলীপুত্রের সম্রাট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ। ৩৮০ সালে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন লাভ। ৬২৯ সালে হিউ-এন-সাং-এর ভারতে আগমন। ৬৩২ সালের ১৬ জুন, ইরান ও ভারতীয় পারসিক সমাজে প্রচলিত জোরাস্তীয় পঞ্জিকা প্রবর্তিত হয়। ৭১২ সালের ২ জুলাই, রাওয়ার যুদ্ধ, মুহাম্মদ বিন ইবনে কাশিমের সিন্ধু বিজয়। ৭১২ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। এ দীর্ঘসময় তাদের অতিবাহিত হয়েছে মুসলিম ও ইংরেজ শাসকদের অধীনে। ৭১২ সালের ২ জুলাই থেকে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলমানের শাসন ছিল। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত ছিল ভারতবর্ষে ইংলিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজ রাজ শক্তির শাসন। ১৯৪৭-পূর্ব দীর্ঘ এ দু’কাল মিলে ১২শ’ বছরের অধিককাল ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। ১০৫২ সালে রাজপুতরা লালকেল্লা (জবফভড়ৎফ) নামে দুর্গ শহর গড়ে তুলেছিল দিল্লীতে। ১১৯২ সালে মুসলিম সুলতান শেহাবউদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরীর সেনাপতি সে দুর্গ অধিকার করে কায়েম করেন সুলতানী শাসন। ১৩৯৮ সালে দুর্ধর্ষ আক্রমণকারী চেংগীজ খাঁ’র আক্রমণে ও লুন্ঠনে লন্ডভন্ড হয় দিল্লী। ১৬৩৮ সালে নির্মাণ করেন চারদিক ঘিরে সুউচ্চ প্রস্তর প্রাচীর এবং প্রাচীর অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করেন সুবিখ্যাত লালকেল্লা (জবফভড়ৎফ)। রেডফোর্ডের সম্মুখভাগে, অদূরে ১৬৪৪-৫৮ সালে সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেন এ জামে মসজিদ। ১৬৪৮ সালের ১৩ মে, মুঘল সম্রাট শাহজাহান দিল্লীতে লালকেল্লার নির্মান কাজ শুরু করেন। ১৬৩১ সালে শাহজাহানের প্রিয়তম স্ত্রী মমতাজমহল সন্তান জন্মদানের সময় মারা গেলে আগ্রার যমুনা নদীর তীরে তাঁকে সমাহিত করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় তাজমহল গড়ার। আজও তাজমহল দুনিয়াজুড়ে প্রতীক হয়ে আছে প্রেম-ভালোবাসার। তাজমহল পরিদর্শনে এখন টিকিটের প্রয়োজন হয়। ১৬৫৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, তাজমহল নির্মাণ করা হয়। ১৬৫১ সালে শাহ্ সুজা ইংরেজদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যে সনদ দান করেন তা-ই তার শেষ পরিণতি। ১৭৩৯ সালে নাদীর শাহ কর্তৃক লুন্ঠিত হয় দিল্লী। তিনি ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর মনি নিয়ে যান নিজ দেশ পারস্যে। (১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ মানে প্রথম আজাদী লড়াই ব্যর্থ হওয়ার মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ ব্রিটিশ শাসন। ১৯১২-১৯৩১ পর্যন্ত পুরানা দিল্লীই থাকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। নয়াদিল্লী নির্মাণ সমাপ্ত হলে সেখানে হয় রাজধানী স্থানান্তরিত। যে স্থানটিতে ক্রীড়াকেন্দ্র সেখানে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দিল্লী দরবার বসেছিল ১৮৭৭ সালে, ১৯০৩ সালে ও ১৯১১ সালে। ওই লালকেল্লায় ১৮৭৭ সালে ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ঘোষণা করা হয়েছিল ভারতসম্রাজ্ঞী। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট, ইউনিয়ন জ্যাক হল চিরদিনের জন্য অবনমিত, অপসারিত। উড্ডীন হল স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা)। ১১৯৩ সালে সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মসজিদ। তার নাম দেন কুওতুল ইসলাম। এর ১৬০ ফুট দূরে শুরু করেন একটি মিনার নির্মাণের কাজ। কিন্তু শেষ করে যেতে পারলেন না কুতুবউদ্দীন। তাঁর ইন্তেকালের পর সুলতান হলেন তাঁর জামাতা ইলতুতমিশ। তিনিই সমাপ্ত করলেন নির্মাণ কাজ (১২৩১-৩২ খ্রি.) এবং তাঁর পীর হযরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর(রহ.) নামানুসারে নামকরণ করলেন ‘কুতুবমিনার’। স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন কুতুবমিনার। পৃথিবীর এ জাতীয় সুন্দরতম সৌধরাজির মধ্যে এটি একটি। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম স্মৃতিসৌধসমূহের মধ্যে কুতুবমিনার অন্যতম। এর উচ্চতা ২৪০ ফুট।
৯ম শতকের পূর্বে ঢাকাতে মানুষের বসবাস গড়ে উঠেনি। ইতিহাসবিদদের চোখে-সেদিনের ‘ডবাক’ই আজকের ঢাকা। সাড়ে পাঁচশ’ বছরের প্রাচীন জনপদ ‘ঢাকা’ আজ এক বিশাল নগরী। ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ১৩-কিলোমিটার উত্তরে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত এ মহানগরীর উত্থানের পেছনেও রয়েছে বিস্তৃত ইতিহাস। ১৪৩৩ সালে প্রথম ঢাকা মান্দা এলাকায় গণেসের ছেলে জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ-এর কর্মচারী শিকদার এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ মসজিদটি ঢাকার প্রথম মসজিদ। ১৪৫৬ সালে ঢাকায় দ্বিতীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয় ‘‘নারিন্দায় বিনাত বিবি মসজিদ’’। তাঁর নাম মুসাম্মৎ বখত বিন। ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার নারিন্দায় এ মসজিদটি মরহামত কন্যা নির্মাণ করেন। বিনাত বিবির মসজিদের আগে ঢাকায় একটি মসজিদ ছিল। ১৪৫৬ সালে নারিন্দায় বিনত বিবির মসজিদ নির্মাণের পূর্ব থেকেই মুসলমানরা ঢাকা নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। যতীন্দ্রমোহন রায়ের লেখা ‘ঢাকার ইতিহাস’ বৃহত্তর ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, ঢাকা নগরীতে অন্তত ১৪৫৬ খ্রির্ষ্টাব্দের আগে থেকেই মুসলমানগণ বসতি স্থাপন করেছেন। (১২৮২ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পুত্র সুলতান নাসির উদ-দীন ঢাকার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন)। ১৬১০ সালে ইসলাম খাঁ কর্তৃক সোনারগাঁ থেকে রাজধানী বর্তমান ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং ঢাকা মোঘল রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু। ১৬২০ সালে মগ রাজাদের বন্দী করা হয়েছিল। এরা আরাকানী, এদেরই নামানুসারে ঢাকার মগবাজারের নামকরণ করা হয়। ১৬২৬ সালে মিডফোর্ড হাসপাতালের লেডিজ হোস্টেলের নিকট বুড়িগঙ্গা নদীর পারে ঢাকা শহরের ২য় মসজিদ তৈরী হয়। ১৬২৬ সালে “ছোটকাটারা” ও “বড়কাটারা”র প্রাসাদ তৈরী করা হয় বাদশা জাহাঙ্গীরের ঢাকা আগমণ উপলক্ষে। ১৬৪১ সালের ১৬ মার্চ, বঙ্গের সুবাদার শাহজাদা সুজা ঢাকায় ‘বড়কাটারা’ নামে বিশাল সরাইখানা নির্মাণ করেন। ১৬৪২ সালে ঢাকায় হোসনী দালান তৈরী করা হয় (শাহ শুজার নৌ-সেনাপতি মীর মুরাদ নামক এক ব্যক্তি এ ইমারত তৈরী করেছিলেন)। ১৬৪২ সাল থেকে ঢাকায় মহরমের তাজিয়া মিছিল মোঘল সুবাদার শাহ সুজার শাসনামলে-সুবাদারের নৌবাহিনীর তত্ত¡াবধায়ক শিয়া দরবেশ হিসেবে পরিচিতি সৈয়দ মির মুরাদ হজরত ইমাম হোসেন(রা.)-এর স্মৃতিস্মারক হিসেবে পুরান ঢাকায় নির্মাণ করেন হোসেনি দালান এবং এ হোসেনি দালানকে কেন্দ্র করেই শুরু করেন শোক পালন অনুষ্ঠান ও ইমাম হোসেনের প্রতীকী শরাধার অর্থাৎ তাজিয়া-সহযোগে শোভাযাত্রার। ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত হয় ইরান থেকে ধর্মপ্রচারার্থে আগত মুসলমানদের মাধ্যমে। ১৬৪২ সালে (বাংলা ১০৪৯ সালে) শ্যামপুরের ফরিদাবাদ এলাকার ৫৬ নম্বর পশ্চিম জুরাইনে মন্দিরটি অবস্থিত।
১৬৬৪ সালের ১৯ মার্চ, শায়েস্তা খাঁ বঙ্গের সুবাদার হিসেবে ঢাকায় আসেন। বাংলায় চলছিল কৃত্রিম খাদ্য সংকট। সায়েস্তা খাঁ বিভিন্ন রাজ্য পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি নিজের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ইতিহাসে স্থান করে নেন কিংবদন্তি পুরুষ হিসেবে। তৎকালীন মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন মির্জা তালিবকে ‘‘শায়েস্তা খান’’ উপাধিতে ভূষিত করেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮(আট) মণ চাল পাওয়া যেত। জনগণের মনে এখনো ‘‘শায়েস্তা খাঁর আমল’’ কথাটির ব্যবহার হয় জিনিসপত্র সুলভে প্রাপ্তির প্রবাদবাক্য হিসেবে। কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ীর কারণে বাজারে যখন ‘তোঘলিক কারবার’ (তোঘলকের শাসনকাল ছিল ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ শাসনকার্যের সুবিধার্থে ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে মকসুদাবাদে আনেন। এ মকসুদাবাদই পরবর্তীকালে নবাব দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয়।
ওলন্দাজরা-ইউরোপে তখন ভারতের মসলা সোনার চেয়েও দামি। সেই মসলার জন্যই পর্তুগিজদের দেখানো জলরেখা ধরে ভারতে যে দ্বিতীয় ইউরোপীয়দের আগমন, তারা হলান্ডবাসী। ঢাকায় তাদের আগমনের তারিখও অজানা। তারা কুঠি স্থাপন করেছিল মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে, ১৬৬৩ সালে। তেঁজগাওয়ে তাদের একটি বাগানবাড়িও ছিল। ওলন্দাজরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সফল হতে পারেনি। টেলর উল্লেখ করেন ১৭৮৩ সালে ঢাকায় ৩২টি ওলন্দাজ পরিবার ছিল। ইংরেজদের কাছে তারা সহায়-সম্পত্তি তুলে দিয়ে ঢাকার পাঠ চুকিয়ে ফেলেন। নারিন্দায় খ্রিষ্টান কবরস্থানে ১৭৭৫ সালের কুঠিপ্রধান ডি ল্যাংহিটের কবরটিই এখন ঢাকায় একমাত্র স্মৃতিচিহৃ হিসেবে টিকে আছে।
ফরাসিরা-ঢাকায় ফরাসিদের স্মৃতি বহন করছে পুরান ঢাকার ফরাসগঞ্জ এলাকাটি। ঢাকার নায়েম নাজিম নওয়াজিশ খান ১৭২৬ সালে ফরাসিদের গঞ্জ বসানোর অনুমতি দিলে তারা একটি আবাসন গড়ে তোলে ফ্রেঞ্চগঞ্জ নামে। পরে লোকমুখে এর নাম ফরাসগঞ্জ। তবে এর আগেই ফরাসিদের ঢাকায় আবির্ভাব। প্রধানত মসলিন বস্ত্রের ব্যবসা করত তারা। ১৭৪২ সালে ঢাকা শহরে ফরাসিরা প্রথম ফরাসগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তারা ইংরেজদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। পলাশীর যুদ্ধের পর এখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যায়।
পর্তুগিজরা-ইউরোপীয়দের মধ্যে ঢাকায় প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা। ভারতে আসার জলপথ আবিস্কারের কৃতিত্ব তাদেরই। ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে তাঁর জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন ১৪৯৮ সালে। উদ্দেশ্য, ভারতের মসলা হাসিল করা। সেই পথ ধরে পরে ইউরোপের আরও অনেকের আগমন। ১৮৩২ সালে ঢাকায় পর্তুগিজদের বাড়ি ছিল ৪১টি। ইসলামপুর, শরাফতগঞ্জ ও নবাবপুরে ছিল তাদের বসবাস।
ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল ১৬০০ সালে। ঢাকায় উপস্থিতি সম্ভবত ১৬৫৮ সালের দিকে বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তাঁদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয় শহরতলিতে, বর্তমানের তেজগাঁওয়ের খামারবাড়ি এলাকায়। টেলর উল্লেখ করেছেন, ঢাকায় প্রথম ১৬৬৬ সালে ইংরেজদের ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়েছিল। ব্রিটিশরা চেষ্টা করে সুবাদারের কাছাকাছি থাকতে। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে কুঠি স্থানান্তর করে এবং ১৬৭৮ সালে তারা নবাবকে নানা উপঢৌকন দেয়ার মাধ্যমে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভে সমর্থ হয়। এর পরের ইতিহাস তো সবারই জানা।
আর্মেনিয়ানরা-যেমন ফরাশগঞ্জ, তেমনি আরমানিটোলা এবং সেকানকার প্রাচীন গির্জা, পোগজ স্কুল, রুপলাল হাউস ঢাকায় আর্মেনীয়নের স্বর্ণযুগের সাক্ষী দেয়। ঢাকায় গোড়ার গাড়ী চালুর কৃতিত্বও তাদের। ১৭৮১ সালে নির্মিত পুরান ঢাকার আরমানিটোলার আর্মেনি গির্জা। সাড়ে সাত শ ফুট লম্বা চারটি দরজা ও ২৭টি জানালার এ গির্জা কালের প্রহারে আজ কিছুটা মলিন ও জীর্ণ। ওয়াইজের গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায়, ১৮৭২ সালে সারা বাংলায় বসবাসরত ৮৭৫ জন আর্মেনীয়র ৭১০ জন কলকাতায় এবং ১১৩ জন ঢাকায় বাস করত। ১৮৭০ সালে আই. জি. এন. পোগোজের হিসাব অনুযায়ী, ঢাকার আর্মেনীয়দের সংখ্যা ছিল ১০৭, যাদের মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ, ২৩ জন নারী ও ৪৮ জন শিশু। ১৮৮২ সালে আর্মেনিয়ান জি. এন. পোগজের নামে পোগজ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের ১৪ আগষ্ট, ঢাকার শেষ আর্মেনীয়-মিখাইল মার্টিরোসেনের জন্ম ঢাকায়। উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। অনেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে যায়।
গ্রিকরা-লবণ ও পাটের কারবার করে বেশ টাকাকড়ি করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, ইউরোপীয়দের মধ্যে তারাই ঢাকায় এসেছিল সবার পরে। জেমস টেলর উল্লেখ করেছেন, কলকাতার গ্রিক স¤প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আরগিরি ঢাকায় বসবাস করতেন এবং ১৭৭৭ সালে তিনি পরলোকগমণ করেন। তাঁর পরে অনেকেই আসে। তবে ১৮৩২ সালে ঢাকায় ২১টি পরিবার ছিল। রেসকোর্সের পার্শ্বে ছিল তাদের কবরস্থান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে একটি গ্রিক কবর তাদের স্মৃতিবাহী। ঢাকা ছাড়া নারায়নগঞ্জেও গ্রিকদের বসবাস ছিল। সেখানে ১৯৫৬ সালে র্যালি ব্রাদার্স নামের একটি পাটকল চালূ করেছিল র্যালি ভাইয়েরা।
ঢাকায় যেসব কাশ্মীরি ধনে-মানে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, তাঁদের মধ্যে ঢাকার নবাব পরিবার অন্যতম। এই পরিবারের আদি পুরুষ আবদাল হাকিম নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে প্রথমে বসতি স্থাপন করেছিলেন সিলেটে। পরে তাঁরা ঢাকায় আসেন। লবণ ও চামড়ার কারবারে প্রভূত ধনসম্পদ অর্জন করেন। আবদাল হাকিমের ভাই আবদুল্লাহ সিলেট থেকে ব্যবসা গুটিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁর পুত্র হাফিজুল্লাহ আর্মেনীয়দের সঙ্গে যৌথ কারবার করে বিত্তবৈভব বাড়িয়ে তোলেন এবং ১৮১২ সালে বাকেরগঞ্জে জমিদারি ক্রয় করেন। নিঃসন্তান হাফিজুল্লাহর পর উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভাই খাজা আলিমুল্লাহ। তাঁর পুত্র আবদুল গনি। তাঁর পুত্র নবাব আহসানউল্লাহ। তাঁর পুত্র নবাব সলিমুল্লাহ।
চীনা ও অন্যান্যরা-চীনারা ঢাকায় জুতার ব্যবসায় বেশ অগ্রগতি লাভ করেছিল। মিডফোর্ড এলাকায় ছিল তাদের কারখানা। এ ছাড়া তারা লন্ড্রির ব্যবসায়ও নিয়োজিত ছিল। ইরানিরা ঢাকায় আসেন সপ্তদশ শতকে। ইরাকিরা এখানে এসেছিল প্রধানত দিল্লি থেকে। তারা মূলত শিয়া স¤প্রদায়ের। হোসনি দালান ইমামবাড়াকেন্দ্রিক তাঁদের স¤প্রদায়ের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। ঢাকার বেনারসি কারিগরদের পূর্বপুরুষ এসেছিল ভারতের বেনারস থেকে। মিরপুরে তাঁদের প্রধান বসতি। তেলেগু স¤প্রদায়ের ঢাকা আগমন উনিশ শতকে। সায়েদাবাদ এলাকায় এখনো তাদের বংশধরদের বসবাস। রাজধানী হিসেবে ৪০০ বছরের মাইলফলক পেরিয়ে গেল এই শহর। ঢাকার প্রথম সেশন জজ শেরম্যান বার্ড।
১৭৭৭ সালে তৎকালীন ঢাকার জমিদার গোলাম নবী টিলার উপরে সুরম্য একতলা ইমারত নির্মাণ করেন। ১৭৮০ সালে ঢাকার বকশিবাজারের অরফ্যানেজ রোডে মাদরাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৯ সালে তৈরি হয় ঢাকার জনসন রোডে সাধু থোমার ক্যাথেড্রাল গির্জা। ১৮৫৩ সালে ‘বিগ বেন’ ঘড়িটি তৈরি হয়েছিল লন্ডন শহরে। আর সাধু থোমার ক্যাথেড্রালের ঘড়িটি তৈরি করা হয়েছিল ১৮৬৩ সালে। মজা করে কেউ কেউ ক্যাথেড্রালের ঘড়িটিকে ‘ইয়ংগার ব্রাদার অব বিগ বেন’ বলে ডাকেন। মানে বড় বেনের ছোট ভাই আরকি। ঘড়িটি নিয়ে ১৯০৮ সালে দি ইম্পেরিয়াল গ্যাজেট অব ইন্ডিয়ার জুলাই সংস্করণে লেখা হয়, ‘‘চার্চের চুড়ার ঘড়িটি ১৮৬৩ সালে বসানো হয়েছিল, যা কিনা লন্ডনের বিখ্যাত ‘বিগ বেন’-এর কারিগরদের দ্বারা প্র¯ত্ততকৃত।’’ ঘড়িটি নষ্ট এক যুগেরও বেশি সময় ধরে। ১৮২৪ সালের ৪ জুনের ঘটনা লর্ড বিশপ রেজিল্যান্ড হেবার নৌকায় করে সুদূর কলকাতা থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসেছেন। ঢাকায় নেমেই হাতির ডাক শুনে চমকে গেলেন এক বিদেশি অতিথি। ডায়েরিতে ঢাকায় বেড়ানোর স্মৃতি লিখতে গিয়ে হাতির কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। বিশপ হেবার বেশ কদিন ছিলেন ঢাকায়। সদরঘাট হাতির ডাকে উচ্চকিত থাকত। কারণ বুড়িগঙ্গায় গোসল করাতে আনা হতো হাতির পাল। ১৮২৫ সালে ঢাকা জেলের কয়েদিদের লাগিয়ে তিন মাসের পরিশ্রমে রমনার জঙ্গল পরিস্কার করে স্থাপন করা হয় রেসকোর্স ময়দান। ১৮৩১ সালের জানুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যায় লাহোরের বিখ্যাত ঘোড়া সরবরাহকারী জবরদস্ত খান ঢাকায় এসে উপস্থিত। সঙ্গে এনেছেন এক ডজন উচ্চ জাতের আরব্য ঘোড়া। পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অশ্ব অনুরাগের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করে ঢাকায় পেশাদারি ঘোড়দৌড় চালু করেছিলেন তদীয় পুত্র খাজা আবদুল গনি। এ রেসকোর্সের প্রবেশপথে ডস দুটি স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন। এ গেটকে বলা হতো ‘রমনা গেট’। এ গেটটি এখনো অটুট অবস্থায় ঢাকার দোয়েল চত্বরের সামনে দেখা যায়। ১৮৭০ সালে রমনা রেসকোর্স গেট তৈরী হয়। রমনার কালীবাড়িটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন মি. ওয়াল্টার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর আমলে লোহারপুল তৈরী কাজ শুরু হয়েছিল ১৮২৮ সালে। দুই বছর লেগেছিল শেষ হতে। পুল তৈরির জন্য নির্মাণসমগ্রী এনেছিল ইংল্যান্ড থেকে। লোহারপুলের খ্যাতি কর্ণেল ডেভিডসন ১৮৪০ সালে ঢাকায় এসে লোহারপুল দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন পুল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সৌন্দর্যে। ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই, মিস্টার রিজ নামের এক ইংরেজ কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। জেমস টেলরের মতে, ১৮৪০ সালে এ দেশের বস্ত্রশিল্প যখন ধ্বংসের মুখে, তখনো ৩৬ রকম কাপড় বুনন হতো ঢাকায়। এরমধ্যে বেনারসি অবশ্যই ছিল। তবে তা একবারেই স্বল্প পরিসরে। ১৯৪৩ সালে পুরান ঢাকার মালিটোলা, দক্ষিণ মুহসেন্দি, ভজহরি সাহা স্ট্রিটের অল্পকিছু পরিবারই শুধু যুক্ত ছিল বেনারসি বুননের সঙ্গে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারতের বেনারস থেকে ব্যাপকসংখ্যক মুসলিম মোহাজের ঢাকায় এসে যখন বসতি স্থাপন করে, তখন প্রধানত মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে বেনারসি তৈরি হতো।
১৮৪০ সালে কলকাতা থেকে ডেভিডসন ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলেন। লিখেছেন ‘খুব সবুজ এবং সুন্দর রেজিমেন্টের সব অফিসারের মধ্যে একজন বা দু’জন থাকেন সেনানিবাসের ভেতরে। বাকীরা জ্বরে ভুগে বা জ্বরের ভয়ে থাকেন শহরে। সেনানিবাসের পাশে আছে বেশ বড় এক জলাভূমি যা মারাত্মক ম্যালেরিয়ার উৎস।’ পল্টনে আরও বেশ কটি বড় পুকুর ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৮৪০ সালের দিকে জনস্বার্থে সেনানিবাস পুরানা ও নয়াপল্টন থেকে (পর্যায়ক্রমে রমনা থেকে লালবাগ ও মিরপুরে সেনানিবাসটি স্থানান্তর করা হয়েছিল বলে ঐতিহাসিককেরা উল্লেখ করেছেন) সরিয়ে নেওয়া হলেও এর নাম পল্টন থেকে যায়। ১৮৬০ সালে ঢাকা এসে জর্জ গ্রাহাম নামের এক সিভিলিয়ান পল্টনকে দেখেছেন একটা ‘ম্যালেরিয়া পরিত্যক্ত সেনানিবাস’ হিসেবে। এরপর এলাকাটি ঢাকা পৌরসভার অধীনে চলে আসে। মুনতাসীর মামুনের বিবরণ থেকে জানা গেছে, ১৮৭৪ সালে ঢাকায় নবাব খাজা আহসান উল্লাহ ৮০ বিঘা জমি পত্তন নিয়ে বাগান করেন, যা দিলকুশা হিসেবে নতুন নামকরণ হয়। কোম্পানি বাগিচা থেকে সেগুনবাগিচা বলে, তার আদি পরিচয় ছিল ‘কোম্পানি বাগিচা’ নামে। এই খালি মাঠটি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। একসময় ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠলে মাঠটিতে খেলাধুলা শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে সেখানে একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলে সরকার। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে এবং ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় মওলানা ভাসানীর বিখ্যাত জনসভাগুলোর স্থান হিসেবে পল্টন ময়দান বাঙালির রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে পল্টন ময়দান গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে আছে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম এলাকা ভরাট করে তিনি বিরাট মাঠ নির্মাণ করেন। কোম্পানি বাগান থেকে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম। সবুজ পল্টন এখন দূর অতীতের স্মৃতিমাত্র। ১৮৪১ সালের ২০ নভেম্বর, ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০ সালের আগে এলাকাবাসীর পানির সমস্যা সমাধানের জন্য বংশালের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও জমিদার হাজি বদরুদ্দীন ভুট্টো নিজ জমিতে পুকুর খনন করেন ৬-বিঘা জমির ওপর। এ কারণে পুকুরটি ভুট্টো হাজির পুকুর হিসেবেও পরিচিত। এখনো পুকুরটি টিকে আছে। ১৮৫৬ সালের ১৮ এপ্রিল, সাপ্তাহিক ‘ঢাকা নিউজ’-এর প্রকাশনা শুরু। ১৮৫৭ সালের ২২ নভেম্বর, ঢাকার লালবাগ দূর্গে বিপ্লবী সিপাহী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ। ১৮৫৭-এর স্মরণে’’ ১৯৪৭ সালের পর সেই সব শহীদদের স্মরণে ওখানে নির্মিত হয় শহীদ স্মৃতিসৌধ। আজকের বাহাদুর শাহ পার্কের ঐ স্থানটি ছিলো আন্টাঘর ময়দান। ইংরেজ প্রশাসন পরে ভিক্টোরিয়া পার্ক নামকরণ করে।
১৮৫৮ সালের ১ মে, পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গার পারে মিডফোর্ড হাসপাতাল পূর্ববঙ্গের প্রথম আধুনিক চিকিৎসানির্ভর হাসপাতাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৪ সালের শুকনো মৌসুমে হাসপাতালের নির্মাণকাজ শুরু হয়। মাত্র ১৮,৫৩৬ টাকায় ১৮৫৮ সালের মধ্যে ঠিকাদার কোম্পানি একটি প্রধান হাসপাতাল তৈরী করেন। ১৮৭২ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ, হাওড়া হাসপাতাল এবং মিটফোর্ড হাসপাতালে যত ‘মেজর’ অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল তার মধ্যে অস্ত্রোপচার-পরবর্তী মৃতের হার মিটফোর্ড হাসপাতালেই সবচেয়ে কম। ১৮৭৫ সালের ১৫ জুন, মিটফোর্ড হাসপাতালের বলয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের প্রথম মেডিকেল স্কুল, যা পর্যায়ক্রমে আজকের স্যার সলিমূল্লাহ মেডিকেল কলেজ। ১৯২০ সালের ১ এপ্রিল, সরকারি হাসপাতালে পরিণত হয় মিটফোর্ড হাসপাতাল। বর্তমানে ৬০০ শয্যায় উন্নীত হয় মিটফোর্ড হাসপাতালটি। রবার্ট মিটফোর্ড ছিলেন ঢাকা জেলার প্রাদেশিক আপিল ও সার্কিট আদালতের দ্বিতীয় বিচারক। লন্ডনে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ১৭৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ‘রাইটারের’ চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন রবার্ট। ১৮১৬ সালের সেপ্টেম্বরে কালেক্টর হিসেবে ঢাকায় আসেন মিটফোর্ড। রাজনৈতিক ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য হারিয়ে ঢাকা তখন এক গুরুত্বহীন শহর। এ শহরেই ১২টি বছর কাটিয়ে দেন রবার্ট মিটফোর্ড। ঢাকার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ১৮২৮ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। সেখানে আট বছরের মত বেঁচে ছিলেন রবার্ট মিটফোর্ড। ১৮৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্যারিসে বেড়াতে যান মিটফোর্ড, সেখানেই মারা যান। জীবনের শেষ সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৮৫৯ সালের ঢাকা শহরের মানচিত্র রয়েছে জাতীয় আরকাইভসের প্রদর্শনী কক্ষে। ১৮৬০ সালে ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথমে ‘‘কস্যচিৎ পথিকস্য’’ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ‘‘নীলদর্পণ’’। ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ, ঢাকা শহরের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘ঢাকা প্রকাশ’-এর প্রকাশনা শুরু।
১৮৪০ সালে ঢাকা মিউনিসিপাল কমিটি। ১৮৬৪ সালের ১ আগষ্ট, ঢাকা শহরকে পৌরসভা করা হয়। ১৮৬৪ সালের ১ আগষ্টের পর প্রথম চেয়ারম্যান হন এডওয়ার্ড ড্রামন। ‘ড্রামনের’ হাত ধরে আজ আমরা উপনীত হয়েছি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র। ১৮৭১ সালে ঢাকার পাটুয়াটুলিতে গণ-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর ‘‘নীলদর্পণ’’ নাটক প্রযোজনা হয়। ফরাসীরা ১৮৭২ সালে ঢাকার নবাŸ বাড়ির ‘‘আহসান মঞ্জিল’’টি তৈরী করেন। ১৮৭৫ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭৬ সালে ঢাকাতে সার্ভে স্কুল, ১৯০৮ সালে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৪৭ সালের মে মাসে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ১৯৬২ সালের ১ জুন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৮০ সালের পূর্বে ঢাকা শহরে ঘোড়ারগাড়ী ছিলা না। ১৮৮৩ সালে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় সরকারী জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৮৩ সালে ঢাকায় মুসলমান সুহৃদয় সমিতি গঠিত হয়। ১৮৮৫ সালে ঢাকা কোর্টের জন্ম। ১৮৯০ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার প্রথম ঢাকা নগরীর আধুনিক অভিজাত আবাসিক এলাকা ওয়ারীকে গঠন করে।
১৮৯২ সালের ১৬ মার্চ, ঢাকায় তথা বাংলাদেশে যিনি প্রথম আকাশ জয় করেছিলেন, তিনি একজন আমেরিকান নারী, যাঁর নাম জিনেট ভানতাসেল। বিষয়টি আমরা জানতে পারি সিলেটের বিখ্যাত হাসন রাজার ছেলে গনিউর রাজার ডায়েরি থেকে। তিনি সে সময় ঢাকায় ছিলেন ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে ঘটনাক্রমে একটি পুরোনো আলোকচিত্র পাওয়ার কারণে ঢাকায় যে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। জিনেট ভানতাসেল ও তাঁর স্বামী পি. এ. ভানতাসেলকে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে বেলুনে চড়ার জন্য নবাব আহসানউল্লাহ চুক্তিবদ্ধ করেন। ১৮৯২ সালের ১০ মার্চ, তাঁরা ঢাকায় আসেন এবং ১৬ মার্চ জিনেট বেলুনে করে বিকেলে বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে আকাশে উড়েন এবং কথা ছিল বেলুন ছয় হাজার ফুটের ওপরে ওঠারপর প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেবেন নবাববাড়ির ছাদে নামার উদ্দেশে। কিন্তু বাতাসের তীব্র বেগের কারণে বেলুন ভাসতে ভাসতে শাহবাগে নবাবের বাগানবাড়ির একটি ঝাউগাছে আটকে যায় এবং জিনেট ১৫ থেকে ২০ ফুট ওপরে প্যারাসুটের সঙ্গে ঝুলতে থাকেন। এ সময় ঢাকার এক ইংরেজ পুলিশ কর্মকর্তা তিনটি বাঁশ বেঁধে তার সাহায্যে জিনেটের নেমে আসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নিচে নেমে আসার সময় বাঁশের বাঁধন আলগা হয়ে গেলে জিনেট নিচে পড়ে আঘাত পান। প্রায় অচেতন জিনেট এরপর প্রচন্ড জ্বরে ভুগে ১৮ মার্চ দুপুর একটায় মৃত্যুবরণ করেন। বিকেল চারটায় জিনেটকে ঢাকার নারিন্দায় খ্রিষ্টান গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। ঢাকার আকাশে বেলুনে উড্ডয়নের দু-একদিন আগে থেকেই ঢোল পিটিয়ে ঢাকাবাসীকে এ বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ঢাকার প্রথম আকাশচারী।
১৯০১ সালে আহসান মঞ্জিলে জেনারেটর দ্বারা প্রথম বিদ্যুতের বাতি জ্বালানো হয়। ১৯০২ সালে ইংরেজরা ঢাকায় প্রথম জগন্নাথ কলেজে সিনেমা দেখায়। ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রæয়ারি, ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন ঢাকায় ‘কার্জন হলের’ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের নামে কার্জন হল তৈরী করা হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গের সময় ঢাকাকে ‘আসাম ও পূর্ববাংলার’ রাজধানী করা হয়। ১৯০৫ সালে ঢাকায় প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯০৯ সালে ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সালে ঢাকায় সলিমুল্লাহ এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯১১ সালের ১৮ আগষ্ট, ঢাকা ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর, বঙ্গ-ভঙ্গ রথ করা হয় এবং ঢাকা থেকে রাজধানী বাতিল করা হয়। ১৯১৩ সালে ঢাকা যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১৬ সালে ঢাকার সদরঘাটের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউট। ১৯২১ সালের সি. এস. রেকর্ড অনুযায়ী ২০০৬-এর রাজধানী শহরের যেসব খালের ৩৫টি উল্লেখ রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হলে এখন সেটা দস্তুরমতো গবেষণা করেই দেখতে হবে। ১৯২৫ সালে ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। লায়ন থিয়েটার হলে ১৯২৭ সালে নির্বাক সিনেমা প্রর্দশন করা হতো। ১৯৩০ সালে ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ী ছিল; রিক্সা ছিল না। গলির শেষ মাথায় লাগানো ছিল কেরোসিন বাতির ল্যা¤প পোষ্ট। ১৯৩৩ সাল থেকে সবাক চলচ্চিত্র প্রর্দশন শুরু হয়। ১৯৩৩ সালে প্রথম ঢাকায় সিনেমা হল তৈরী করা হয়। ১৯৩৫ সালে প্রথম মুড়াপাড়ার জমিদার ঢাকায় মটরগাড়ী আনে। ১৯৩৯ সালে কলকাতা থেকে ঢাকা শহরে প্রথম রিক্সা আনা হয়। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর “ঢাকা বেতার কেন্দ্র” প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই, ঢাকা ম্যাডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৬ সালে ঢাকায় ইডেন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা ছিল একটি জেলা শহরই মাত্র।
১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে ঢাকা শহরে ৩’শত টেলিফোন ছিল। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় লোকসংখ্যা ছিল ২ লাখ ৯৫ হাজার। ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে প্রথম হরতাল। হরতাল গুজরাতী শব্দ। ১৯৪৮ সালে প্রথম মুড়ির টিনমার্কা বাস চলাচল করে সদরঘাট থেকে চকবাজার হয়ে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রথম ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চে, ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব-পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের এক অধিবেশন বসে। ১৯৪৯ সালের জুলাই, ঢাকা বারলাইব্রেরীতে এক ঘরোয়া সভায় ইত্তেফাক নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা দেন এবং ওই সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে চারশত টাকার একটি তহবিল গঠন করেন। তা দিয়ে ১৫ আগষ্ট, ইত্তেফাকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম অফিস ছিল ৭৭, মালিটোলায় এবং পরে ৯৪, নবাবপুর রোডের আওয়ামী মুসলিম লীগ কার্যালয়ে। ১৯৫০ সালে ঢাকায় প্রথম সরকারীভাবে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আজিমপুরে ‘আজিমপুর সরকারী কোয়ার্টার’ নির্মাণ করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি, খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব-পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী থেকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ঢাকার এক জনসভায় বলেন-“উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’’। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি, পূর্ব-বাংলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রæয়ারি, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষারদাবীতে আন্দোলণরত জনতার উপর পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শহীদ হয়। এদের মধ্যে ৫(পাঁচ) জনের নাম জানা আছেঃ বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক ও অহিউল্লাহ। বরকত ছিলেন ছাত্র, সালাম ছিলেন সচিবালয়ের পিয়ন, জব্বার ছিলেন ছোট চাকুরে, রফিক ছিলেন প্রেসের কর্মচারী আর অহিউল্লাহ ছিলেন কিশোর বালক। পাঁচ জনের মধ্যে চার জনই ছিলেন সাধারণ মানুষ, দরিদ্র কর্মচারী বা ছোট ব্যবসায়ী। বাংলা ভাষার জন্য তাঁরা প্রাণ দিলেন, তাঁদের রক্তের ওপর দিয়ে দেশ স্বাধীন হল; কত লোকের ভাগ্য খুলে গেল, কিন্তু বাংলা ভাষার মধ্যে পরিবর্তন এলনা। বাংলা ভাষায় বড়লোক-ছোটলোকের তারতম্য রয়ে গেল। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রæয়ারি, ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে আয়োজিত শোক মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ। ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রæয়ারি, ভাষা আন্দোলনকারী জনতার উপর গুলীর প্রতিবাদে ‘‘দৈনিক আজাদ’ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের প্রাদেশিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ। ১৯৫২ সালের ২৯ মার্চ, ঢাকা বার এসোসিয়েশনে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের ২৮ জুন, ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় প্রথম নিউমার্কেট তৈরী করা হয়। ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর, বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৫৮ সালে ঢাকায় প্রথম চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৮ মার্চ, ঢাকা মুসলিম চেম্বার এবং ইউনাইটেড চেম্বার একত্রকরণের মাধ্যমে ‘‘ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির’’ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬১ সালের ৮ মার্চ, মতিঝিল বাস ডিপো হতে মাত্র ৪টি বাস নিয়ে তৎকালীন ইপিআরটিসি যাত্রা শুরু করে। ১৯৬২ সালে ঢাকা শহরে প্রথম ফুটপাত তৈরী হয়।
১৯৬৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় টেলিভিশন দেখা শুরু। ১৯৬৬ সালে প্রথম ঢাকায় ফাইভ স্টার “শেরাটন হোটেল” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ, পল্টন ময়দানের এক বিশাল জনসভায় বিভিন্ন নেতা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ, রমনা রেস কোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাসন দেন। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ, শেষবারের মতো ঢাকা সফরে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ, পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা বৈঠক শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ, পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা। ১৯৭১ সালের ২০ মার্চ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রায় সোয়া দু‘ঘন্টাব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ, ছিল এক বিভ্রান্তিপূর্ণ দিন। প্রেসিডেন্ট হাউজে ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার ছিল ২২ মার্চের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, পূর্ব-পাকিস্তানে গণহত্যর নির্দেশ দিয়ে আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। পাক-বাহিনী রাতে ঢাকায় শুরু করে ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকান্ড ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নিরস্ত্র জনগণের উপর অমানসিক নির্যাতন শুরু।
১৯৭১ সলের ১৭ এপ্রিল, কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরের বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননে প্রথম বিপ্লবী সরকারের মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর, শহীদ হন এ দেশের বুদ্ধিজীবীরা। তাই এদিনটিকে প্রতি বছর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪(চৌদ্ধ) লক্ষ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাক-বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি, পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন ১০ জানুয়ারি। তিনি ১২ জানুয়ারি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠান। ২০১৫ সালে ঢাকা শহরে লোকসংখ্যা হলো প্রায় ১.৮০(এক কোটি আশি লক্ষ)।
১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তৎকালীন বাংলায় অনেকগুলি মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠে এবং এ অঞ্চলে ফার্সী ভাষা চর্চার এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। দীর্ঘ সাড়ে ছয়শত বছর (১২০৩ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম শাসনামলে মুসলিম জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ১২০৩ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত ফার্সী ভাষা এতদঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল)। বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান হন দিনাজপুর অঞ্চলের বাসিন্দা জাতিতে মঙ্গোলিয়ান কোচ নামে পরিচিতি। বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কোচ নেতাকে ইসলাম ধর্মে রুপান্তরিত করে নাম রাখা হয় মোহাম্মদ আলী কোচ। সে-ই বঙ্গদেশের প্রথম মুসলমান বলে প্রমাণিত হয়। ১২০৬ সালের ৯ জুন, কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লীর স্বাধীন সুলতান পদে আসীন হন। ১২৩৫ সালের ১ মে, দিল্লীর সুলতান শামসউদ্দীন আলতামাসের ইন্তেকাল। ১২৬০ সালে দিল্লীর তৎকালীন প্রধান কাজী এবং প্রখ্যাত পন্ডিত মীনহাজ-ই-সিরাজ রচনা করেন তবকাত-ই-নাসিরী। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রথমদিকের প্রামান্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহের অন্যতম এ গ্রন্থটি ২৩ খন্ডে বিভক্ত। লেখক এই বিশাল গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে শুরু ইসলামের উন্মেষ এবং হিজরি ৭ম শতক পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাজবংশের বর্ণনা লিখে গেছেন। বাংলার ইতিহাস রয়েছে ২০, ২১ ও ২২ তবকাতে। তবকাত-এর অর্থ কাহিনী। প্রতœতত্ত¡ গবেষক ও ইতিহাসবিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তবকাত-ই-নাসিরী ফার্সী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। উল্লেখিত ৩টি তবকাত বা অধ্যায়। ১২৬০ সালে তবকাত-ই-নাসিরী ভারতবর্ষের প্রথম বই ফার্সী ভাষায় লেখা । এর পূর্বে ভারতবর্ষে আর কোন ভাষায় বই লেখা হয়নি। ১২৬৬ সালের ১৬ জুলাই, ভারতবর্ষের সাধক সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের ইন্তেকাল। ১১’শ শতকে শুরু হয় ভারতে মুসলিম ধর্ম প্রচারের সময় এবং ১২’শ শতকে কেরলাতে ভারতের প্রথম মসজিদ তৈরী হয়। ১২৯৬ সালের ২১ অক্টোবর, আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩০৩ সালের ২৬ আগষ্ট, আলাউদ্দিন খিলজী ‘চিতোর গড়’ দখল করেন। ১৩০৭ সালের ২৪ মার্চ, আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি দূর্গ দখল করেন। ১৩২৬ সালের ৫ জানুয়ারি, দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ইন্তেকাল। ১৩৩৮ সালে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের সূচনা করেন। ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল অব্যাহত ছিল। ২০০ বছর পর্যন্ত সুলতানি আমল অব্যাহত ছিল। ১৩৫১ সালের ২৩ মার্চ, ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৮৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের ইন্তেকাল। ১৩৮৯ সালের ১৯ ফেব্রæয়ারি, সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক (দ্বিতীয়) দিল্লীতে নিহত হন। ১৩৯৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর, পানিপথের যুদ্ধে তৈমুর লং দিল্লীর এক লক্ষ লোক হত্যা করেন এবং দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের কাছ থেকে দিল্লী দখল করে নেন। ১৩৯৯ সালের ১ জানুয়ারি, তৈমুর লং দিল্লী দখল করে নিজেকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করেন। ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধে, অর্থাৎ মুসলমান শাসনামলে। অনেকেই এটিকে পূর্ণাঙ্গ বাংলা অক্ষরে রচিত সর্বপুরাতন’ গ্রন্থ বলে দাবী করেন। বলা বাহুল্য, ‘চর্যাচর্য বিনিশ্চয়’ সার্বজনীনভাবে বাংলা ভাষার আদিতম পান্ডুলিপি বলে স্বীকৃত হয়। বাংলা ভাষার জন্ম মুসলিম শাসনামলে। ১৪০১ সালের ২৪ মার্চ, তৈমুর লং দামেস্ক অধিকার করেন। ১৫৫০ সালে বাঙলার ভূমি ও নদনদীর নক্শা প্রথম তৈরী করে জাও দ্য ব্যারোস-কৃত। ১৬৬০ সালে বাঙলার ভূমি ও নদনদীর নক্শা দ্বিতীয় বলে খ্যাত তৈরী করেন ফন্ ডেন ব্রোক-একজন ডাচ বনিক। ১৭৬৪-৮১ সালে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্র¯ত্তত মেজর রেনেলের বাঙলার মানচিত্র।
১৫১০ সালে পর্তুগীজরা গোয়ায় এসে পৌঁছায়। ১৫১১ সালে পৌঁছল মালয় উপদ্বীপের মালাক্কাতে। ১৫১৬ সালে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলাদেশে আগমণ করে। ১৫২৫ সালের ১৭ নভেম্বর, পঞ্চম দফা অভিযানের মধ্য দিয়ে মোঘল সম্রাট বাবরের ভারত বিজয়। ১৫২৬ সালের ২০ এপ্রিল, পানিপথের যুদ্ধে মোগলরা আফগানদের পরাজিত করে। ১৫২৬ সালের ২১ এপ্রিল, পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সম্রাট বাবর ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৬ সালের ২৭ এপ্রিল, বাবর দিল্লীর সম্রাট হন এবং মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৬ সালের ১০ মে, পানিপথের যুদ্ধে বিজীয় হয়ে মোগল সম্রাট বাবর আগ্রায় প্রবেশ করেন। ১৫২৭ সালের ১৬ মার্চ, মেবারের রানা সংগ্রাম সিং(প্রথম)-কে পরাজিত করে মোগল সম্রাট বাবর চিতোর জয় করে। ১৫২৮ সালের ২৯ জানুয়ারি, মোগল সম্রাট বাবর চান্দেরী দুর্গ দখল করেন। ১৫২৯ সালের ২৫ জুন, বঙ্গ বিজয়ের পর মোঘল সম্রাট বাবর আগ্রা প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিনি রাজধানী স্থাপন করেন আগ্রায়। ১৫৩৩-১৫৩৮ সাল পর্যন্ত মাহমুদ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। ১৫৩৮ সালে মুঘল সম্রাট হুমায়ূন প্রথম বাংলা জয় করেন। ১৫৩৮ সালে বাংলা অধিকার করেন শের খান। ১৫৩৮ সালে গৌড় দখল করার পর সম্রাট হুমায়ূন জাহিদ বেগ নামক তাঁর এক আমীরকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৫৩৯ সালের ২৬ জুন, বক্সারের কাছে চৌসারের যুদ্ধে শের শাহের কাছে মোগল সম্রাট হুমায়ূনের পরাজয়। ১৫৪০ সালের ১৭ মে, শেরশাহ কনৌজের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ূনকে পরাজিত করেন। ষোড়শ শতকে শেরশাহ তাঁর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এবং ঘোড়ার ডাকের প্রচলনের সুবাদে দিল্লী (পাঞ্জাবের অধীনে ছিল) থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত প্রায় ১,৭০০(এক হাজার সাতশত) মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাসখ্যাত এ পথের নাম গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। সোনারগাঁওয়ের আমিনপুর থেকে শুরু হয়ে মেঘনা পাড় হয়ে রাজপথ কামরুপ হয়ে দিল্লী পর্যন্ত বি¯তৃত ছিল। সোনারগাঁওয়ের আমিনপুর হয়ে মোগড়াপাড়ার সামনে দিয়ে উদ্ধবগঞ্জ বাজার থেকে বৈদ্যের বাজার পর্যন্ত কেবল এ রাস্তাটির অস্তিত্ব টিকে আছে। ক্রমাগত নদী ভাঙ্গন এবং ভূমির বিবর্তনের ফলে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া দুস্কর। কলকাতা থেকে দিল্লী (তখন পাঞ্জাব প্রদেশের অধীনে দিল্লী ছিল) পর্যন্ত এখনও গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড চালু আছে। ১৫৫৪ সালের ২২ মে, দিল্লীর সম্রাট শেরশাহ নিহত হন। ১৫৫৫ সালের ২২ জুন, মোগল সম্রাট হুমায়ূন সিরহিন্দ যুদ্ধে জয়লাভের পর আকবরকে তার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, কিশোর জালালুউদ্দিন আকবর ১৪ বছর বয়সে মোগল সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা হুমায়ূনের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৫৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল, সম্রাট আকবরের শাসনামল থেকে পহেলা বৈশাখকে বাংলা সালের প্রথম দিন ধরে আনুষ্ঠানিক বাংলা বর্ষ গণনা শুরু হয়। ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর, পানিপথের ২য় যুদ্ধে মোগল সম্রাট আকবরের বাহিনীর হাতে হিমু’র পরাজয়। ১৫৬১ সালের ৩১ জানুয়ারি, মোগল সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী বৈরাম খান নিহত হন। ১৫৬২ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ তৈরী হয় এবং ১৯৯২ সালের ৫ ডিসেম্বর (কংগ্রেস সরকারের আমলে) উগ্রবাদী হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। ১৫৬৫ সালের ৭ জুন, দাক্ষিণাত্যের রাজা হুসাইন নিজাম শাহের ইন্তেকাল। ১৫৬৮ সালের ২৮ ফেব্রæয়ারি, মোগল সম্রাট আকবরের কাছে চিতোরের রানা উদয় সিং-আত্মসমর্পণ করে। ১৫৭০ থেকে ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত মোঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল আগ্রা শহর থেকে ৪০ কি. মি. পশ্চিম দিকে অবস্থিত ফতেহপুর সিক্রি। সেই সময় সম্রাট আকবরের কোন ছেলে ছিল না। ১৫৭৬ সালের ১৮ জুন, মহারাজা প্রতাপ সিংহ ও মোগল সম্রাট আকবরের মধ্যে হলদিঘাটে যুদ্ধ শুরু। ১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই, দাউদ খান কররানীর পরাজয় ও মৃত্যু। ১৫৭৭ সালের ২৪ অক্টোবর, শিখ স¤প্রদায়ের উদ্যোগে ভারতের অমৃতসর নগরী’র পত্তন হয়। ১৫৮০ সালে পর্তুগীজ কর্তৃক হুগলী শহর প্রতিষ্ঠার ফলে নিকটবতী বিখ্যাত সাতগাঁও বন্দরের পতন। ১৫৮৫ সালের ১০ মার্চ, মোঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত বাংলা সন (বঙ্গাব্দ) চালুর ফরমান জারি করেন। ১৫৮৬ সালের ২৫ ফেব্রæয়ারি, সম্রাট আকবরের সভাকবি বীরবল নিহত হন। ১৫৮৬ সালে কাসিম খান কুচবিহার হ’তে হুগলি যাওয়ার পথে গৌড় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যান। ১৫৮৬ সালে ইংরেজ পর্যটক র্যালফ ফিচ বাংলা ভ্রমণ করেন। ১৫৮৮ সালের ১৯ এপ্রিল, জাহান্দর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫৮৯ সালের ৬ মে, সংগীত জগতের প্রবাদ পুরুষ মিঞা মুহাম্মদ তানসেনের মৃত্যু।
১৫৯৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, লন্ডনে ফাউন্ডার্স হলে ২৪(চব্বিশ) জন ব্যবসায়ী ভারতে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যদিয়ে ‘‘ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’’ গড়ে ওঠে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ১৬০১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, ক্যাপ্টেন ল্যাঙ্কেমটরের নেতৃত্বে ইস্ট-ইন্ডিয়া কো¤পানীর জাহাজ বহর ভারত পৌঁছে। শাহ সুজা ৩,০০০(তিন হাজার) টাকা শুল্ক দেওয়ার শর্তে ইংরেজদেরকে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাস্ত করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কো¤পানী ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ ১০১(একশত এক) বছর শাসন করে এবং ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর থেকে বৃটিশ রাজতন্ত্র ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত বৃটিশ রাজতন্ত্র ভারতবর্ষ শাসন করে ৮৯(উনানব্বই) বছর। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ রাজতন্ত্র ভারতবর্ষ শাসন করে মোট ১৯০(একশত নব্বই) বছর। মানুষই শ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট, ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে বাধ্য হলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বলে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আয়ুস্কাল ছিল ২৪ বছর ৪ মাস ৩ দিন) পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় নয় মাস মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়। ভারতবর্ষে তখনও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশ হয়নি।
১৬০৫ সালের ২৪ অক্টোবর, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, কুতুবুদ্দিন খান বাংলা ও বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬১২ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করার অনুমতি লাভ করে। ১৬১৩ সালের ১১ জানুয়ারি, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সুরাটে কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৬১৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রদূত টমাস রো মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভারতে পৌঁছেন এবং ১৬১৬ সালের ১০ জানুয়ারি, বৃটিশ রাজদূত টমাস রো মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে পৌঁছেন। ১৬১৮ সালের ১৭ ফেব্রæয়ারি, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত টমাস রো ভারত ত্যাগ করেন। ১৬২১ সালের ১৫ নভেম্বর, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর উত্তর ভারতের কাংড়া দুর্গ অধিকার করেন। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়ালদের ওপর কাঁচামাল খরিদ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তথাপি ইংরেজরা পরে কাসিমবাজারে একটি বড় কারখানা স্থাপন করে। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলে যার নাম বহুদিন যাবৎ প্রচারিত হয়েছে সেই জব চার্নকও এক সময় এ কাসিমবাজার কুঠিতেই একজন অধঃস্তন কর্মচারী ছিলেন। ১৬২৮ সালের ৪ ফেব্রæয়ারি, সম্রাট শাহজাহান আনুষ্ঠানিকভাবে আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীকে রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নেন সম্রাট শাহজাহান।
১৬৩৩ সালের মে, মহানদীর মুখে হরিহরপুরে ইংলিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে; তখন হ’তে রচিত হ’তে থাকে পলাশীর পটভূমি। ১৬৩৫ সালের ১১ ফেব্রæয়ারি, মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহ কান্দাহার বিরোধী তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। ১৬৩৭ সালে সম্রাট শাহজাহানের আমলেই তারই তত্ত¡াবধান এবং নির্দেশনায় নির্মাণ করা হয় ‘লাহোর শালিমার বাগ’। বাগানটি উন্মোচিত হয় ১৬৪২ সালে। ১৬৩৯ সালের ৮ জানুয়ারি, মোগল সেনা অধিনায়ক হিসেবে দারাশিকোহ পারস্যের বিরুদ্ধে কান্দাহারে প্রথম অভিযান চালান। ১৬৩৯ সালের ১৯ জানুয়ারি, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো’র লেখা ‘সাফিনাৎ-উল-আউলিয়া’ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৬৪০ সালের ১ মার্চ, বৃটিশরা মোগলদের কাছ থেকে মাদ্রাজে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৬৪৮ সালের ১৩ মে, মুঘল সম্রাট শাহজাহান দিল্লীতে লালকেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ১৬৫৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, মোগল সম্রাট শাহজাহান প্রিয়তমা স্ত্রীর নামে ‘‘তাজমহল’’ নির্মাণ করেন। ১৬৫৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, মোগল সম্রাট শাহজাহান আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে সিংহাসন নিয়ে সন্তানদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৬৫৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুজা বাহাদুরপুরে তাঁর ভাই দারার কাছে পরাজিত হন। ১৬৫৮ সালের ৮ জুন, আওরঙ্গজেব তাঁর পিতা সম্রাট শাহজাহানকে অন্তরীণ রেখে আগ্রার দুর্গ দখল করেন। ১৬৫৮ সালের ৩১ জুলাই, সম্রাট আওরঙ্গজেব আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ১৬৫৯ সালের ১৪ এপ্রিল, দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদ্বয় আওরঙ্গজেব ও তার ভাই দারাশিকোহ’র সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬৫৯ সালের ১৫ জুন, আওরঙ্গজেব আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৫৯ সালের ৩০ আগষ্ট, মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ দারাশিকোহ ঘাতকের হাতে নিহত হন। ১৬৬১ সালের ৩ এপ্রিল, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি যুদ্ধে অংশ নেয়া এবং অস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদির অধিকার সংক্রান্ত সনদ লাভ করে। ১৬৬৫ সালের ২৭ জানুয়ারি, শায়েস্তা খানের পুত্র উমেদ খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় ও ২(দুই) হাজার মগসেনা বন্দী। চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের চুড়ান্ত অন্তর্ভুক্তি। ১৬৬৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও মারাঠা নেতা শিবাজির মধ্যে পুরন্দর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৬৭০ সালের ৩ অক্টোবর, শিবাজি সুরাট অভিযান শুরু করেন। ১৬৭৬ সালের ১৫ অক্টোবর, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে টাকা মুদ্রনের অনুমতি লাভ করে। ১৬৮৬ সালের ২০ ডিসেম্বর, হুগলি ত্যাগ করে জব চার্নক সুতানুটিতে আশ্রয় নেন। ১৬৮৭ সালের ১৬ জুন, ইংরেজরা মোগল সাম্রাজ্যের সুতানুটিতে অস্ত্রাগার ও পোতাশ্রয় নির্মাণের অনুমতি পায়। ১৬৮৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব হায়দরাবাদের গোলকুন্ডা দখল করেন। ১৬৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম মাদ্রাজে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করেন।
১৬৮৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর, জবচার্ণক সুতানটি গ্রামে প্রথম এসেছিলেন। ১৬৯০ সালের ২৪ এপ্রিল, বৃটিশ নাগরিক জব চার্নক ভারতের সুতানুটিতে বৃটেনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে এ স্থানটি কলকাতা হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৬৯০ সালের ২৪ আগষ্ট, কলকাতা শহরের জন্ম। ১৬৯৩ সালের ১০ জানুয়ারি, কলকাতা নগরীর পত্তনকারী জব চার্নকের মৃত্যু। ১৬৯৮ সালের নভেম্বর মাসে ইংরেজরা বাংলার গভর্ণর আজিমউশ্বানের কাছ থেকে এ তিনটি গ্রাম কেনবার অনুমতি পেয়েছিলেন। ১৬৯৮ সালে ইংরেজরা কলকাতা সম্পূর্ণ দখল করে। ১৭০০ সালের ৮ জুন, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী সুতানুটির নাম পরিবর্তন করে ‘ক্যালকাটা’ রাখেন। ১৭০৭ সালে প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ১৭০৯ সালে সাবর্ণ চৌধুরী কালীঘাটের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ১৭১৭ সালে ডাক্তার হ্যামিলটনের সৌজন্যে, ফারুক সিয়ারের নিকট থেকে ৩৮টি গ্রামের জমিদারী কেনার অনুমতি পায়। ১৭১৮ সালের ১৭ এপ্রিল, ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় প্রথম মাদ্রাসা স্থাপন করেন।
১৭২০ সালে কলকাতার প্রথম জমিদার মি. ফ্রিক। ১৭২৭ সালে কলকাতা পৌরসভা শুরু, ১৭৮৭ সালে নাগরিকদের উপর টে´ বা কর বসায়। ১৭৩৪ বা ১৭৪৭ সালে প্রথম স্থাপিত হয় ফ্রি স্কুল ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত। ১৭৩৬ সালে কলকাতায় প্রথম অল্ডারম্যান ডা. সেফালিয়া হলওয়েল। ১৭৩৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, প্রচন্ড বেগে ঝড় উঠেছিল ও গঙ্গার জল ৪০ ফিট পর্যন্ত উঠেছিল। ১৭৪২ সালে প্রথম পাকা রাস্তার কাজ আরম্ভ আর শেষ ১৭৮০ সালে (সার্কুলার রোড)। ১৭৪৫ সালে প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত হয় লালদীঘির পার্শে¦। ১৭৫২ সালে কলকাতায় চালের মণ ১(এক) টাকা ছিল। ১৭৫৬ সালের ১৭ জুন, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ইংরেজদের দখল থেকে কলকাতা পুনরুদ্ধারে অভিযান চালান। ১৭৫৬ সালের ২০ জুন, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৫৬ সালে কলকাতা নবাব সিরাজদৌল্লাহ দখল করে নাম দেন ‘আলিনগর’। ১৭৫৬ সালের ১০ অক্টোবর, রবার্ট ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে ৫টি যুদ্ধজাহাজে ৯০০ সৈন্য নিয়ে কোলকাতা দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি, রবার্ট ক্লাইভ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কাছ থেকে কলকাতা দখল করে। ১৭৫৭ সালের ৯ জানুয়ারি, রবার্ট ক্লাইভের হুগলী দখল। ১৭৫৭ সালের ৮ ফেব্রæয়ারি, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার দ্বিতীয় দফা কলকাতা আক্রমণ এবং ইংরেজদের সাথে আলীনগরের সন্ধি। ১৭৫৭ সালের ২৩ এপ্রিল, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের সিলেক্ট কমিটিতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে নবাব করার নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের ২৮ এপ্রিল, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের সিলেক্ট কমিটি প্রস্তাব নিল যে, ক্লাইভ যেন নবাবের প্রতি দরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোভাব কী রকম এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে মসনদে বসাবার পরিকল্পনায় তাদের প্রতিক্রিয়া কী তা জানার জন্য উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করেন। ১৭৫৭ সালে কলকাতায় প্রথম টাকশাল স্থাপিত হয়। ১৭৫৭ সালে চৌরঙ্গির জঙ্গল পরিস্কার করে প্রথম গড়ের মাঠ তৈরী হয়। ১৭৫৭ সালে ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণ কাজ শুরু এবং শেষ ১৭৭৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। ১৭৬২ সালের মহামারীতে মারা যায় ৫০,০০০ বাঙ্গালী এবং ৮শত ইউরোপীয়। ১৭৬২ সালে প্রথম মুদ্রা তৈরী হয়। ১৭৬৫ সালের ৩ মে, বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে লর্ড রবার্ট ক্লাইভ কলকাতায় আসেন। ১৭৭৪ সালের ২৬ মার্চ, সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়।
১৭৭৪ সালের ১ আগষ্ট, কলকাতাকে ভারতবর্ষের রাজধানী ঘোষণা করে। ১৭৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি, রবার্ট নাইটের সম্পাদনায় ‘দি ইন্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান’ পত্রিকার প্রকাশনা। ১৭৭৫ সালের ৫ আগষ্ট, কুলিবাজারে প্রথম ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হন মহারাজ নন্দ কুমার। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি, ১ম বাংলা গেজেট ও মাসিক প্রত্রিকা “দিকদর্শন” প্রকাশনা হয়। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি, জেমস আগাস্টাস হিকির সম্পাদনায় ভারতের প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘বেঙ্গল গেজেটের’ সম্পাদনা শুরু হয়। ১৭৮০ সালের ১৪ নভেম্বর, বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করে। ১৭৮০ সালে রাইটার্স বিল্ডিং তৈরী করা হয়। ১৭৮১ সালের ১৭ এপ্রিল, গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় প্রথম আলীয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটী নামে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৭৮৫ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা থেকে কত টাকা খাজনা পায় বছরে-১,২২,৪১৮ টাকা। ১৭৮৫ সালে প্রথম দাস ব্যবসা শুরু হয়। ১৭৮৫ সালে হিকে সাহেবের আত্মজীবনীতে প্রথম টানা পাখার উল্লেখ পাওয়া যায়; তবে ফরাসী পর্যটক গ্রএে ১৭৮৯ সালে কলকাতায় এসে টানা পাখার হাওয়া খেয়েছেন। ১৭৮৮ সালের ৬ এপ্রিল, শনিবার অমাবস্যার রাতে নরবলি দেওয়া হয়েছিল। ১৭৮৯ সালে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় কলকাতা শহরে (ভারতবর্ষে প্রথম)। ১৭৯০ সালের ৩ ডিসেম্বর, লর্ড কর্নওয়ালিস কলকাতায় নিজামত আদালত স্থানান্তরিত করেন। ১৭৯১ সালের ৩ অক্টোবর, ভারত উপমহাদেশের প্রথম মাসিক পত্রিকা ‘ক্যালকাটা ম্যাগাজিন এন্ড ওরিয়েন্টাল মিউজিয়ামের প্রকাশনা শুরু। ১৭৯৩ সালে প্রথম ওকালতি শুরু হয়। ১৭৯৩ সালে প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। ১৭৯৩ সালের ১১ নভেম্বর, শিক্ষাব্রতী ধর্মযাজক উইলিয়াম কেরি ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছান। ১৭৯৪ সালের ৯ মার্চ, কলকাতায় প্রথম দলিল রেজিস্ট্রি শুরু হয়। ১৭৯৪ সালে প্রথম ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর, প্রথম বাংলা নাটক “কাল্পনিক সংবদন” অভিনীত হয়।
১৭৯৫ সালে ভারতবর্ষের প্রথম ব্যাংকের নাম ক্যালকাটা ব্যাংক। ১৮০০ সালের ৩ মে, কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৫ সালে শহীদ মিনার নির্মাণ হয় এবং উচ্চতা ১৫২ ফুট, ২২৩টি সি‘ড়ি। ১৮১৬ সালে কলকাতা শহরে ২৫০ জন ইউরোপিয় মহিলা ছিলেন। ১৮১৬ অথবা ১৮১৭ সালে কলকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপনে রাজা রামমোহনের অবদান। ১৮১৮ সালের ১৫ মে, বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র ‘বেঙ্গল গেজেটের’ প্রকাশনা শুরু। ১৮১৯ সালে কলকাতা রেসকোর্স মাঠ তৈরী হয়। ১৮২৪ সালের ৩১ মার্চ, প্রথমবারের মত ভারতীয় টাকশালের কার্যক্রম শুরু। ১৮২৭ সালের ১২ মে, কলকাতার ময়দানে সমবেত হয়ে সরকারের জারি করা নির্দেশের বিরুদ্ধে পাল্কি বেহারারা সর্বাত্বক আন্দোলন গড়ে তোলার যে সংকল্প ঘোষণা। ১৮২৯ সালে লর্ড রেন্টিং কর্তৃক সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। ১৮২৯ সালে প্রথম কালিঘাটের টালী নালার উপর লোহার সেতু নির্মান করা হয়। ১৮৩০ সালে ডালহাউসীতে প্রথম ’’¯েপনসেস হোটেল” নির্মাণ হয়। ১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজের জনপ্রিয় শিক্ষক ডিরোজিওর বাড়িতে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এ দেশের প্রথম ছাত্র সংগঠন ‘একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’। বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। এরপর ১৮৩৮ সালের ১২ মার্চ, গঠিত হয় আরেকটি ছাত্র সংগঠন। যার নাম ছিল ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’। এ সংগঠনের সদস্যরা নিয়মিতভাবে আলোচনায় বসতেন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করতেন। এ সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার পর ১৮৪১ সালে কলকাতায় গঠিত হয় আধা রাজনৈতিক সংগঠন ‘দেশহিতৈষণী সভা’। এ সংগঠনের সদস্যরাও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং সমস্যা-সমাধানের উপায়ও সন্ধান করতেন। কিন্তু ১৮৪৩ সালের ২৫ এপ্রিল, জন্ম নেওয়া ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি’ সর্বপ্রথম বাঙালির সংগঠন, যারা সরাসরি রাজনৈতিক দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছিল। তাদের প্রধান দাবি ছিল ভারতীয়দের জন্য ব্রিটিশের সমমর্যাদা দান। এ দাবির পক্ষে সংগঠনের সদস্যরা জনমত গঠন করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাজনৈতিক দল হলো একটি সংঘবদ্ধ সংস্থা, যা দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলিকে তার কর্মসূচীতে সন্নিবিষ্ট করে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে বদ্ধপরিকর হয়। ১৮৩৪ সালে ক্যালকাটা চেম্বারস অব কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারপর ২০-বছর পর-এর নামকরণ করা হয় ১৮৫৪ সালের ১৫ জুলাই, বেঙ্গল চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাজট্রিজ। এ প্রতিষ্ঠান সারা ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৮৩৫ সালে প্রথম ম্যাডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৬ সালের ২১ মার্চ, কলকাতায় প্রথম গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৮ সালে কলকাতায় দিয়াশলাই তৈরী হয়। ১৮৪৪ সালে প্রথম ডাক্তারী শিক্ষার জন্য গোপালচন্দ্র শীল, ভোলানাথ বসু, সুর্য কুমার চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ বসু এঁরা বিলেতে যান। ১৮৫০ সালে কলকাতা থেকে কানপুর ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক যেত। ১৮৫৪ সালে প্রথম ডাকটিকিট বিক্রি শুরু হয়।
১৮৫৫ সালের ৩০ জুন, প্রথম সাওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। এ বিদ্রোহ ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজের বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন হয়। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই, কলকাতায় বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর, হিন্দু সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধবা বিয়ের প্রচলন শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতায় পথের আলো জ্বলেছিল ঠিকই, তা ছিল গ্যাসের আলো। ১৮৬২ সালের মে মাসে, কলকাতা শহরে হাওড়ার রেলের ১২(বারো) শ্রমিক আট ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেন। ১৮৬২ সালে কলকাতায় প্রথম ‘‘ফুটপাত’’ ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীটে তৈরী হয়। ১৮৬২ সালে কলকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ সালের ২৭ আগষ্ট, ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন “শ্রমজীবী সংঘ’’ গঠিত হয়। ১৮৭৩ সালে প্রথম কলকাতায় রঙ্গ-মঞ্চে মেয়েরা এসেছেন। ১৮৭৪ সালে কলকাতা নিউমার্কেট। ১৮৭৬ সালে প্রথম চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয় ৪৮-একর জমিতে। ১৮৭৭ সালের ১২ মে, কলকাতায় কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ সালের ১ এপ্রিল, কলকাতা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯ সালের ৪ মার্চ, ব্রিটেনের বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে প্রথম মহিলা কলেজ কলকাতার বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮০ সালের ১ নভেম্বর, কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম সার্ভিস চালু হয়। ১৮৮১ সালে প্রথম টেলিফোন চালু হয়। ১৮৮১ সালের ১৪ ফেব্রæয়ারি, অবিভক্ত ভারতে কলকাতায় প্রথম হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৮২ সালের ১৩ ফেব্রæয়ারি, প্রথমবারের মতো কলকাতায় পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ সালে রসগোল্লার উৎপত্তি এ নিয়ে বিতর্ক চলছে-কলকাতা না ওডিশা।
১৮৯৯ সালের ৩০ মে, কলকাতার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ শুরু। ১৮৯৯ সালে ভারতবর্ষের কলকাতা শহরে প্রথম ট্রাফিক পুলিশের কার্যক্রম চালু হয়। ১৯০২ সালে এইচ. এম. ভি. কোম্পানি কলকাতা শহরে প্রথম গানের রেকর্ড করা শুরু করে শিল্পী গহরজানকে দিয়ে। ১৯০৫ সালে কলকাতা শহরে প্রথম টেক্সি চলে। ১৯০৫ সালের ৫ মার্চ, কলকাতা শহরে প্রথম আঞ্জুমান মফিজুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩/১৪ সালে চায়নাবাসী প্রথম রি´া চালায়, ১৮৭০ সালে জাপান প্রথম রি´া তৈরী করে। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতা শহরে ইংরেজরা রাস্তার মোরে মোরে ফ্রি চা পান করায়। ১৯২০ সালে দমদম বিমান বন্দর তৈরী হয়। ১৯২২ সালে কলকাতা শহরে প্রথম বিমান উড়ে। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সর্বপ্রথম কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। ১৯২৭ সালের ২৬ আগষ্ট, কলকাতায় প্রথম বেতার কেন্দ্র ‘ইন্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস’ চালু হয়। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতায় প্রথম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। এ দাঙ্গা এক বছর চলে এবং হিন্দু-শিখ সন্ত্রাসীদের হাতে ৫০ হাজার মুসলমান মারা যায়। হিন্দু সাংবাদিকদের হিসাবে ৫ হাজার লোক নিহত হয়েছিল ও ১৫ হাজার আহত হয়। স্টেটসম্যান পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী, ২০ হাজার লোক হতাহত হয়। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ঃ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম)। ১৯৫৮ সালের ৩ মার্চ, প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগষ্ট, কলকাতায় খাদ্যের দাবীতে কৃষকদের মিছিলে পুলিশের গুলীতে ৮০-ব্যক্তি নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট, কলকাতায় দুরদর্শন কেন্দ্র চালু হয়। ১৯৮৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, কলকাতায় পাতাল রেল চালূ। ১৯৮৮ সালের হিসাব অনুসারে, খোদ কলকাতা শহরে রয়েছে ২,২২০টি নোটিফায়েড বস্তি যাতে ১৭,০০,০০০ লাখ লোকের বাস। পুর এলাকার ১৪১টি ওয়ার্ডের মাত্র ২টি ছাড়া সব ওয়ার্ডেই বস্তি আছে। ২০০২ সালে কলকাতা শহরে প্রায় ৪,০০০ হাজার রাস্তা বেয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে ১ কোটিরও বেশী মানুষ। ২০১৫ সালে কলকাতা শহরে ১.৯৫ কোটি লোক বাস করে।
১৬৯১ সালের ১০ ফেব্রæয়ারি, মোঘল সাম্রাজ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের অনুমতি দিয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান জারি। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর, ইস্ট-ইন্ডিয়া কো¤পানী কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এ তিনটি গ্রামের জমিদারি সনদ লাভ করেন। ১৭১২ সালের ১৯ এপ্রিল, জাহান্দার শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৭১৩ সালের ১৩ ফেব্রæয়ারি, মোগল সম্রাট জাহান্দার শাহ নিহত হন। ১৭১৭ সালে ইংরেজরা মুঘল সম্রাট ফারুখ শিয়ারের কাছ থেকে শুল্কবিহীন বাণিজ্যের ছাড়পত্র দত্ত¡ক পেয়েছিল। ১৭৫৭ সালের ৪ জানুয়ারি, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তাঁদের বিশেষ অধিকার ফিরিয়ে দেন। ১৭৫৭ সালের ১৩ জুন, রবার্ট ক্লাইভ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যুদ্ধ অভিযান শুরু করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, প্রথম পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবাব সিরাজ দৌল্লাহ ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ হ’তে যাত্রা শুরু করেন এবং মীরজাফর, খাদিম হোসেন ও রায়দুর্লভ তাঁরা সৈন্যদের নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে নিস্ক্রীয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন, মীর জাফর আলী খাঁ বাংলার নবাব হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ। ১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই, মীরজাফর তনয় মীরনের নির্দেশে নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে হত্যা করা হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত (পলাশীর যুদ্ধের পর) মীর জাফর নামেমাত্র নবাব ছিলেন। ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর, রবার্ট ক্লাইভ বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতো-মক্তব, মাদ্রাসা, টোল ও রাজদরবারকে কেন্দ্র করে। মধ্যযুগে মুসলমানদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ‘‘মক্তব’’। আরবি, ফারসি ও ইসলাম ধর্মের উচ্চতর শিক্ষা হতো ‘‘মাদ্রাসায়’’। ‘‘মুঘল’’ আমলে বাংলা গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করেন ‘‘টোডরমল’’।
১৭৫৮ সালের ১২ ডিসেম্বর, ফরাসি জেনারেল ল্যালি ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ দুর্গ দখল করেন। ১৭৫৮ সাল থেকেই ফকির বিদ্রোহের নেতা মজনু শাহ প্রথমদিকে বাস করতেন ভারতের কানপুর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মকানপুর নামক শাহ মাদারের দরগায়। ১৭৫৮ সাল থেকে শুরু হয়ে আঠার শতকের পর উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ফকির অভিযান অব্যাহত ছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘটিত সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছিল-ফকির আন্দোলন। ১৭৫৯ সালের ৩০ নভেম্বর, মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর নিজ মন্ত্রীর হাতে নিহত হন। ১৭৬০ সালের ১১ জুন, মহীশুরের নবাব হায়দার আলীর সাথে বৃটিশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হয়। ১৭৬০ সালে বর্ধমাণ জেলায় সন্ন্যাসীরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে ১ম সংগ্রাম শুরু করে। ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা ইস্ট-ইন্ডিয়া কো¤পানীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে অভিহিত। ১৭৬১ সালের ৬ জানুয়ারি, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। পেশোয়া বালাজি বাজিরাও, গোয়ালিওর রাজসিন্ধিয়াসহ পাঠান সর্দারদের সম্মিলিত বাহিনী আহমদ শাহ আবদালীর নিকট পরাজয়বরণ করে। একদিনের যুদ্ধে ২-লক্ষাধিক মারাঠা সৈন্য নিহত। ১৭৬১ সালের ১৪ জানুয়ারি, মারাঠা বাহিনী ও আহমদ শাহ দুররাণীর মধ্যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৬১ সাল হ’তে নুতন কো¤পানী সরকার বার বার রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকে। ১৭৬১ সালে ফকিররা ইংরেজদের ঢাকা কুঠির আক্রমণ ও লুটপাট করেন। ১৭৬৩ সালের ২৪ জুন, বৃটিশ সৈন্যদের মুর্শিদাবাদ দখল এবং মীর জাফর আলী খাঁকে বাংলার নবাবী প্রদান। ১৭৬৩ সালের ২ আগষ্ট, মুর্শিদাবাদ দখলের পর বৃটিশ সৈন্য গিরিয়াতে মীর কাশিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে মীর কাশিম পরাজিত হয়। ১৭৬৩ সালের ৬ নভেম্বর, নবাব মীর কাশিমের কাছ থেকে ব্রিটিশের পাটনা দখল।
১৭৬৩ সালে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে এদেশে যে ফকির আন্দোলন বা সন্ন্যাস আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের নেতা ছিল ফকির মজনু শাহ। ফকির মজনু শাহ ছাড়া আর কে ছিল-ভবানী পাঠক। ১৭৬৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, বৃটিশ বাহিনী রাজমহলের কাছাকাছি উদয়নালায় মীর কাশিমকে পরাজিত করে। ১৭৬৩ সালে বরিশালে ফকিররা প্রথম ইংরেজদের ওপর হামলা করে। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর, মীর কাসিম এবং ইংরেজদের মধ্যে ‘বক্সার’ নামক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা ও বিহারে নবাবী আমলের অবসান। ১৭৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর, বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর কাছে মীর কাসিমের পরাজয়। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট, মোগল সম্রাট বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কো¤পানীর হাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী তুলে দেন। ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কোম্পানির এলাহাবাদ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৭৬৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ফকির-সন্ন্যাসীকে দমন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৭৬৫ সালে রবার্ট ক্লাইভ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ লাভ করে দক্ষিণ এশিয়ার বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৭৬৫ সালে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা প্রথম ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে আসে। ১৭৬৭ সালের জানুয়ারি, ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যার্তন করলে তার ব্যবস্থায় ফাটল ধরে। ১৭৬৭ সাল থেকে ১৭৬৯ সালের মধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে ফকিরদের সংঘর্ষে সেনাপতি মার্টল ও লেফটেন্যান্ট কিথ নিহত হন। ১৭৬৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, কর্ণেল স্পিথ হায়দরাবাদের নিজামের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৬৮ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস গর্ভনর জেনারেল হয়ে ভারতে আসেন। ১৭৬৯ সালের ১৭ মার্চ, তাঁত ও মসলিন শিল্প ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে বাংলার তাঁতিদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দেয়া শুরু হয়। ১৭৬৯-৭০ সালে ভারতবর্ষের বাঙলা আর বিহার জুড়ে দুর্ভিক্ষের কথা বলছি। এ দুর্ভিক্ষে এদের মোট প্রজার এক-তৃতীয়াংশ মারা গেল। (বাংলা ১১৭৬ সালে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাকে বলা হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)। ১৭৭০ সালের ২৫ জুন, মুর্শিদাবাদ হ’তে কো¤পানীর আবাসিক প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের রিপোর্টঃ “এ এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ইহার বর্ণনা অসম্ভব। দেশের কয়েক অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতি সত্য’’। ১৭৭০-৭১ সালে ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে রেশম উৎপাদন হ্রাস পায় শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। ১৭৭১ সালে দুর্ভিক্ষের পর (সেখানে দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যাওয়ার পরও) তাদের রাজস্ব আদায় হল ১৫ কোটি ৭২ লাখ টাকা। ১৭৭১ সালের ২৫ ডিসেম্বর, দ্বিতীয় শাহ আলম মোঘল সম্রাট হিসেবে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। ১৭৭২ সালের ১৫ আগষ্ট, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী জেলা পর্যায়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানি আদালত পৃথক করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান করা হয় এবং ১৭৭২ সালেই কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি শাসন সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেন। ১৭৭২ সালে সর্বপ্রথম ফরাসী বণিক জঁলিয়ে লুই বোনার্দ হুগলী জেলার তালডাঙ্গায় নীলের বাগান করেন। তা দেখে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী অনুপ্রাণিত হয় এবং ১৭৮৮ সালে বাংলায় নীল চাষ শুরু করে।
১৭৮১ সালের ২ জুলাই, মহিশূরের বীর হায়দার আলী বৃটিশ বাহিনীর হাতে পরাজিত হন। ১৭৮১ সালের ১২ নভেম্বর, ব্রিটিশ বাহিনী দক্ষিণ ভারতের নাগাপট্টম দখল করে। ১৭৮২ সালের ৭ ডিসেম্বর, মহীশুরের বীর যোদ্ধা হায়দর আলীর মৃত্যুর পর টিপু সুলতান মহিসুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে “রংপুর বিদ্রোহ’’ জোতদার ও রায়তেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৭৮৪ সালের ১১ মার্চ, মহিশুরের টিপু সুলতানের সাথে ইংরেজদের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর। ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত ফকির মজনু শাহ’্র বাহিনী কো¤পানী সৈন্যের সঙ্গে বহুবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৭৮৭ সালে ফকির মজনু শাহ্’র মৃত্যু হয়। ১৭৮৭ সালে মজনু শাহের মৃত্যুর পরে ফকির বাহিনী ততটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। ১৭৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর, ইস্ট-ইন্ডিয়া কো¤পানীর আমলে ভারতে প্রাচীন সৈন্যবাহিনীর রেজিমেন্টের জন্ম। ১৭৯১ সালের ২১ মার্চ, বৃটিশ সৈন্যরা টিপু সুলতানের কাছ থেকে বাঙ্গালোর দখল করে নেয়। ১৭৯১ সালের ডিসেম্বর, বৃটিশ শেষ ইজারাদারদের অত্যাচার হ’তে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বলাকী শাহ্ তাঁর ৫(পাঁচ) হাজার সশস্ত্র শিষ্য নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৭৯১-৯২ সালকে বলা হয় বলাকী শাহ্’র বিদ্রোহ। ১৭৯২ সালের ৫ ফেব্রæয়ারি, টিপু সুলতান কর্তৃক বৃটিশ শাসিত হায়দরাবাদের নিজামের নিকট মহীশূরের অর্ধেক হস্তান্তর। ১৭৯৯ সালের ৪ মে, ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে মহিশূরের টিপু সুলতান নিহত হন। ১৭৯৯ সালের ১৪ জুলাই, মাহাজেরা ৫(পাঁচ) হাজার সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে পলায়নের পথে মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৫৬ সালের ৭ ফেব্রæয়ারি, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৫৬ সালের ৪ জুলাই, মৌলভী আহমদ উল্লাহ ও লাখনৌর বেগম হযরত মহলের সাথে যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয়। ১৮৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি, ব্যারাকপুরের সিপাহিরা প্রথম বিদ্রোহ করে। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, ভারতের ব্যারাকপুর সেনা ব্যারাকে মঙ্গলপান্ডের গুলী ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বভারতীয় প্রথম সংগ্রাম কোনটি ‘‘সিপাহী বিদ্রোহ’’। ভারতীয় সৈনিকদ্বারা ইউরোপীয় অফিসারদের ব্যারাকপুরে আক্রমণ করা হয়। ১৮৫৭ সালের ৩ এপ্রিল, রাণী ভিক্টোরিয়াকে ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল, সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রণী সৈনিক মঙ্গল পান্ডের ফাঁসি হয়। ১৮৫৭ সালের ১০ মে, ভারতের উত্তর প্রদেশের মিরাটে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৮৫৭ সালের ১১ মে, দিল্লীতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ শুরু। ১৮৫৭ সালের ১৭ মে, সিপাহী বিপ্লবের নেত্রী ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই-এর মৃত্যু। ১৮৫৭ সালের ৩০ মে, বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে লক্ষেèৗতে, সমগ্র আওয়াধ অঞ্চলে। ১৮৫৭ সালের ৫ জুন, নানা সাহেব ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্র-ধারণ করল এবং দেড় মাস যেতে না যেতেই ১৮ জুলাই, ইংরেজদের কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। ১৮৫৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, সিপাহী বিপ্লবের বীর যোদ্ধা নানা সাহেব নেপালে নির্বাসনকালে মারা যান।
এ অঞ্চলে কলকাতা শহরে ১৭৩৪ বা ১৭৪৭ সালে প্রথম স্থাপিত হয় ফ্রি স্কুল ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত। তারপর কলকাতা শহরে ১৭৮৭ সালে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৮৯ সালে এ স্কুল থেকে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়া হয়। বাংলাদেশে প্রথম ১৭৮০ সালে ঢাকায় আলীয়া-ই-মাদ্রাসা এবং তারপর বিক্রমপুরে ১৮০৫ সালে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮২৮ সালে রাজশাহী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের প্রথম কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৮০০ সালের ৩ মে, ‘‘ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ’’। বাংলাদেশের প্রথম কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ সালের ২০ নভেম্বর, ‘‘ঢাকা কলেজ’’। ১৮৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি, ইস্ট-ইন্ডিয়া রেলওয়ে উদ্বোধন। ১৮৫৩ সালের পর হ’তে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা দ্রæত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল, বোম্বাইয়ে প্রথম ট্রেন চলাচলের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে রেল যোগাযোগের সূচনা হয় এবং ১৮৫৪ সালে ভারতের বোম্বে হতে কলকাতা শহরে প্রথম রেল চলাচল করে। দর্শনা হতে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হয় ১৮৬২ সালে। ১৮৬৭ সালে কুষ্টিয়া হতে গোয়ালন্দ রেলপথ নির্মাণ করা হয়। ১৮৮৫ সালের ৪ জানুয়ারি, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রেলপথ নির্মাণ করা হয়। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রেলপথটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭ জুলাই, ১৯৯৭ সালে ছেড়ে দেয়।
ভারতবর্ষে একই বছর তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি, কলকাতা, মুম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু। ভারতবর্ষের প্রথম দু’জন গ্র্যাজুয়েটের নাম হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। ১৮৫৮ সালে সিন্ডিকেটের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ও সঙ্গী গ্র্যাজুয়েট যদুনাথ বসু। উভয়েই পরীক্ষায় ফেল করেছিল এবং দু‘জনকেই ‘‘এজ এ স্পেশাল এক্ট অব গ্রেস” দিয়ে পাশ করানো হয়েছিল। তাঁরাই ভারতবর্ষের প্রথম গ্রাজুয়েট। ১৮৬২ সালের ২১ জুন, অবিভক্ত ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ১৮৭৭ সালে ১২(বার) জন ভারতীয় এম. এ. পাশ করেন। ১৮৮২ সালে ভারতবর্ষে মেয়েরা প্রথম স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং এদেরই একজন চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৪ সালে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম মাষ্টার ডিগ্রী লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ১৯৮ জন বাঙালি মুসলমান স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। উনিশ শতকে সীমিত পরিসরে সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়াস চালানো হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম নারীসমাজের শিক্ষাবিস্তার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে ক’জন মহিলা উদ্যোগ নেন তাঁদের মধ্যে বিবি তাহেরা নেসা, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩), করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬) এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) তাহেরা নেসা প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা লেখক। তিনি ১৮৬৫ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় ‘শিক্ষা ও সামাজিকতায় নারীর অধিকার’ সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ সালে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৫-১৬ সাল পর্যন্ত কোনো মুসলমান মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেননি; ১৯১৮-১৯ সালে মাত্র একজন মেয়ে এ পরীক্ষায় পাস করেন। তবে ১৯২১-২২ সালে ১০২ জন মুসলিম ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)।
১৮৮৫ সালে মুম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস পার্টির জন্ম। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর, বোম্বে শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন ডবিøউ. সি. ই. (ইংরেজ)। বাঙ্গালী ব্যারিস্ট্রার উমেশ চন্দ্র ব্যাণার্জি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি। বাঙ্গালী ব্যারিস্ট্রার উমেশ চন্দ্র ব্যাণার্জির বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন-‘‘অ্যালান অক্টোভিয়ান ইিউম’’। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, ঢাকার নবাব স্যার সলিমূল্লাহ’র প্রাসাদে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে ‘‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে এম. এন. রায় ও কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে রাশিয়ার তাসখন্দে বসে ‘‘ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি’’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ সালের ২৬ আগষ্ট, লাহোরে ৭৫ জন লোক নিয়ে ‘জামায়াতে ইসলামী’ নামে একটি আদর্শবাদী দল গঠন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা শহরে ‘‘নেজামে ইসলামী পার্টি’’ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে বি. জে. পি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন, ঢাকার ‘‘রোজ গার্ডেনে’’ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ’’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে ‘‘আওয়ামী লীগ’’ নাম করণ করা হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ন্যাপ) গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রæয়ারি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রচলিত সকল রাজনৈতিক দল বাতিল ও বেআইনী ঘোষণা করে ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি (বিএনপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি, ‘বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি’ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এছাড়াও আরো অনেক পার্টি ও গ্রæপ আছে।
৬৩৮ খৃষ্টপূর্ব গ্রিক কবি সোলোনের জন্ম, মৃত্যু-খৃষ্টপূর্ব ৫৫৯। ৬২০ খ্রিষ্টপূর্ব রোমান নাট্যকার ঈসপের জন্ম, মৃত্যু-খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬০। ৫৮০ খৃষ্টপূর্ব দার্শনিক পিথাগোরাসের জন্ম, খৃষ্টপূর্ব ৫০০ মৃত্যুবরন করেন। ৫৫১ খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ আগষ্ট, চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের জন্ম এবং খৃষ্টপূর্ব ৪৭৯ মৃত্যুবরন। ৪৮৪ খৃষ্টপূর্ব গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিডিসের জন্ম, মৃত্যু-খৃষ্টপূর্ব ৪০৬। ৪৬৯ খৃষ্টপূর্ব গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের জন্ম, মৃত্যু-খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯। ৪৬০ খৃষ্টপূর্ব হিপোক্রেটসের জন্ম এবং মৃত্যু-৩৭০ খৃষ্টপূর্ব। ৪২৭ খৃষ্টপূর্ব প্লেটো জন্মগ্রহন করেন এবং ৩৪৭ খৃষ্টপূর্ব মৃত্যুবরন করেন। ৩৮৪ খ্রিষ্টপূর্ব গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল জন্মগ্রহন এবং মৃত্যুবরন করেন ৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব। ৩৫৬ আলেকজান্ডার দি গ্রেট খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৬ জন্ম, মৃত্যু-১৩ জুন, ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব। ৩০০ খৃষ্টপূর্ব অশোকের জন্ম, খৃষ্টপূর্ব ২৩২ মৃত্যু। ২৮৭ খ্রিস্টপূর্ব আর্কিমিডিসের জন্ম এবং মৃত্যু খ্রিষ্টপূর্ব ২১২। ১০৬ খৃষ্টপূর্ব গ্রিক দার্শনিক, কবি ও নাট্যকার সিসেরোর জন্ম, মৃত্যু-খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩। খ্রিষ্টপূর্ব ৫ রোমান দার্শনিক সেনেকার জন্ম, মৃত্যু-৬৫ সালে। ৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর, রোম সম্রাট নিরোর জন্ম, মৃত্যু-৬৮ খ্রিষ্টাব্দ। রোমান সম্রাট নিরো ৬৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক খেলায় অ্যাথলেট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং সব ইভেন্টে তিনি জয়ী হয়েছেন অন্য সবাইকে ঠকিয়ে। ১০০ সালে রোমের রাষ্ট্রপ্রধান ও সমরনায়ক জুলিয়াস সিজারের জন্ম, মৃত্যু-১৫-০৩-১৪৪ তারিখ।
৫৭০ সালের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার প্রত্যুষে আরবের মক্কা নগরীতে সভ্রান্ত কুরাইশ বংশে মাতা আমেনার গর্ভে হযরত মুহাম্মদ(স.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ রবিউল আউয়াল, ১১শ হিজরী মোতাবেক ৭ জুন, ৬৩২ সালে প্রায় ৬৩-বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। বিশ্ব নবীর গোটা জীবনকাল প্রায় ২২,৩৩০(বাইশ হাজার তিনশত ত্রিশ) দিন ৬(ছয়) ঘন্টা সময়। মহানবী(স.) মক্কা নগরীতে অবস্থান করেণ ১২ বছর ৫ মাস ২১ দিন। মহানবী(স.) মদীনায় অবস্থান করেণ ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন। বিশ্বনবী(সা.) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বদরের এবং ওহুদের যুদ্ধ। মহানবী(দ.)-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী নাজিল হয় ৬১০ সালের ৬ আগষ্ট মোতাবেক ২৭ রমজান। বিশ্বনবী(সা.) ১২ রবিউল আউয়াল ১১শ হিজরী মোতাবেক ৭ জুন ৬৩২ সালের রোজ সোমবার দিন ইন্তেকাল করেন। ৯৪১ সালে মহাকবি ফেরদৌসী জন্মগ্রহন করেন এবং ১০২০ সালে মৃত্যুবরন করেন। ৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলবেরুনীর জন্ম এবং ১২ ডিসেম্বর, ১০৪৮ সালে মৃত্যুবরন করেন। ৯৮২ সালে বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর মুন্সীগঞ্জের সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১০৫৪ সালের ১৮ নভেম্বর, দেহত্যাগ করেন চীনদেশে। ১৯৭৮ সালের ২৩ জুন, অতীশ দীপংকরের দেহভস্ম চীন থেকে ঢাকায় আনা হয়। ১০৯৬ সালে আনুমানিক রাজা বিজয় সেন জন্মগ্রহন করেন এবং মৃত্যুবরণ-১১৫৯ সালে। ১০৯৯ বা ১১০০ সালে ভূগোলবিদ ও মানচিত্রকার আল ইদ্রিসী স্পেনের সিউটাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১১৬৬ সালে বা কারো কারো মতে তার মৃত্যু-১১৮০ সালে। ১১১৪ সালে দক্ষিণ ভারতে ভাস্করাচার্যের জন্ম, মৃত্যু-১১৮৫ সালে। ১১৪২ সালে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)’র জন্ম, মৃত্যু-১২৩৬ সালে। ১১৬২ সালে ইতিহাসে বিতর্কিত পুরুষ বহু দেশ বিজেতা ও মঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁনের জন্ম এবং মৃত্যু-১৮-০৮-১২২৭ তারিখ। ‘চীনা ভূখন্ডেই চেঙ্গিস খানের সমাধি রয়েছে’। চীনে চেঙ্গিস খানকে শ্রদ্ধা করা হয় এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তাকে মহান ‘চীনা’ রাজবংশের অগ্রদুত হিসেবে মনে করে থাকে। ১২০৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী(রহ.)’র জন্ম, মৃত্যু-১৬-১২-১২৭৩ তারিখ। ১২০৮ সালে মিশরে ইবনুন নাফিসের পুরো নাম আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবুল হাজমের (একজন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী) জন্ম, কায়রোতে শুক্রবার দিন সকালে ইন্তেকাল করেন-১৮-১২-১২৮৮ তারিখ। ১২৫৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, ইতালীর ভেনিস শহরে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলোর জন্ম, মৃত্যু-০৮-০১-১৩২৪ তারিখ। ১২৭১ খ্রিষ্টাব্দে, ইয়েমেনীতে হযরত শাহ জালালের (রহ.) জন্ম, মৃত্যু-১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু মৃত্যু দেখানো হয়েছে ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। প্রতি বছর ২২ ডিসেম্বর থেকে ওরসের কাজ শুরু হয়। ১৩০৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর, হযরত শাহ জালাল(রা.) ছিলেন (ইয়েমেনী) সিলেট আগমনের সাতশ’ বছর পূর্তি হয় ১৮-১২-২০০৩ তারিখ হযরত শাহ জালাল(রা.) সুরমা নদীর যে ঘাট দিয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ করেছিলেন সেই ঐতিহ্যবাহী স্থান শেখঘাট মসজিদ থেকে দরগাহ পর্যন্ত শোভাযাত্রা হয়েছিল। শাহ জালাল (রহ.) মাত্র ৩২ বছর বয়সে ৩৬০(তিনশত ষাট) জন সঙ্গী নিয়ে সিলেটে আগমন করেন।
১৩০৪ সালে ইবনে বতুতা তানজিয়ারে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তার আসল নাম ছিল ‘‘মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ’’ তিনি মরক্কোতে ফিরে যান এবং সেখানকার কোন এক শহরের তিনি কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৩৬৮ সালে তিনি মারা যান। তিনি কমপক্ষে ৭৫-হাজার মাইল পরিভ্রমণ করেছেন। সর্বপ্রথম ইবনে বতুতার নাম জনসমক্ষে প্রচার হয় ১৮২৯ সালে, ডা. স্যামুয়েল কর্তৃক একখানা ক্ষুদ্র অনুবাদ গ্রন্থের দ্বারা। (ইবনে বতুতা বাংলা সফর করেন সুলতানি আমলে)। ১৪০০ সালে জার্মানের এক ভদ্র পরিবারে মুদ্রণ শিল্পের পথিকৃৎ ইওহান জোহান্স গুটেনবার্গের জন্ম, মৃত্যু-২৩-০২-১৪৬৮ তারিখ (মুদ্রণ যন্ত্রের আবিস্কারক হিসাবে পরিচিতি)। ১৪১২ সালে ফ্রান্সের জন্মদাত্রী-স্বাধীনতাকামী বালিকা জোয়ান অব আর্কের জন্ম, মৃত্যু-১৪৩১ সালের ৩০ মে, ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী বালিকা জোয়ান অব আর্ককে ডায়নীর অপরাধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ১৪১৫ সালে কবি কৃত্তিবাসের জন্ম এবং মৃত্যুবরণ-১৪৩৩ সালে। ১৪৫১ সালের আগষ্ট মাসে ক্রিস্টোফার কলম্বাস জন্মগ্রহন করেন এবং ২০-০৫-১৫০৬ তারিখ, এক সাধারণ কুটিরে মৃত্যুবরন করেন। ১৪৬৯ সালে ইতালীয় লেখক ও রাষ্ট্রনায়ক নিকোল ম্যাকিয়াভেলির জন্ম, মৃত্যু-২২-০৬-১৫২৭ তারিখ।
১৪৬৯ সালে ভারতের পাঞ্জাবে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জন্ম, মৃত্যু-১০-১০-১৫৩৯ তারিখ। ১৪৭২ সালের ১৯ ফেব্রæয়ারি, পোলান্ডের টোরন শহরে জার্মান বংশোদ্ভূত এক ধনী পরিবারে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের প্রবক্তা পোলিশ বিজ্ঞানী ও আধুনিক জোতির্বিজ্ঞানের জনক নিকোলাস কোপারনিকাসের জন্ম, পোলান্ডের ফ্রয়েনবার্গ শহরে মৃত্যু-২৪-০৫-১৫৪৩ তারিখ। ১৪৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোগল সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের জন্ম, মৃত্যু-২৬-১২-১৫৩০ তারিখ। ১৪৮৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের সংস্কারক জার্মান ধর্মতাত্তি¡ক মার্টিন লুথার কিংকের জন্ম, মৃত্যু-১৮-০২-১৫৪৬ তারিখ। ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রæয়ারি, গৌরীয় বৈঞ্চব ধর্মের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম, মৃত্যু-২৯-০৬-১৫৩৩ তারিখ। ১৫০৮ সালের ৭ মার্চ, মোগল সম্রাট হুমায়ূনের জন্ম, ইন্তেকাল-২৮-০১-১৫৫৬ তারিখ। ১৫৩৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, বৃটেনের রাণী প্রথম এলিজাবেথের জন্ম, মৃত্যু-১৬০৩ সালে। ১৫৪২ সালের ২৩ নভেম্বর, মোঘল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের জন্ম, আগ্রায় ইন্তেকাল-১৭-১০-১৬০৫ তারিখ। ১৫৫১ সালের ১৪ জানুয়ারি, মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সম্রাট আকবরের মন্ত্রী পন্ডিত শেখ আবুল ফজলের জন্ম, মৃত্যু-২২-০৮-১৬০২ তারিখ। ১৫৬১ সালে ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহন করেন, মৃত্যু-১৬২৯ সালে। ১৫৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল, ইংল্যান্ডে ইয়র্কশায়ারের এক দরিদ্র পরিবারে কবি ও সাহিত্যিক উইলিয়ম শেক্সপিয়রের জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৪-১৬১৬ তারিখ।
১৫৬৪ সালে ইতালিতে পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ গ্যালিলিও গ্যালিলাই জন্মগ্রহন করেন এবং মৃত্যু-০৮-০১-১৬৪২ তারিখ। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তা প্রমাণ করতে ১৬১১ সালের ১৪ এপ্রিল রোম শহরের একটি পাহাড়ে নিজের বানানো টেলিস্কোপ প্রদর্শন করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। এ কারণে ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের হাতে তিনি নিগৃহীত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার ৪০০ বছর পর গত ১৪-০৪-২০১১ তারিখ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে ভ্যাটিকান। গ্যালিলিও যে জায়গায় টেলিস্কোপ প্রদর্শন করেছিলেন, সেখানে গড়ে উঠেছে আমেরিকান একাডেমি নামে কলা ও মানবিকবিষয়ক গবেষণাগার। গ্যালিলিওর সম্মানে সেখানে শিল্পকলার প্রদর্শনী হয়। ১৪-০৪-২০১১ তারিখ সেখানে ভ্যাটিকানে রক্ষিত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন সরঞ্জামেরও প্রদর্শনী হয়। ১৫৬৪ সালে পাঞ্জাবের সরহিন্দে শেখ আহমেদ সরহিন্দি জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৬২৪ সালে। ইসলামের প্রথম যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব খলিফা উমরের বংশধর বলে নিজেকে দাবি করেন। ১৫৬৯ সালের ৩০ আগষ্ট, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম, মৃত্যু-২৮-১০-১৬২৭ তারিখ। ১৫৭৩ সালে ইংরেজ কবি জন ডানের জন্ম, মৃত্যু-৩১-০৩-১৬৩১ তারিখ। ১৫৭৭ সালের ৮ জানুয়ারি, বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও মনীষী রবার্ট বার্টনের জন্ম, মৃত্যু-২৫-০১-১৬৪০ তারিখ। ১৫৭৮ সালের ১ এপ্রিল, রক্তসঞ্চালন পদ্ধতির অন্যতম উদ্ভাবক ডা. উইলিয়াম হার্ভের জন্ম, মৃত্যু-১৬৫৭ সালে। ১৫৮১ সালে আইরিশ ধর্মযাজক জেম্স আশার জন্ম, মৃত্যু-১৬৫৬ সালে। (তিনি লিখেছিলেন ‘অ্যানালস অফ ওল্ড অ্যান্ড নিউ টেষ্টামেন্ট’ (পুরনো ও নতুন টেষ্টামেন্টের বছরওয়ারী বিবরণী)। ১৫৯২ সালের ৫ জানুয়ারি, মোগল সম্রাট শাহজাহানের জন্ম, মৃত্যু-২২-০১-১৬৬৬ তারিখ। ১৫৯৯ সালের ২৫ জানুয়ারি, বৃটেনের বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতা অলিভার ক্রমওয়েলের জন্ম এবং মৃত্যু-০৩-০৯-১৬৫৮ তারিখ।
১৬০১ সালে ইরানি বংশোদ্ভূত শায়েস্তা খার (আসল নাম মির্জা আবু তালিব) জন্ম। তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ভাই। বাংলার নবাব মির জুমলার মৃত্যুর পর ১৬৬৪ সালে ৬৩ বছর বয়সে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক মনোনীত হয়ে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৬৬৪ সালের ১৯ মার্চ, শায়েস্তা খাঁ বঙ্গের সুবাদার হিসেবে ঢাকায় আসেন। বাংলায় চলছিল কৃত্রিম খাদ্য সংকট। সায়েস্তা খাঁ বিভিন্ন রাজ্য পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি নিজের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ইতিহাসে স্থান করে নেন কিংবদন্তি পুরুষ হিসেবে। তৎকালীন মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন মির্জা তালিবকে ‘‘শায়েস্তা খান’’ উপাধিতে ভূষিত করেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮(আট) মণ চাল পাওয়া যেত। জনগণের মনে এখনো ‘‘শায়েস্তা খাঁর আমল’’ কথাটির ব্যবহার হয় জিনিসপত্র সুলভে প্রাপ্তির প্রবাদবাক্য হিসেবে। কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ীর কারণে বাজারে যখন ‘তোঘলিক কারবার’ (তোঘলকের শাসনকাল ছিল ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)। ১৬০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর, লন্ডনে বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন মিলটনের জন্ম, মৃত্যু-০৮-১১-১৬৭৪ তারিখ। ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্ম, (তিনি ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুলাই, ভারতের সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে বসেন এবং ৯৪ বছর বয়সে ও প্রায় ৫০ বছর ধরে রাজত্ব করার পর) ১৭০৭ সালের ৩ মার্চ, দাক্ষিণাত্যের শিবিরে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ইন্তেকাল করেন। ১৬২৩ সালে ফরাসি দার্শনিক, গণিতবিদ এবং পদার্থবিদ বেøইজি প্যাসকেলের জন্ম, মৃত্যু-১৬৬২ সালে। ১৬২৭ সালের ১০ এপ্রিল, মারাঠা অধিনায়ক শিবাজির জন্ম, মৃত্যু-১৪-০৪-১৬৮০ তারিখ। ১৬৪২ সালের ২৫ ডিসেম্বর, (বড়দিনে) মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের জন্ম, মৃত্যু-২০-০৩-১৭২৭ তারিখ। ১৬৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর, বিখ্যাত ইংরেজ লেখক আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে জোনাথন সুইফটের (গালিভার’স ট্রাভেলস লিখে অমর হয়ে আছেন যিনি) জন্ম, ডাবলিনে মৃত্যু-১৯-১০-১৭৪৫ তারিখ। তাঁর সেরা লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৭২৬ সালে ‘গালিভার’স ট্রাভেলস’। ১৬৭১ সালের ১১ আগষ্ট, হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মীর কামালউদ্দিন খাঁর জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৬৭৬ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দী খানের জন্ম, মৃত্যুঃ ১০-০৪-১৭৫৬ তারিখ। ১৬৮৬ সালের ২৪ মে, থার্মোমিটারের উদ্ভাবক পোলিশ-জার্মান পদার্থবিদ ডানিয়েল গাব্রিয়েল ফারেনহাইটের জন্ম, মৃত্যু-১৬-০৯-১৭৩৬ তারিখ। ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খানের জন্ম, মৃত্যু-০৫-০২-১৭৬৫ তারিখ। জাফর আলী খান ১৭২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নবাব আলীবর্দী খানের বৈমাত্রের ভগিনী শাহ খানমের সাথে বিবাহ হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মায়ের সৎ ফুফুকে বিয়ে করেন মির জাফর আলী খান। এক কথায় সিরাজ-উদ-দৌলার নানার সৎ বোনের স্বামী-মির জাফর।
১৭০৩ সালে যুক্তরাজ্য প্যাট্রিক মুরের জন্ম (প্যাট্রিক মুরের জন্ম-১৭০৩ সালে, ৩ বছর বয়সে প্যাট্রিকমুরে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে যোগ দেন)। ১৭০৬ সালে আমেরিকাতে মার্কিন সাংবাদিক, বিজ্ঞানী ও কবি-সাহিত্যিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম, মৃত্যু-১৭-০৪-১৭৯০ তারিখ। ১৭১৩ সালের ৫ অক্টোবর, ফরাসী দার্শনিক ঔপনাসিক, প্রাবন্ধিক ও এনসাইক্লোপেডিস্ট ডেনিস দিদেরো জন্মগ্রহণ করেন এবং প্যারিসে মৃত্যু-৩০-০৭-১৭৮৪ তারিখ। ১৭১৭ সালে বাংলার নবাব মীর কাশিমের জন্ম, ইন্তেকাল ০৬-০৬-১৭৭৭ তারিখ। ১৭২৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, পলাশী যুদ্ধের বিজেতা এবং বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের স্থপতি আয়ারল্যান্ডের একটি মাঝারি জমিদার পরিবারে রবার্ট লর্ড ক্লাইভের জন্ম, মৃত্যু-২২-১১-১৭৭৪ তারিখ তিনি গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ১৭২৮ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাহর জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৭-১৭৫৭ তারিখ। তাঁর পূর্ণ নাম ও পদবি হয়-নবাব মনসুর-উল-মুলক মির্যা মোহাম্মদ শাহ কুলি খান সিরাজ-উদ-দৌলা হয়বত জঙ বাহাদুর নামে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল মহা জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁর মাতামহের মসনদে আরোহণ করেন। (তাঁর মাতামহ নবাব আলিবর্দী খান ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দী খাঁর ইন্তেকাল। মারা যাওয়ার ৭(সাত) দিন পর ক্ষমতা গ্রহণ করে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাহ’র সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত হন ২৩-০৬-১৭৫৭ তারিখ।) ১৭২৮ সালের ২৭ অক্টোবর, ইংরেজ পর্যটক ক্যাপটেন জেমস কুক জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৪-০২-১৭৭৯ তারিখ। ১৭৩০ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলার কচুয়া গ্রামে (বাংলা ১১৩৭ সনের ১৮ ভাদ্র) লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার বারদী গ্রামে মৃত্যু-০২-০৬-১৮৯০ তারিখ (বাংলা ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সন)। মারা যান ১৬০ বছর বয়সে। সিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবনের শেষ দিনগুলো এ গ্রামেই অতিবাহিত করেন। আজকের বারদী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের কারণেই বিখ্যাত। জ্যোতিবসুর পৈতৃক ভিটা এ গ্রামেই অবস্থিত। ঢাকা থেকে বারদী খুব একটা দূরের পথ নয়। প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব হবে। ১৭৩২ সালের ৩ জানুয়ারি, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী ও দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসীনের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-১১-১৮১২ তারিখ। ১৯০৬ সালে হাজী মহসীন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠিত হয় কলকাতায়। ১৭৩২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, মার্কিন যুক্তরাষ্টের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের জন্ম, মৃত্যু-১৪-১২-১৭৯৯ তারিখ।
১৭৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিস্কারক স্কটিশ বিজ্ঞানী জেম্স ওয়াটের জন্ম, ২৫-০৮-১৮১৯ তারিখ, ৮৩-বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরন করেন। ১৭৩৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর, লন্ডনের মেফেয়ারে একটি অভিজাত পরিবারে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশের জন্ম, ০৫-১০-১৮০৫ তারিখ, ভারতের গাজীপুরে মারা যান। ১৭৫৭ থেকে ১৭৯২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা ও ঔপনিবেশিক শাসক। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকালে একজন ডাকসাইটে ব্রিটিশ জেনারেল হিসেবে তার পরিচিতি ছিল সর্বত্র। ১৭৪৯ সালের ২৮ আগষ্ট, জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুট শহরে জার্মান মহাকবি যোহান উলফগ্যাঙ ভন গ্যাটের জন্ম, মৃত্যু-২২-০৩-১৮৩২ তারিখ। তাঁর জার্মান সাহিত্যিকের সাহিত্য জীবন শুরু হয় ১৭৬৭ সালে। ১৭৫০ সালের ২০ নভেম্বর, ভারতের মহিশূরে টিপু সুলতানের জন্ম, ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে মহিশূরের টিপু সুলতান নিহত হন ০৪-০৫-১৭৯৯ তারিখ। ১৭৫১ সালের ২৫ মে, বাংলায় মুদ্রিত প্রথম ব্যাকরণ গন্থের রচয়িতা হ্যালহেডের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৭৫৩ সালে ইংল্যান্ডে অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর জন্ম, মৃত্যু-১১-০৯-১৮২৩ তারিখ। ১৭৫৪ সালে বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যান্টের জন্ম, মৃত্যু-১২-০২-১৮২৪ তারিখ। ১৭৫৫ সালের ১০ এপ্রিল, জার্মানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যার জনক ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্ম, মৃত্যু-০২-০৭-১৮৪৩ তারিখ। ১৭৫৫ সালের ১১ এপ্রিল, পার্কিনসন রোগের উদ্ভাবক জেমস পার্কিনসনের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৭৬১ সালে বৃটিশ মিশনারী ও বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের লেখক উইলিয়াম কেরীর জন্ম, মৃত্যু-০৯-০৬-১৮৩৪ তারিখ। ১৭৬৫ সালে দার্শনিক জোহানগট লিব ফিকটের জন্ম, মৃত্যু-১৮৫৪ সালে। ১৭৬৯ সালের ১৫ আগষ্ট, কর্সিকাতে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ম, মৃত্যু-০৫-০৫-১৮২১ তারিখ। ১৭৭০ সালে ফরিদপুর জেলার তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের বীর সেনানী হাজী শরীয়াত উল্লাহ(রহ.) এবং মৃত্যু-২২-০১-১৮৩৯ তারিখ। হাজী শরীয়াত উল্লাহ(রহ.) ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রপথিক। হাজী শরীয়াত উল্লাহ(রহ.) ১৭৯২ সালে জ্ঞান অর্জনের জন্য কলকাতা চলে যান। ১৭৯৯ সালে মৌলভী বাসারত আলী-হাজী শরীয়াত উল্লাহ(রহ.)কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা শরীফ গমন করেন। ১৭৭০ সালের ২৭ আগষ্ট, দার্শনিক জর্জ ভিলহেলম ফ্রেডারিক হেগেলের জন্ম, মৃত্যু-১৪-১১-১৮৩১ তারিখ। ১৭৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর, বনের বাড়িতে জার্মানীর বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ফন বিটোফেনের জন্ম, মৃত্যু-২৬-০৩-১৮২৭ তারিখ ভিয়েনায়। ১৭৭৪ সালের ৭ মে, ফ্রান্স থেকে আসা আয়াল্যান্ডে এক প্রটেস্ট্যান্ট পরিবারে বুফোর্টের জন্ম, মৃত্যু-১৭-১২-১৮৫৭ তারিখ। এভাবেই সম্মান জানানো হয়েছে সমুদ্র অভিযান, সমুদ্র পথ, সমুদ্র উপকুল অনুসন্ধানী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বুফোর্টকে। ১৭৭৪ সালের ১০ মে, বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বাংলার তথা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ বলা হয়। ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায় লন্ডনে ফিরে আসেন এবং ২৭-০৯-১৮৩৩ তারিখ বৃষ্টল শহরে মৃত্যুবরণ করেন। ১৭৭৪ সালের ১৭ অক্টোবর, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড থানার হরিশপুর গ্রামে (কুষ্টিয়া জেলায়) বাউল সম্রাট ও মরমী কবি ফকির লালন শাহের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৭-১০-১৮৯০ তারিখ।
১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের শেষ মুগল সম্রাট আবু জাফর সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ জাফর (দ্বিতীয়)-এর জন্ম, ১৮৫৮ সালের ৯ মার্চ, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর শেষ মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে শেকলে বন্ধী করে বার্মায় নির্যাতনে পাঠানো হয়। বাহাদুর শাহ জাফর দীর্ঘ ৪-বছর এক গ্যারেজে অন্তরীণ থাকার পর ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর, পরিচয়হীনভাবে অবমাননাকর অবস্থায় রেঙ্গুনের উপকন্ঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এ মৃত্যতেও ব্রিটিশ সিংহের ভয় কাটেনি বলেই মনে হয়। কারণ তার কবরের কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখা হয়নি। এর আগে তাঁর পুত্রদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। রেঙ্গুনে বাহাদুর শাহ জাফরের মাজার অলংকরণে ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করলো মিয়ানমার ঃ তার এই কবরের সঠিক অবস্থান বহুকাল অজ্ঞাত থাকার পর মাত্র ১৯৯১ সনে একটি স্মারক ভবন নির্মাণের জন্য খোঁড়াখোঁড়ির সময় কবরটির অবস্থান আবিস্কৃত হয়। কবরের নিচের মাটিতে রয়েছে এ কবর। ওপরেরটি নকল। দৃশ্যতঃ মনে হয় ভারতের শেষ সম্রাটকে নিয়ে ভারতে যাতে জাতীয়তাবাদী আবেগের জোয়ার না সৃষ্টি হয় সেজন্যই এ কৌশল। এ ধরণের মর্মান্তিক পরিণতির কথা অনুমান করেই খুব সম্ভবত তিনি তাঁর এ অমর কাব্যচরণ লিখতে প্রেরণা পেয়েছিলেন “দো গজ জমিন ভি না মিলি”। অর্থাৎ যে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের অধীশ্বর ছিলেন তিনি সেই তারও শেষ শয়নের জন্য হিন্দুস্তানের মাটিতে মাত্র দু‘গজ যায়গাও মিললো না। ১৭৭৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের জন্ম, রুশ জার আলেকজান্ডার (প্রথম)-এর মৃত্যু-০১-১২-১৮২৫ তারিখ।
১৭৮১ সালের ৯ জুন, রেলওয়ে ইঞ্জিনের নকশাকার ও স্টিম ইঞ্জিনের রূপকার ইংরেজ উদ্ভাবক জর্জ স্টিফেনসনের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৮-১৮৪৮ তারিখ। ১৭৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী মীর নিসার আলীর (শহীদ তিতুমীর) জন্ম, মৃত্যুঃ ১৪-১২-১৮৩১ তারিখ। ১৭৮২ সালের ২১ এপ্রিল, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির উদ্গাতা ফ্রিডরিখ ফ্রোয়েবেলের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৭৯১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, ইংরেজ রসায়ন ও পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৮৬৭ সালে। (১৮৪৫ সালে বিদ্যুৎ আবিস্কারক)। ১৭৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর, যুক্তরাজ্যের লন্ডনে চার্লস ব্যাবেজের জন্ম, মৃত্যু-১৮-১০-১৮৭১ তারিখ। তিনি ১৮২২ সালে ডিফারেন্স মেশিন নামের বিশ্বের প্রথম কমপিউটার তৈরি করেন। ১৭৯৪ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর সুবিদিত ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবসা বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-০১-০৮-১৮৪৬ তারিখ। ১৭৯৫ সালের ৩১ অক্টোবর, ইংরেজ কবি জন কিটসের জন্ম; মৃত্যু-২৩-০২-১৮২১ তারিখ। ১৭৯৭ সালে অযোধ্যার অন্তর্গত খয়রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মৃত্যু-১৮৬১ সালে আন্দামান দ্বীপে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবে মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসনে পাঠায়। ১৭৯৭ সালে ভারতের দিল্লী শহরে উর্দু ও ফার্সি সাহিত্যের মহাকবি কবি মির্জা আসাদ উল্লাহ খান গালিবের জন্ম, ইন্তেকাল-১৫-০২-১৮৬৯ তারিখ। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়েছে। এ বিদ্রোহের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ১৮০৪ সালের ২৮ জুলাই, জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক ল্যুৎদভিগ ফয়েরবাখের জন্ম, মৃত্যু-১৩-০৯-১৮৭২ তারিখ। ১৮০৯ সালের ৪ জানুয়ারি, অন্ধদের পাঠ পদ্ধতির উদ্ভাবক ফরাসী গবেষক লুই ব্রায়ির জন্ম, মৃত্যু-২৮-০৩-১৮৫২ তারিখ। ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রæয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের ষোলতম প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী নেতা আব্রাহাম লিংকনের জন্ম, মৃত্যু-১৫-০৪-১৮৬৫ তারিখ। ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ইংল্যান্ডের শ্রæসবরিতে বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস রবার্ট ডারউইনের জন্ম, মৃত্যু-১৮-০৪-১৮৮২ তারিখ। তাঁর লেখা ‘অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ’ বহুল আলোচিত গ্রন্থটি ১৮৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৮১৫ সালের ১৭ অক্টোবর, আলিগড়ের প্রখ্যাত মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার অগ্রদূত, নেতা, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদের জন্ম, মৃত্যু-১৮৯৮ সালে। ১৮১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর, যুক্তরাজ্য, লন্ডন, অগাষ্টা আডা বায়রনের (আডা লাভলেস) জন্ম, মৃত্যু-২৭-১১-১৮৫২ তারিখ। পৃথিবীর প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার। চার্লস ব্যাবেজ উদ্ভাবিত কমপিউটারের জন্য প্রথম প্রোগ্রাম লেখেন। ১৮১৭ সালের ১৫ মে, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বাংলা গদ্যের লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যুঃ ০৫-০১-১৯০৫ তারিখ। ১৮১৮ সালের ৫ মে, জার্মানে সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের জন্ম; ইংল্যান্ডে মৃত্যু-১৪-০৩-১৮৮৩ তারিখ। ১৮৪৮ সালের ১৮ ফেব্রæয়ারি, কার্ল-মার্কস কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো ঘোষণা করেন। ১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রæয়ারি, কার্ল-মার্কস ও ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৮১৮ সালে ঢাকার নবাব স্যার নওয়াব খাজা আবদুল গনির জন্ম, মৃত্যু-১৮৭৩ সালে। খাজা আবদুল গনি বংশানুক্রমিক নবাব উপাধি লাভ করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১৮৬৫ সালে। ১৮২০ সালের ১২ মে, ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে ইংরেজ সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জন্ম, ১৩-০৮-১৯১০ তারিখ, এ মানব দরদী মহীয়সী নারীর মৃত্যু। ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম; মৃত্যুঃ ২৯-০৭-১৮৯১ তারিখ। ১৮৪০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র ‘‘বিদ্যাসাগর’’ উপাধি পান। ১৮৮০ সালে বিদ্যাসাগর সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর, জার্মানে এঙ্গেলসের জন্ম, ইংল্যান্ডে মৃত্যু-১৮৯৫ সালে। ১৮২০ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মহারাষ্ট্রে সিপাহী বিপ্লবের আপসহীন নেত্রী ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাই’র জন্ম, মৃত্যু-১৭-০৬-১৮৫৮ তারিখ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাণ। ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর, ফরাসী রসায়নবিদ ও অনুজীব বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৯-১৮৯৫ তারিখ। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি, যশোরের সাগর দাঁড়ির দত্ত পরিবারের একমাত্র পুত্র মহাকবি ও সাহিত্যক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-০৬-১৮৭৩ তারিখ কলকাতার আলীপুর হাসপাতালে।
১৮২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, রাজনৈতিক দাদাভাই নওরোজির জন্ম, মৃত্যু-১৯১৭ সালের ৩০ জুন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম এশীয় সদস্য দাদাভাই নওরোজীর মৃত্যু। ১৮২৬ সালের ২৪ জানুয়ারি, অবিভক্ত ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার গণেন্দ্রমোহন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-০৫-০১-১৮৯০ তারিখ। ১৮২৭ সালের ৫ এপ্রিল, পচনরোধী ওষুধের আবিষ্কারক ইংরেজ চিকিৎসক যোসেফ লিস্টারের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৮২৮ সালের ৮ মে, রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনান্ট সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৯১০ সালের ৩০ অক্টোবর। ১৮২৮ সালের ২৮ আগষ্ট, মানবতাবাদী লেখক ও রাশিয়ার বিপ্লবী সাহিত্যিক লেভ টলষ্টয়ের জন্ম; মৃত্যু-২০-১১-১৯১০ তারিখ। ১৮২৮ সালের ৩১ অক্টোবর, বৃটিশ রসায়নবিদ ও বিদ্যুৎ বাতির উদ্ভাবক জোসেফ সোয়ানের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৮২৮ সালে নবাব আব্দুল লতিফ ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ১৮৪৮ সালে কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী ও আরবী বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন, ১৮৬২ সালে নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে প্রথমবঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৮৪ সালে নবাব আব্দুল লতিফ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন, মৃত্যুঃ ১০-০৭-১৮৯৩ তারিখ। ১৮৩২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার চিতওয়া গ্রামে ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর জন্ম, ঢাকায় মৃত্যু-০৯-০২-১৮৮৫ তারিখ।
১৮৩৩ সালের ২০ জুলাই, কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কুন্ডুপাড়ার এক দরিদ্র পরিবারে গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৎ উনিশ শতকের সংবাদপত্র গ্রামবার্তা প্রকাশিকার সম্পাদক কাঙাল হরিণাথ মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০৪-১৮৯৬ তারিখ। ১৮৬৩ সালে কুমারখালী বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক কাঙাল হরিণাথ মজুমদার মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রকাশ করেন। ১৮৩৩ সালের ২১ অক্টোবর, সুইডেনের রাজধানী স্কটহোমে জন্মগ্রহণ করেন আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল, মৃত্যু-১০-১২-১৮৯৬ তারিখ। তিনি সুইডেনের একজন খ্যাতিমান শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, যিনি বিশ্বের সেরা এই পুরস্কারের প্রবর্তক, যা তাঁর নিজ নামে সন্নিহিত তথা নোবেল প্রাইজ রুপে বিশ্ববিশ্রুত। ১৮৬৭ সালে পেটেন্টকৃত আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেলের বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবিস্কার ‘ডিনামাইট’ জগৎ জুড়ে শিল্প উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর অবদান রেখে আসছে। ১৯০১ সালে প্রথমবার নোবেল প্রাইজ প্রদানের পর থেকে অদ্যাবধি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় তা নোবেল কমিটি কর্তৃক প্রকাশের পূর্বে কেউই নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে এ পুরস্কার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। ১৮৩৪ সালের ১৪ মে, নরসিংদীর সদর উপজেলার মেহেরপাড়ায় কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক গিরিশ চন্দ্র সেনের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৫-০৮-১৯১০ তারিখ। তিনি ১৮৮০ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত টানা সাত বছর কাজ করে কোরআন শরিফের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার হোমনাবাদ পরগনার পশ্চিমগাঁও-এ নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৯-১৯০৩ তারিখ। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কুমিল্লা জেলার প্রথম নবাব উপাধি পান। ১৮৩৮ সালের ২৬ ফেব্রæয়ারি, মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘরের পশ্চিম ঘোষপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন প্রতিথযশা এ আইনবিদ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, মৃত্যু-জানা নেই। ১৯০৬ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন, বাংলা উপন্যাসিক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম; মৃত্যু-০৮-০৪-১৮৯৪ তারিখ। ১৮৪০ সালের ১১ মার্চ, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবি, দার্শনিক, গনিতজ্ঞ, বাংলা শর্টহ্যান্ড ও স্বরলিপির উদ্ভাবক, চিত্রশিল্পী ও স্বদেশ প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যু-১৯-০১-১৯২৬ তারিখ।
১৮৪০ সালে হুগলি জেলা নিবাসি দেলোয়ার হোসেন আহমেদ বা মির্যা দেলোয়ার হোসেনের জন্ম (মুসলমানের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৩ সালে) মৃত্যু-১৯১৬ সালে। ১৮৪০ সালে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার অমৃতবাজার গ্রামে সংবাদপত্রের জগতের কিংবদন্তি শিশির কুমার ঘোষের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১০-০১-১৯১১ তারিখ। ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রæয়ারি, প্রকাশ করেন ‘সাপ্তাহিক অমৃতবাজার’ পত্রিকা । ১৮৭১ সালে সপরিবারে কলকাতায় গিয়ে সেখান থেকেই ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ বের করতে থাকেন। ১৮৯১ সালে পত্রিকা দৈনিক হিসেবে প্রকাশ হতে থাকে। ১৮৪৪ সালের ২৮ ফেব্রæয়ারি, নাট্যকার, পরিচালক ও বাংলা নাটকের লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম, মৃত্যু-১০-০১-১৯১১ তারিখ। ১৮৪৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার পেয়ারাকান্দি গ্রামের কাজী বাড়িতে নবাব সিরাজুল ইসলামের জন্ম, মৃৃত্যু-১৯২৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে নবাব সিরাজুল ইসলাম ১৮৬৮ সালে বি. এ. পাশ করেন (কুমিল্লা জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট) এবং কিছুকাল তিনি পোগোজ হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত থাকেন। পরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী চলে যাবার পর কলকাতা আইন কলেজ থেকে আইন পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজী শিক্ষিত প্রথম মুসলমান এডভোকেট ছিলেন। সিরাজুল ইসলাম ১৯০৬ সালে ‘নবাব’ উপাধি পান। ১৮৪৬ সালে ঢাকার নবাব স্যার খাজা আহসান-উল্লাহর জন্ম, মৃত্যু-১৬-১২-১৯০১ তারিখ। ১৮৪৭ সালের ১১ ফেব্রæয়ারি, কানাডার মিলানে মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের জন্ম এবং মৃত্যু-১৮-১০-১৯৩১ তারিখ। ১৮৪৭ সালের ৩ মার্চ, এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ডে, আলেকজান্ডার গ্রাহামবেলের জন্ম, মৃত্যু-০২-০৮-১৯২২ তারিখ। ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর, কুষ্টিয়া জেলার গৌরী নদীর তীরে লাহিনীপাড়া গ্রামে ‘বিষাদসিন্ধু’র রচয়িতা ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেনের জন্ম, মৃত্যুঃ ১০-১২-১৯১২ তারিখ।
১৮৪৯ সালের ৬ এপ্রিল, উড়িষ্যার কটকে বিচারপতি স্যার সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম; মৃত্যু-০৩-০৮-১৯২৮ তারিখ লন্ডনে। ১৮৭৩ সালে সৈয়দ আমীর আলী ব্যারিস্টার হন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রিভি কাউনসিল হন সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৯০ সালের ২ জানুয়ারি, সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের মুসলমানের মধ্যে প্রথম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৮ সালে এম. এ. (ইতিহাস)-এ পাস করেন হুগলি কলেজ থেকে, তিনি বাঙালি মুসলমানের মধ্যে প্রথম এম. এ. পাস এবং প্রথম ব্যারিস্টারও তিনি। ১৮৪৯ সালে বিক্রমপুরের গাড়ডুগা গ্রামে প্রখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক রাজকুমার সেনের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। পদার্থ বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনাসহ জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৮৫৪ সালের ২১ ডিসেম্বর, সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী গ্রামের বিখ্যাত জমিদার, বাংলার মরমী কবি ও সাধক হাছন রাজার জন্ম, মৃত্যুঃ ০৭-১২-১৯২২ তারিখ। মরমী কবি হাছন রাজা হলো দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নানা। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই, ইংল্যান্ডের ভুবলিন শহরে নোবেল বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ’র জন্ম, মৃত্যু-০২-১১-১৯৫০ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯২৫ সালে নোবেল পান। ১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারি, বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার অন্তর্গত বাটোজোর একটি ছোট গ্রামের সচ্ছল কায়স্থ ভূম্যধিকারী পরিবারে জনহিতৈষী ও জাতীয়তাবাদী নেতা এডভোকেট অশিনীকুমার দত্তের জন্ম, মৃত্যু-০৭-১১-১৯২৩ তারিখ। ১৮৫৬ সালে পেনসিলভানিয়ার ক্রেসনে উত্তর মেরুজয়ী মার্কিন অভিযাত্রী রবার্ট পিয়েরির জন্ম, ১৯২০ সালে মারা যান। ১৯১১ সালে রিয়ার এডমিরাল হিসেবে অবসর নেন পিয়েরি। ১৯০৯ সালের ৬ এপ্রিল, বহু দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী ম্যাথু হ্যানসন ও চারজন দুঃসাহসী এস্কিমো নিয়ে প্রথম পা রাখলেন আর্কটিকের উত্তর মেরুতে রবার্ট পিয়েরি। উত্তর মেরুজয়ের ১০০ বছর পুরো হবে ০৬-০৪-২০০৯ তারিখ। ১৮৫৭ সালের ৮ নভেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের সাদক ফকির আফতাব উদ্দিন খাঁর জন্ম, মৃত্যু-২৫-০১-১৯৩৩ তারিখ। ১৮৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর, যুক্তরাষ্টের ২৬তম প্রেসিডেন্ট থিডোর রুজবেল্টের জন্ম, ১৯১৯ সালের ৬ জানুয়ারি, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের মৃত্যু।
১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর, বিজ্ঞানী স্যার জগদীস চন্দ্র বসু ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন (মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের রাড়িখাঁল গ্রামে বাবার বাড়ি), ২৩-১১-১৯৩৭ তারিখ গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন ফরিদপুরের একটি স্কুলে। তারপর ১১ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে সেন্ট জিভিয়ার্স স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১৮৭৫ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৭৯ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৮৯৬ সালে লন্ডন ভার্সিটি থেকে ‘ডক্টর অব সাইন্স’ উপাধি পান। ১৮৫৮ সালে বাঙ্গালী ঐতিহ্য ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ইরানী বংশোদ্ভূত বাংলাকাব্যের মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ, মৃত্যুবরণঃ ২১-০৭-১৯৫১ তারিখ। ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বিটঘর গ্রামে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৯৪৩ সালে। মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আর্থানুকূলে ২৫টির অধিক উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব পরিচালিত হয়। উনার বাবার নামে কুমিল্লা ইশ্বর পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৮ সালে উপমহাদেশের নন্দিত গণিতসম্রাট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার কামারচন্দ্র থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২৬-১১-১৯২৩ তারিখ। তিনি ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স, ১৮৭৮ সালে এফ. এ., ১৮৮০ সালে বি.এ. পাস করেন এবং ১৮৮৬ সালে গণিতে এম. এ. পাস করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। বি. এ. পাস করার পর ১৮৮১ সালে ছয় বছর মিশন কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৭ থেকে একাদিক্রমে ২৮ বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯১৫ সালে অবসর নেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৮৫৯ সালের ১১ জানুয়ারি, ভারতের ভাইসরয় লর্ড জর্জ কার্জন জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২০-০৩-১৯২৫ তারিখ। ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক, শার্লক হোমসের রচয়িতা স্যার আর্থার বোনান ডয়েলের জন্ম, মৃত্যু-১৯৩০ সালে। ১৮৫৯ সালের ২৩ অক্টোবর, যশোরের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের জন্ম, মৃত্যু-২৪-১০-১৯৩২ তারিখ। ১৮৮১ সালে এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দীর্ঘকাল ছিলেন যশোর পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান, যশোর জেলা বোর্ডের প্রথম মনোনীত চেয়ারম্যানও।
১৮৬১ সালের ৭ মে, (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বাংলা) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যু-০৭-০৮-১৯৪১ তারিখ। ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মৃণানিলী দেবীর বিয়ে হয়। তিনি ১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর, নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙ্গালীদের মন জয় করেছিলেন। ১৮৬১ সালের ১৮ জুলাই, প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর জন্ম, (১৮৮৬ সালে প্রথম ভারতীয় ডিগ্রিপ্রাপ্ত নারী চিকিৎসক ছিলেন) মৃত্যুঃ ০৩-১০-১৯২৩ তারিখ। ১৮৬১ সালে ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগনার নরসিংদী গ্রামে কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য্যরে জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৫-১৯৪১ তারিখ। ১৮৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, ভারতের কাশ্মীরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনীতিবিদ পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর জন্ম, মৃত্যুঃ ০৬-০২-১৯৩১ তারিখ। ১৮৬২ সালের ১০ নভেম্বর, ইংল্যান্ডের উম্বারল্যান্ডের হেপসকট শহরে রমনা-নিসর্গের স্থপতি রবার্ট লুইস প্রাউডলকের জন্ম, মৃত্যু-১৯৩৬ সালের পরে হবে, জানা নেই। প্রায় ১০০ বছর আগে তিনি রাজধানী শহর ঢাকাকে উদ্যানের নগর হিসেবে গড়ে তুলতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, সেই অসামান্য অবদানের জন্য তিনি আমাদের কাছে নমস্য হয়ে থাকবেন। ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার, নবীনগর উপজেলার, শিবপুর গ্রামে সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ’র জন্ম, মৃত্যু-মাইসুর, কলকাতাঃ ০৬-০৯-১৯৭২ তারিখ। ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারি, আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার ‘জনক’ তিনি হলেন ফ্রান্সের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ব্যারন পিয়ের দ্য কুব্যাঁর্ত্যাের জন্ম, মৃত্যু-০২-০৯-১৯৩৭ তারিখ। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি, হিন্দুধর্ম ও সমাজ সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, ০২-০৭-১৯০২ তারিখ ৯টা ৫০মিনিটের সময় মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৬৩ সালের ১০ মে, কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার মাছূয়া গ্রামের রায় পরিবারে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ২০-১২-১৯১৫ তারিখ। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ছিলেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু। উপেন্দ্র কিশোর রায় ১৮৯৪ সালের দিকে কলকাতায় বইছাপা কারখানা দেন এবং পরে নিজেই পাবলিসারস হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৬৩ সালে ফেনী জেলার শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক খান বাহাদুর আবদুল আজীজের জন্ম, মৃত্যু-১৯২৬ সালে। তাঁর পিতা আমজাদ আলী ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী। আবদুল আজীজ ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বি.এ. পাস করে। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। পরিচয় হলোঃ কবি হাবিবুল্ল¬াহ বাহার ও কবি শামসুন নাহারের নানা। ১৮৬৩ সালে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিখ্যাত চিকিৎসক এবং শিক্ষাবিদ ডা. হাকিম আজমল খানের জন্ম, মৃত্যু-১৯২৭ সালে। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং অল ইন্ডিয়া খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।
১৮৬৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল, নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৭-০৪-১৯২৯ তারিখ। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম মন্ত্রী, বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন, প্রধান বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় কলকাতা মলঙ্গা লেনের এক বাসাবাড়িতে এবং ২৫-০৫-১৯২৪ সালে পাটনায় হঠাৎ-ই পরলোগমন করেন। ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর ঝালকাঠি জেলার বাসন্ডা গ্রামে কবি কামিনী রায়ের জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৯-১৯৩৩ তারিখ। তিনি ১৫ বছর বয়সেই লিখেছেন প্রথম কবিতাগ্রন্থ “আলো ও ছায়া”। ১৮৬৬ সালে নাছিরনগর উপজেলার গোকর্ণ গ্রামে নবাব স্যার সৈয়দ শামসূল হুদার জন্ম, (সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন) মৃত্যু-১৯২২ সালে। ১৮৬৬ সালে চীনা জাতীয়তাবাদী নেতা সানইয়াৎ সেনের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৩-১৯২৫ তারিখ। ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর, ওয়রশতে পোলিশ বংশোদ্ভূত ফরাসি রসায়নবিদ ও বিশ্বের প্রথম তেজস্ক্রিয় মৌল পোলোনিয়ামের আবিস্কারক মেরি কুরীর জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৭-১৯৩৪ তারিখ। ১৮৯৮ সালে প্যারিসে খনিজ পিচবেøন্ড থেকে-পোলোনিয়াম নিস্কাশন করেন। পরবর্তী সময় একই বছরেই তিনি রেডিয়াম নামের আরেকটি তেজস্ক্রিয় মৌল আবিস্কার করেন। ১৮৬৭ সালে সিলেট জেলায় গজনফর আলী খানের জন্ম (গজনফর আলী খান ১৮৯৭ সালে অবিভক্ত ভারতের প্রথম বাঙালি মুসলিম আই.সি.এস. অফিসার ছিলেন) মৃত্যু-২৬-০৩-১৯৫৯ তারিখ। ১৮৬৭ সালের ১৬ এপ্রিল, অরবিল রাইট আমেরিকান ইন্ডিয়ানা প্রদেশে জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৫-১৯১২ তারিখ। ১৮৭১ সালে উইলবার রাইট আমেরিকান ইন্ডিয়ানা প্রদেশে জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৫-১৯৪৮ তারিখ। ১৯০৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাদের নির্মিত উড়োজাহাজের সফল উড্ডয়ন ঘটান। এরা দুই-ভাই বিমান উৎপাদন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। ১৮৬৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলায় বাংলা চলচ্চিত্রের জনক ও প্রবাল পুরুষ হীরালাল সেনের জন্ম, মৃত্যু-২৯-১০-১৯১৭ তারিখ। ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল, বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।
১৮৬৮ সালের ২৮ মার্চ, রাশিয়ায় বিপ্লবী সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম, মৃত্যু-১৮-০৬-১৯৩৬ তারিখ। ১৮৬৮ সালের ৭ জুন, পশ্চিম বাংলার উত্তর ২৪(চব্বিশ) পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ’র জন্ম, ১৯৬৮ সালের ১৮ আগষ্ট, তিনি ঢাকাতে ইন্তেকাল করেন। ১৯০৩ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে তিনি দৈনিক আজাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ সালের ৩০ এপ্রিল, ভারতের সিনেমা জগতের অগ্রদূত দাদা সাহেব ফালকে’র জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৯১২ সালে ভারতের বোম্বে প্রথম সিনেমা তৈরী করেন দাদা সাহেব ফালকে। ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর, গুজরাটে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম, আততায়ীর গুলিতে নিহতঃ ৩০-০১-১৯৪৮ তারিখ। ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল, রুশ বিপ্লবের নেতা ও মার্কসবাদের রুপকার ভøাদিমির ইলিচ মহামতি লেনিনের জন্ম, মৃত্যু-২২-০১-১৯২৪ তারিখ। ১৮৭০ সালের ৭ জুন, নবাব স্যার সলিমুল্লাহর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০১-১৯১৫ তারিখ। (রাত আড়াই ঘটিকায় কলকাতায় চৌরঙ্গীস্থ বাসভবনে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। পরদিন ১৭ জানুয়ারি, বিকেলে বিশেষ স্টীমারযোগে নবাবের মরদেহ ঢাকায় আনা হয় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বেগম বাজারস্থ পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। ১৯০৩ সালে দিল্লীর দরবারে সপ্তম অ্যাডওয়ার্ডের মুকুট পরিধান উৎসবে সলিমুল্লাহকে নবাব বাহাদুর উপাধি প্রদান করে ইংরেজ সরকার। ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর, মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার তেলিরবাগ গ্রামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম; মৃত্যুঃ ১৬-০৬-১৯২৫ তারিখ।
১৮৭০ সালে ড. স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন সোহরাওয়ার্দীর জন্ম, মৃত্যু-১৯৩৫ সালে কলকাতায়। তিনি ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী বাঙালি মুসলমান। ১৮৭১ সালের ৭ আগষ্ট, কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৫-১২-১৯৫১ তারিখ। ১৮৭১ সালের ১০ অক্টোবর, চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিশিষ্ট পুঁথি সংগ্রাহক ও লেখক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ৩০-০৯-১৯৫৩ তারিখ। ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর, ঢাকায় কবি, গীতিকার ও গায়ক অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম, লক্ষেèৗয়ে মৃত্যুঃ ২৬-০৮-১৯৩৪ তারিখ। ১৮৭২ সালের ৪ এপ্রিল, গুজরাটের বস্ত্র শিল্প অধ্যুষিত সুরাট নগরে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর জন্ম, (আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ১৮৯৫ সালে অবিভক্ত ভারতের প্রথম মুসলিম আই. সি. এস. অফিসার ছিলেন) মৃত্যু-১০-১২-১৯৫৩ তারিখ লন্ডনে। ২৩ বছর বয়সে তরুণ ইউসুফ আলী ভারতের নতুন আই. সি. এস. অফিসার হিসেবে, ১৮৯৬ সালে যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুরে এ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদেন। ১৮৭২ সালের ১৮ মে, ইংল্যান্ডের মনমর্ডিথশায়ারের রাভেনস্ক্রফ্ট শহরে নোবেল জয়ী সাহিত্যিক, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ বারট্রান্ড রাসেলের জন্ম, মৃত্যু-০২-০২-১৯৭০ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৫০ সালে নোবেল পান। ১৮৭২ সালের ১৫ আগষ্ট, কলকাতায় জাতীয়তাবাদী নেতা, আধ্যাত্মিক সাধক ও দার্শনিক অরবিন্দু ঘোষের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৫-১২-১৯৫০ তারিখ। ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার গুনিয়ক গ্রামে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, বি. সি. এল.-এর জন্ম, লন্ডনে মৃত্যুঃ ৩১-০৭-১৯১৭ তারিখ। তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা। ১৮৭২ সালের ১৬ অক্টোবর, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার খাসপুর গ্রামে সাহিত্য চর্চা, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক ও সাংবাদিক আবদুল গফুর সিদ্দিকীর জন্ম, মৃত্যু-১৯৫৯ সালে। ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাকেরগঞ্জের সাতুরিয়া গ্রামে তাঁর মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন, ঢাকায় মৃত্যু-২৭-০৪-১৯৬২ তারিখ। চাখারে তিনি একটি একতলা ইটের বাংলো বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালের ৩০ নভেম্বর, ইংল্যান্ডে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক উইনষ্টন চার্চিল জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২৪-০১-১৯৬৫ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে নোবেল পান। ১৮৭৫ সালের ৩০ অক্টোবর, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয়তাবাদী নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম, মৃত্যু-১৫-১২-১৯৫০ তারিখ। ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, বিখ্যাত কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম, মৃত্যু-১৬-০১-১৯৩৮ তারিখ।
১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর, করাচিতে (জিন্নার বাবা-মায়ের নাম ছিল জেনাভাই ঠক্কর এবং মিঠাভাই) জেনাভাই এবং মিঠাভাইয়ের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথা অনুসারে জেনাভাই নাম স্থির করেন, মিঠাভাই সম্মতি জানান। মুহম্মদ আলি জেনাভাই। মামলায় সম্পত্তি হারানোর পর ১৮৯৩ সালের জানুয়ারিতে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা আদায় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুহম্মদ আলি জেনাভাই ইংল্যান্ডে জিন্নাহ নাম ধারণ করে। করাচি থেকে ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে বম্বের দুর্গা মহল্লাতে থাকতে শুরু করেন মুহম্মদ আলি জিন্নাহর বাবা ও মা। জায়গাটা বম্বের কেল্লার ঠিক বাইরে। জিন্না খোজা মুসলিম ছিলেন। তিনি শিয়া গোষ্ঠীর ইথনা আশারি স¤প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। হিন্দু লোহানা, জাতি থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন খোজা স¤প্রদায়। যার মধ্যে হিন্দু-মুসলিম দুয়েরই মিশ্রণ। ভারতের গুজরাত প্রদেশে কাথিয়াবাড়ের অবস্থান, কচ্ছের বৃহৎ রানের তলায়। পশ্চিমে আরব সাগর তাকে ঘিরে রয়েছে, প্রসারিত হয়েছে স্থলের দিকে, উর্বর এবং সুজলা ‘একশো রাজত্বের’ ভূমি, ভাল নাম সৌরাষ্ট্র। কাথিয়াবাড় অর্থাৎ কাথিদের ভূমি, যেখানে পাওয়া যায় উত্তম কাথিয়াবাড়ি ঘোড়া, সুন্দরী-কাথি নারী, বিচক্ষণ বণিক এবং বহু ধনী বণিক পরিবার, হিন্দু এবং মুসলিম। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন-১১-০৯-১৯৪৮ তারিখ করাচিতে। তিনি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তবে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুর আচরণে তিনি আলাদা রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, এমনকি পাকিস্তানের জন্মের পরও জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তান কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না এবং এ রাষ্ট্র হবে সকলের জন্য সমান। জিন্নাহ এবং সরোজিনী নাইডু ইংল্যান্ডে একই সময়ে ছিলেন। জিন্না মঞ্চাভিনয় করার চেষ্টা করেছিলেন, হয়তো তা পেশা হিসেবে নেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। জিন্নাহ ও সরোজিনী নাইডু দুজনেই শিল্পে আগ্রহী ছিলেন, সরোজিনী কবি ও লেখক হিসেবে, জিন্না নাটকে। জিন্না ভারতবর্ষে একমাত্র ব্যক্তি জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একসাথে প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর, সাতক্ষিরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা গ্রামে শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লাহ’র জন্ম, মৃত্যু-০৯-০২-১৯৬৫ তারিখ। তিনি পরীক্ষায় রোল নম্বর সিস্টেম করেন, এর আগে পরীক্ষায় নাম লেখা থাকত। ১৮৭৭ সালের ৯ মে (বাংলা ১২৮৪ সালের ২৫ বৈশাখ) চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার গোমদন্ডী গ্রামে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীলের জন্ম, মৃত্যু-০৬-০৪-১৯৬৭ তারিখ। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কবিগানের আসরে রমেশ চন্দ্র শীলকে ‘বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল’ উপাধি দেন উদ্যোক্তারা। ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর, বিখ্যাত উর্দু মহাকবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে জন্ম এবং মৃত্যু-২১-০৪-১৯৩৮ তারিখ। ১৮৭৮ সালের ২৫ জানুয়ারি (বাংলা-১০ মাঘ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ), বি-বাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সাতমোড়া গ্রামে সাধক ও কবি মহর্ষি মনোমোহন দত্তের জন্ম, মৃত্যু-০৫-১০-১৯১০ তারিখ (বাংলা-২০ আশ্বিন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। মহর্ষি মনোমোহন দত্ত বেঁচেছিলেন ৩১ বছর ৮ মাস ১০ দিন। মানবতাবাদী মহর্ষি মনোমোহন দত্ত তাঁর স্বল্প আয়ুতে ২০টিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যার মধ্যে মলয়া (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) সবচেয়ে আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মলয়া কাব্যগ্রন্থে গানের সংখ্যা সর্বমোট ৪২৬টি। এর মধ্যে প্রথম খন্ডে ২৮৭ এবং দ্বিতীয় খন্ডে ১৩৯টি মরমি গান লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত এ মরমিসংগীত মলয়ার প্রতিটি গানের সুরারোপ করেছেন মনোমোহনের আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম সাথি ও শিষ্য ফকির আফতাব উদ্দিন খাঁ। এ ছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, যোগপ্রণালী, উপাসনা প্রণালী, উপবন, তপোবন, লীলারহস্য, আরাধনা, গিরিজা মালতি, প্রেম পরিজাত, পথিক, পাথেয়, দেববাণী প্রভৃতি। ১৮৭৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, বিক্রমপুরে বানাড়ি গ্রামে চারণ কবি, গায়ক, নাট্যকার, সমাজসেবক, অভিনেতা ও পরিচালক মুকুন্দ দাসের জন্ম এবং কলকাতায় মৃত্যু-১৮-০৫-১৯৩৫ তারিখ। ১৮৭৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর, সোভিয়েত নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান জোসেফ স্তালিনের জন্ম, মৃত্যু-০৫-০৩-১৯৫৩ তারিখ। ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ব্রাহ্মণগাঁও, বিক্রমপুরে ভারতের কবি, রাজনীতিবিদ, বাগ্মী, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী ও ‘প্রাচ্যের বুলবুল’ সরোজিনী নাইডুর জন্ম, লক্ষেèৗ গভর্নর হাউসে মৃত্যু-০১-০৩-১৯৪৯ তারিখ। তিনি ১৮৯১ সালে বার বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাস। সরোজিনী নাইডু ১৯৪৫ সালে অল-ইন্ডিয়া ওমেন্স কনফারেন্স এ সভাপতি নির্বাচিত হন। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত ১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু এ পদে দায়িত্ব পালন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ব্রাহ্মণগাঁও। তাঁর পিতার নাম ড. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিজামের শিক্ষা উপদেষ্টা। ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ, জার্মানে আপেক্ষিকতাবাদের জনক বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম এবং মৃত্যু-১৮-০৪-১৯৫৫ তারিখ আমেরিকাতে। ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই, সিরাজগঞ্জে মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতিক, কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম, মৃত্যু-১৭-০৭-১৯৩১ তারিখ। ১৮৮০ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ি উপজেলার রাউথভোগ গ্রামে হতদরিদ্র ঘরে সূর্য কুমার বসুর জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। এ কৃতীপুরুষ পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম ১৯২২ সালে ‘ঢাকেশ্বরী কটন মিলস’ নামে বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর, রংপুর জেলার পায়রা বন্ধ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম এবং মৃত্যু কলকাতায় ভোর রাতে-০৯-১২-১৯৩২ তারিখ। ১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সাথে। ১৯১৬ সালে কলকাতায় ‘আঞ্জুমানে খাদেমুন ইসলাম’ নামে মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করেন। ১৯২৯ সালে তিনি কলকাতায় প্রথম মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ সালের ২৫ অক্টোবর, বিশ্বখ্যাত স্পেনীয় চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর জন্ম, মৃত্যু-০৮-০৪-১৯৭৩ তারিখ। ১৮৮১ সালের ১৯ মে, আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা, স্থপতি ও মহান নেতা মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক পাশার জন্ম, ইন্তেকাল-১০-১১-১৯৩৮ তারিখ। ১৮৮২ সালের ৩০ জানুয়ারি, যুক্তরাষ্টের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৪-১৯৪৫ তারিখ। ১৮৮২ সােেলর ৯ এপ্রিল, লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা বাজার গ্রামে কবি ও সাহিত্যিক শেখ ফজলুল করিমের জন্ম, ইন্তেকাল ২৮-০৯-১৯৩৬ তারিখ। ১৮৮২ সালে ইংরেজী সাহিত্যের এক দিকপাল ভার্জিনিয়া উলফের জন্ম, আত্মহত্যা করেন-২৮-০৩-১৯৪১ তারিখ। ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন কেইনসের জন্ম, মৃত্যু-১৯৬৩ সালে। ১৮৮৩ সালে ইতালীর স্বৈরশাসক বেনিত্তো মুসোলিনির জন্ম, (স্ত্রীর নাম ছিল ক্লারেটা) সস্ত্রীক নিহত হন-২৮-০৪-১৯৪৫ সালে। ১৮৮৩ সালে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার উলানিয়া জমিদার পরিবারে মুসলিম ঐতিহ্য ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-০৩-০২-১৯৮১ তারিখ। ১৮৮৪ সালের ১২ মার্চ, টাঙ্গাইল জেলার বিল্লাইক গ্রামে আইনজীবী ও সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের জন্ম, মৃত্যু-১২-০২-১৯৬১ তারিখ। ১৮৮৪ সালের ৬ এপ্রিল, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার শ্রীকাইল গ্রামে নরেন্দ্রনাথ দত্তের (ক্যাপ্টেন দত্ত নামে সুপরিচিত) জন্ম, মৃত্যু-২১-০৯-১৯৪৯ তারিখ। তিনি শ্রীকাইল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪১ সালে। ১৮৮৪ সালের ২০ এপ্রিল, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার মিজিতলা গ্রামে বৌদ্ধ ধর্মগুরু ও সপ্তম সংঘনায়ক অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের জন্ম, মৃত্যু-০১-০৭-১৯৭৪ তারিখ। ১৮৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুর খাঁ পরিবারে উজ্জল রতœ ও সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ’র জন্ম, মৃত্যুঃ ০২-০৯-১৯৬৭ তারিখ। ১৮৮৪ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নাগবাড়ী গ্রামে সাবেক বঙ্গীয় আইন সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এবং বছরখানেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন (১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) এবং (১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতায় তদানীন্তন পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন) ও প্রাদেশিক পরিষদের সাবেক স্পীকার (১৯৬২-১৯৬৮) আব্দুল হামিদ চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৯-১৯৬৯ তারিখ। ১৮৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কালীকচ্ছ গ্রামের বাঘবাড়িতে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৭-০৫-১৯৬৫ তারিখ। ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় শিক্ষাবিদ, পন্ডিত, বহু ভাষাবিদ ও মনীষী ইমিরিটাস অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ’র জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ১৩-০৭-১৯৬৯ তারিখ। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত সালের জুন মাসে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান করে ২৩ বছর অধ্যাপনা করে ১৯৪৪ সালে (অব.)। ১৮৮৫ সালের ১২ ডিসেম্বর, পাবনা জেলা সিরাজগঞ্জ শহরের কিছু দূরে এবং যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ধানগড়া গ্রামে মওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৭-১১-১৯৭৬ তারিখ। ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ভাসানচরে এক বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে ‘‘ভাসানী’’ শব্দটি যুক্ত হয়।
১৮৮৬ সালের ২ নভেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে রামরাইল গ্রামে আইনজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিক শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের জন্ম, ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পাক আর্মী কুমিল্লার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং গুলিতে মৃত্যু-১৪-০৪-১৯৭১ তারিখ। উনি একমাত্র ব্যক্তি প্রথম পাকিস্তানের জাতীয় গণ-পরিষদে বলেছিলেন, বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর, কলকাতা শহরে শিশু সাহিত্যিক ও কবি সুকুমার রায়ের জন্ম, মৃত্যুঃ ১০-০৯-১৯২৩ তারিখ। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও কবি এবং ছড়াকার, শিশুদের জন্য। ১৮৮৭ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের জন্ম, মৃত্যু-০৮-০১-১৯৭৬ তারিখ। ১৮৮৭ সালের ৩১ অক্টোবর, চীনা যোদ্ধা এবং জাতীয়তাবাদী চীনের (বর্তমান তাইওয়ান) প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেকের জন্ম, মৃত্যু-০৫-০৪-১৯৭৫ তারিখ। ১৮৮৭ সালের ২২ অক্টোবর, দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের লেখক ও সাংবাদিক জন রীডের জন্ম, মৃত্যু-১৯..? ১৮৮৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার শ্যামগ্রাম গ্রামে রাখাল চন্দ্র রায়ের জন্ম, মৃত্যু-০২-১১-১৯৮৯ তারিখ ১০২(একশত দুই) বছর বয়সে। উনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর, ঢাকার ভাগ্যকুলে সংস্কৃত পন্ডিত, গবেষক ও শিক্ষাবিদ অমরেশ্বর ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যু-২৪-০১-১৯৭৯ তারিখ। ১৮৮৮ সালের ১ জানুয়ারি, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার কাঞ্চনা গ্রামে রায় সাহেব কামিনীকুমার ঘোষের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে। কলকাতা থেকে ফিরে এসে চাঁচা বঙ্গচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ১৯১৩ সাল থেকে আইন পেশায় নিযুক্ত হন। বিয়ের পর ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর ভারত শাসন আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে আইন পেশা ছাড়েন এবং আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি, বিক্রমপুরে রোহিনীকান্তের ঔরসে ও শরৎকামিনী দেবীর গর্ভে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর জন্ম, মৃত্যু-০৬-০২-১৯৪৭ তারিখ। ১৫৫৭ সালে মুঘল-পাঠানদের যুদ্ধের সময় কেদার রায়ের রাজ্যে বিক্রমপুর চলে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন টঙ্গীবাড়ি উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামেই বাস করত বাৎস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবার-ভট্টশালীরা। ১৮৮৮ সালের ২০ নভেম্বর, চাঁদপুর জেলার পাইকারদী গ্রামে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ‘সওগাত’ সম্পাদক ও বেগম পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের জন্ম, মৃত্যু-২১-০৫-১৯৯৪ তারিখ। ১৯১৭ সালে কলকাতা শহরে ‘সওকাত’ পত্রিকা প্রকাশ করে।
১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর, মক্কায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম, মৃত্যু-২২-০২-১৯৫৮ তারিখ (১৮৯০ সালে বাবা সপরিবারে কলকাতায় আসেন)। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পূর্বপুরুষেরা বাবরের আমলে হেরাট থেকে ভারতে আসেন। প্রথমে তাঁরা ডেরা বাধেন আগ্রায়; পরে ওঠে চলে যান দিল্লীতে। আলেমউলেমাদের এই পরিবারের মাওলানা জামালউদ্দিন ছিলেন আকবরের সময়ের একজন নামজাদা ধর্মগুরু। এ পরিবারের অনেকেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হন। শাহজাহানের আমলে মহম্মদ হাদীকে আগ্রার দুর্গাধিপতি করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবার মাতামহ ছিলেন মৌলানা মুনাবরউদ্দিন। তিনি ছিলেন মোগল যুগের অন্যতম শেষ রুকন-উল-মুদারসসিন। প্রথম শাহজাহানের সময়ে এ পদটির সৃষ্টি হয়। লেখাপড়া আর বিদ্যাচর্চার প্রসারে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের তদারকি করা ছিল এর উদ্দেশ্য। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবা মৌলানা খয়রুদ্দিন যখন খুবই ছোট তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পিতামহের মৃত্যু হয়। সুতরাং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবা তাঁর মাতামহের কাছে মানুষ হন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবার বয়স তখন পঁচিশ। তিনি সোজা মক্কায় চলে গিয়ে সেখানেই থেকে যান। নিজের একটি বাসভবন তৈরি করে শেখ মোহাম্মেদ জাহের বতবির কন্যাকে তিনি বিয়ে করেন। শেখ মোহাম্মেদ জাহের ছিলেন মদিনার একজন বড় তত্ত¡জ্ঞ। আরবদেশের বাইরেও তাঁর নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। মিশর থেকে দশ খন্ডের আরবী কেতাব বেরোবার পর ইসলামিক দুনিয়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবাও খ্যাতিমান হন। তিনি বহুবার বোম্বাইতে এবং একবার কলকাতায় আসেন। দু জায়গাতেই তাঁর বিস্তর ভক্ত আর শারগেদ ছিল। বাবা ইরাক, সিরিয়া আর তুরস্কেও ব্যাপকভাবে ঘুরেছেন।
১৮৮৮ সালের ৪ ডিসেম্বর, ফরিদপুর জেলার খন্দরপাড়ায় শিক্ষাবিদ ও বাঙালি ঐতিহাসিকদের পুরোধা অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ১২-০২-১৯৮০ তারিখ ভারতে। ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার গ্রামে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীর জন্ম এবং ১৯০৮ সালে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ১৮৮৯ সালের ১৬ এপ্রিল, যুক্তরাজ্যে ইংরেজ অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম, আমেরিকায় মৃত্যু-২৫-১২-১৯৭৭ তারিখ। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক রিলের নির্বাক ‘‘মেকিং এ লিভিং’’ দিয়ে মহান চলচ্চিত্রশিল্পী চ্যাপলিনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল, জার্মান ফ্যাসীবাদী একনায়ক এডলফ হিটলারের জন্ম হয় অস্ট্রিয়ায়, ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল, চুড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে ভূ-গর্ভস্থ বাঙ্কারে এডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন। (মৃত্যু-১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল ইংলিশ চ্যানেলের ওপর ব্রিটিশ বৈমানিকের গুলিতে হিটলারকে বহনকারী বিমান ভূপাতিত। হিটলার নিহত হয়েছেন, তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে লন্ডনে। ২১ বছর বয়সী হ্যারিকেন জেট ফাইটার প্লেনের বৈমানিকের গুলিতে ফুয়েরারকে জার্মান বিমানটি ভূপাতিত হয় ইংলিশ চ্যানেলের ওপর। ধারনা করা হচ্ছে, জার্মান নেতা দ্বীপরাষ্ট্র ইংল্যান্ড আক্রমণের অগ্রগতি সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার অনির্ধারিত অভিযানে ছিলেন।) হিটলারের জার্মান নাগরিত্ব বাতিল করা হয়। হিটলার নিজেই ইহুদি এবং উত্তর আফ্রিকান বংশোদ্ভুত।
১৮৮৯ সালের ৫ আগষ্ট, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি-১৯২০) কমরেড মুজাফফর আহমদের জন্ম নোয়াখালী জেলার স›দ্বীপে, মৃত্যুঃ ১৮-১২-১৯৭২ তারিখ কলকাতায়। ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৫-১৯৬৪ তারিখ। ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনিপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে বিপ্লবী ক্ষুধিরাম বসুর জন্ম, পালাবার সময় ক্ষুধিরাম গ্রেফতার হন এবং ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী ক্ষুধিরামের ফাঁসি কার্যকর হয়-১১-০৮-১৯০৮ তারিখ। ক্ষুধিরাম বড় লাটকে মারতে যেয়ে মেরে ফেলে ভারতবাসীকে। ১৮৮৯ সালে ভারতের জলপাইগুড়িতে শিক্ষাবিদ স্যার আহমদ ফজলুর রহমানের জন্ম, মৃত্যু-১৯৪৫ সালে। উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৮৯০ সালে চারসাদ্দাই তহশিল, জেলা পেশোয়ারে সীমান্ত গান্ধীর নাম, ভারত-রতœ বাদশা খান বা খান আবদুর গফফার খানের জন্ম, ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবাদ পুরুষ মৃত্যু-২০-০১-১৯৮৮ তারিখ। (তাঁর আসল বয়স-এর চাইতে অনেক বেশি বা কেউ মনে করে যে, ১৮৮০ সালে প্রকৃত জন্ম)। তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক। ১৮৯০ সালের ১৯ মে, ভিয়েতনামের বিপ্লবী জন নেতা হো. চি. মিনের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৯-১৯৬৯ তারিখ। ১৮৯০ সালের ২ অক্টোবর, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম, তাসখন্দে মৃত্যুঃ ২৩-০৯-১৯৬৫ তারিখ। ১৮৯০ সালে ফদিপুরে অবিভক্ত বাংলার অন্যতম তেজস্বী মুসলিম লীগ নেতা, প্রথম মুসলমান সরকারী কৌসুলি, ফরিদপুর আইনজীবী সমিতির সুদীর্ঘকালের সভাপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একদা প্রবীণতম আইনজ্ঞ খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইলের জন্ম, মৃত্যু-ঢাকায় ০৮-০৫-১৯৮১ তারিখ। ১৮৯০ সালে পাঁচবাগ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী (জাতীয় সংসদে স্বীকৃত) এবং একাধারে তিন দশক ধরে নির্বাচিত এম.এল.এ. ও এম.এন.এ. হয়রত মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী(রহ.)’র জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৯-১৯৮৮ তারিখ। ১৮৯০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামে নবাব কে. জি. ফারুকীর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৯৮৪ সালে। তিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবাংলার মেদেনীপুরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ০৫-১২-১৯৬৩ তারিখ। ১৮৯২ সালের ২৭ নভেম্বর, বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক ও লেখক স্যার আজিজুল হকের জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৩-১৯৪৭ তারিখ। ১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল, বিপ্লবী রাহুল সাংকৃত্যায়ণের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৪-০৬-১৯৬৩ তারিখ। ১৮৯৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নূরুল আমীনের জন্ম, পাকিস্তানে মৃত্যুঃ ০২-১০-১৯৭৪ তারিখ। ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বংশাই নদীর তীরে শেওরাতলী গ্রামে দারিদ্রপীড়িত এক পরিবারে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ মেঘনাথ সাহার জন্ম, মৃত্যু-১৯৫৬ সালে বিখ্যাত এই জ্যোতিঃ পদার্থবিদ মৃত্যুবরণ করেন। দোকানদার বাবার ছেলে হিসেবে সবাই ভেবেছিল ছেলেটিও দোকানি হবে। ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স ও ১৯১১ সালে এফ. এ. পাস করেন। তিনি জগৎ বিখ্যাত পদার্থ ও অংক শাস্ত্রবিদ। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
১৮৯৪ সালের ১৯ জুলাই, ঢাকায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের জন্ম, রাজনীতিবিদ খাজা নাজিমুদ্দিনের ইন্তেকাল-২২-১০-১৯৬৪ তারিখ। খাজা নাজিমউদ্দিনকে ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে উৎখাত করেন গোলাম মোহাম্মদ ও আইয়ূব খানের সহযোগিতায় তখনকার পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। মীর জাফরের বংশধর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। ইরানি বংশদ্ভূত এস. পি. টুনি মির্যার ছেলে হলো মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। ইস্কান্দার মির্যার জন্ম বাংলায় ছিল। সেনাবাহিনীর সহায়তায় ১৯৫৫ সালে ইস্কান্দার মির্যা পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদ দখল করেন। আর বরখাস্ত করেন মোহাম্মদ আলীকে। ১৯৫৬ সালে আরেক বাঙালি রাজনীতিক হোসেন শহীদ সোহওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। আর নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা দেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করে ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর, প্রধান সেনাপতি আইয়ূব খানকে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যাকে দেশত্যাগে বাধ্য করে নিজে জেনারেল আইয়ূব খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। আবার ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ, জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। সে বছরই সাবেক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যা লন্ডনে মারা যান। কিন্তু তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্টকে নিজ দেশে দাফনের অনুমতি দেননি। তাই লন্ডন থেকে ইস্কান্দারের মরদেহ ইরানে নেওয়া হয় এবং পরে তেহরানে তাঁকে দাফন করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের সাথে এটি ছিল সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে বারবার রাজনীতিতে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করেছে। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন। তারপর আবার ১৯৯৮ সাল থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন জেনারেল (অব.) পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৯ সালে ইস্কান্দার মির্যাকে তেহরানে দাফন করা হলেও তাঁর প্রেতাত্মা এখনো জীবিত। শুধু নাম বদল হয়েছে, কিন্তু চরিত্র বদলায়নি। জেনারেল আইয়ূব খান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল জিয়াউল হক এবং জেনারেল পারভেজ মোশাররফ হোসেন হয়ে বেঁচে ছিলেন।
১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট নেতা ও কমরেড মাও সে তুং-এর জন্ম, মৃত্যু-০৯-০৯-১৯৭৬ তারিখ। ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ, চট্টগ্রামে মাস্টার দা সূর্যসেনের জন্ম, ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নায়ক মাষ্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি হয়। ১৮৯৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার বিরামদি গ্রামে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ’র জন্ম, ইন্তেকাল-২৯-০৩-১৯৭৮ তারিখ। ১৮৯৪ সালে রংপুরে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রি আবু হোসেন সরকারের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৭-০৪-১৯৬৯ তারিখ। ১৮৯৪ সালে নোয়াখালীতে বিট্রিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও সমাজসেবিকা আশালতা সেনের জন্ম, মৃত্যু-দিল্লীতে ০৩-০২-১৯৮৬ তারিখ। ১৮৯৬ সালে পূর্ব পাঞ্জাবের কার্নায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের জন্ম, রাওয়ালপিন্ডিতে জনসভায় বক্তৃতাকালে আততায়ীর গুলিতে নিহতঃ ১৬-১০-১৯৫১ তারিখ। ১৮৯৬ সালের ৪ নভেম্বর, রনদা প্রসাদ সাহার জন্ম, মির্জাপুর (টাংগাইল), যার নাম আরপি সাহা। ১৯৩৮ সালে ৭৫০(সাতশত পঞ্চাশ) শয্যাবিশিষ্ট বিখ্যাত কুমুদিনী হাসপাতাল স্থাপন করেন। ০৭-০৫-১৯৭১ তারিখ, গভীর রাতে পাক বাহিনী রনদা প্রসাদ সাহা ও তার একমাত্র পুত্র রবিকে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। ১৮৯৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, বি-বাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মরিচাকান্দি গ্রামে বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে প্রথম ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মিজানুর রহমানের জন্ম, মৃত্যু-১৫-০৮-১৯৮১ তারিখ। তিনি ১৯২৬ সালে প্রথম বি. সি. এস. লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসুর জন্ম, নেতাজি মৃত্যুবরণ করেছেনঃ ১৮-০৮-১৯৪৫ তারিখ রাত ১১টা ২০মিনিটের সময় তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায়। ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই, কুষ্টিয়ার কুুমারখালী উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের মাতুলালয়ে বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস, ইমিরিটাস অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম, মৃত্যুঃ০৯-১০-১৯৮১ তারিখ। তার ছোটবেলা কেটেছে রাজবাড়ী (ফরিদপুর) জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামের পৈত্রিক নিবাসে। ১৮৯৭ সালের ৩ নভেম্বর, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৩-১৯৭৮ তারিখ। ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বর, বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার নরোত্তমপুর গ্রামে উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, নারীপ্রগতি ও মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ মনোরমা বসুর জন্ম, মৃত্যু-১৯৯০ সালে।
১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর, কিশোরগঞ্জ জেলায় “বাঙ্গালী থাকিব না মানুষ হইব’’ বইয়ের লেখক নিরুদ চন্দ্র চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-১৯৯৯ সালে লন্ডন শহরে। ১৮৯৭ সালের ২১ ডিসেম্বর, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম, মৃত্যুঃ ১৩-১০-১৯৬৪ তারিখ। ১৮৯৮ সালের ১ মে, চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ গ্রামে কথাশিল্পী মাহবুব-উল-আলমের জন্ম, ১৯৮১ সালের ৭ আগষ্ট কাজীর দেউড়ীস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের জন্ম, ইন্তেকাল-১৮-০৩-১৯৭৯ তারিখ। ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই, বাংলা সাহিত্যির দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭২ সালে। ১৮৯৮ সালে বরিশালের সন্তান অকুতোভয় পাইলট ইন্দ্রনীল রায়ের জন্ম, মৃত্যু-১৮-০৭-১৯১৮ তারিখ। পাইলট ইন্দ্রনীল রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ রাখেন যে-বাঙ্গালীরা বীরের জাতি। ১৯১৬ সালে বিশ্বে প্রথম বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় ‘‘ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীতে ক্যাডেট পাইলট হিসাবে তিনি লাভ করেন কিংস কমিশন’’। ১৮ জুলাই তাঁর জঙ্গী বিমানটি ফের গুলি বিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হয়। বিধবস্ত বিমানের সাথে তিনি প্রাণ হারান। মাত্র ২০(বিশ) বছর আয়ু পেয়েছিলেন। ‘‘পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য, তাদের মধ্যে ইন্দ্রনীল রায় একজন…এ অঞ্চলের একমাত্র ফাইটার এইস পাইলট হিসাবে তিনি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।’’ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রæয়ারি, বরিশাল জেলায় বাংলা আধুনিক কাব্যবিক জীবনানন্দ দাশের জন্ম, ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর, কলকাতায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু।
১৮৯৯ সালের ২৫ মে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-০৭-১৯৭৬ তারিখ বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা বেজে ১০ মিনিটে। ১৯২১ সালের ১৭ জুন, নজরুলের সঙ্গে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের সৈয়দা নার্গিস আসর খানম ওরফে সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয়। অজ্ঞাত কারণে বিয়ের রাতেই শেষ হয়ে যায় এ সম্পর্ক। পরে ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল, প্রমীলাকে বিয়ে করেন নজরুল। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই থেকে কবি আলজাইমার্স ডিজিজে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ। মা জাহিদা খাতুন। ১৯১৭ সালে করাচীতে গিয়ে তিনি সৈনিকের খাতায় নাম লেখান। তিনি ১৯২০ সালে সেখান থেকে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজকে উৎসর্গ করেন। কবি-পতœী প্রমীলা নজরুল ইসলাম কলকাতায় ইন্তেকালঃ ৩০-০৬-১৯৬২ তারিখ। কবি-পতœীর ইন্তেকালের প্রায় এক দশক পর কবিকে ঢাকায় আনা হয়েছিল ২৪ মে, ১৯৭২ সালে। ১৮৯৯ সালের ২৮ জুন, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার হুমায়ূনপুর গ্রামে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনয়েম খানের জন্ম, মৃত্যু-১৪-১০-১৯৭১ তারিখ। গভর্নর ছিলেন ২৮-১০-১৯৬২ তারিখ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৯ তারিখ পর্যন্ত। ১৮৯৯ সালে যশোর জেলার ঝিনাইদহের অধিবাসী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের রোমান্সকর ব্যক্তিত্ব বাঘা যতীন দাসের জন্ম, ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, ৬৩ দিন অনশনের পর লাহোর কারাগারে মারা যান। ১৯০০ সালের ১৯ মার্চ, নোবেল বিজয়ী ফরাসী পদার্থবিদ ফ্রেদেরিক জুলিও কুরির জন্ম, ১৯৫৬ সালের ১৭ মার্চ, নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ জোলিও কুরির মৃত্যু।
১৯০০ সালের ৮ মে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মাড় গ্রামের মাতুলালয়ে স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ০৩-১১-১৯৭৭ তারিখ। ১৯০০ সালে সিলেটে আদর্শিক বাবা-মায়ের পরিবারে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিকন্যা, নারীনেত্রী ও দেশব্রতী লীলা রায়ের (নাগ) জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১১-০৬-১৯৭০ তারিখ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। ১৯০০ সালের ১৭ মে, ইরানের খোমেইন শহরে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু ও রাজনৈতিক নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনীর (রহ.) জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৬-১৯৮৯ তারিখ। ১৯০০ সালের ২৭ নভেম্বর, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত হাটিকুমরুল ইউনিয়নের তারুটিয়া নামক গ্রামের সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে কিংবদন্তী পুরুষ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের জন্ম, মৃত্যুঃ ২০-০৮-১৯৮৬ তারিখ। ১৯০০ সালে দিনাজপুর জেলার সুলতানপুর গ্রামে কৃষকনেতা ও রাজনীতিক হাজী মোহাম্মদ দানেশের জন্ম, মৃত্যু-২৮-০৬-১৯৮৬ তারিখ। ১৯০০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে বেহালাবাদক, কন্ঠশিল্পী, সুরকার ও সঙ্গীত শিক্ষক ওস্তাদ মতিউর রহমানের জন্ম, মৃত্যুঃ ০১-০২-১৯৬৭ তারিখ। ১৯০০ সালে বরিশাল জেলায় বিপ্লবী লেখক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম, মৃত্যু-১৯৮৫ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিন খন্ড রচনা সমগ্র প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর লেখা-লেখি করার ওপর বিধিনিষেধ করেছিলেন। ১৯০০ সালের ৮ ডিসেম্বর, রাজস্থানের উদয়পুরে নৃত্যলোকের রাজপুত্র উদয়শংকরের জন্ম, মৃত্যুঃ২৬-০৯-১৯৭৭ তারিখ। তিনিই প্রথম বাঙালি, যিনি জগৎসভায় নৃত্যকলা প্রদর্শন ও প্রচার করে প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন। উদয়শংকরের আদি নিবাস বাংলাদেশের যশোরের কালিয়া গ্রামে। ১৯০১ সালের ৬ জুন, আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার স্থপতি ড. আহমদ সুকর্নোর জন্ম, মৃত্যু-২১-০৬-১৯৭০ তারিখ। ১৯০১ সালের ২৮ জুলাই, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহের জন্ম, মৃত্যুঃ ৩১-১২-১৯৯০ তারিখ। মাতৃকুল ছিলেন নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুরের জমিদার। ১৯০১ সালে ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার রামনগর গ্রামে সাংবাদিক ও রাজনীতিক হামিদুল হক চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৮-০১-১৯৯২ তারিখ। ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর, কুচবিহারের বলরামপুর গ্রামে মরমী শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের জন্ম, মৃত্যুঃ ৩০-১২-১৯৫৯ তারিখ। শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের পিতা জাফর আলী আহমেদ তুফানগঞ্জ আদালতের উকিল ছিলেন। ১৯০২ সালের ১৭ জানুয়ারি, তুরস্কের ছোট্ট শহর আলেপ্লোয় এক নিঃসঙ্গ বিপ্লবী ও বিখ্যাত তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৬-১৯৬৩ তারিখ। ১৯০২ সালের ১ জুলাই, ভারতের পশ্চিম বাংলায় রম্য সাহিত্যিক ও বহু ভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম, ঢাকায় ইন্তেকাল ১১-০২-১৯৭৪ তারিখ।
১৯০২ সালে বর্তমান চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার এক সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক, পাকিস্তানের প্রথম এফআরসিপি (ইউ. কে.) ও বাঙালী মুসলমানদের চিকিৎসা পেশার অগ্রদুত ডা. নওয়াব আলীর জন্ম এবং ঢাকায় ইন্তেকাল-০৪-০৭-১৯৭৭ তারিখ। ১৯০২ সালে পশ্চিমবাংলায় বাংলা সিনেমা জগতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ও নাঠ্যাভিনেতা ছবি (শচীন্দ্রনাথ) বিশ্বাসের জন্ম, মৃত্যু-১১-০৬-১৯৬২ তারিখ মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি, পল্লী কবি জসিমউদ্দীনের জন্ম, মৃত্যু ১৪-০৩-১৯৭৬ তারিখ। ১৯০৩ সালের ১৪ জানুয়ারি, বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় শিক্ষক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. নীহাররঞ্জন রায়ের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-৩০-০৮-১৯৭৮ তারিখ। তাঁর সৃষ্টি বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব। ১৯০৩ সালের ১ জুলাই, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত কেওচিয়া গ্রামে শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক মনস্বী আবুল ফজলের জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৫-১৯৮৩ তারিখ। ১৯০৩ সালের ২৯ অক্টোবর, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ইলমদী গ্রামে সাবেক জাতীয় পরিষদের সদস্য (এম.এন.এ.), ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, কবি ও সাংবাদিক বে-নজীর আহমেদের জন্ম, মৃত্যু-১২-০২-১৯৮৩ তারিখ। ১৯০৩ সালে ভারতের হায়দারাবাদ রাজ্যের আওরংগবাদ শহরে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদীর জন্ম, আমেরিকায় মৃত্যু-২২-০৯-১৯৭৯ তারিখ পাকিস্তান সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা পৌঁনে ছ’টায়। তিনি ১৯৪১ সালের ২৬ আগষ্ট, লাহোরে ৭৫ জন লোক নিয়ে ‘জামায়াতে ইসলামী’ নামে একটি আদর্শবাদী দল গঠন। ১৯০৩ সালের ১ ডিসেম্বর, চট্টগ্রামে বিপ্লবী (চট্টগ্রাম অস্্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম নায়ক এবং রাজনীতিবিদ) অনন্ত সিং-এর জন্ম, মৃত্যুঃ ২৫-০১-১৯৭৯ তারিখ। ১৯০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি, পাবনা জেলার সুজানগর থানার মুরারিপুর গ্রামে শিক্ষাবিদ ও লোকসংস্কৃতি বিশেযজ্ঞ মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের জন্ম, ঢাকার শান্তিনগরে মৃত্যু-১৯-০৯-১৯৮৭ তারিখ। ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ, অন্নদা শংকর রায়ের জন্ম, মৃত্যু-২৮-১০-২০০২ তারিখ। তিনি ১৯২৯ সালে আই.সি.এস. পাশ করেন। কবি, সাহিত্যক, ছড়াকার এবং ১৯২৯ সালে বিলেত গিয়েছিলেন। ১৯০৪ সালের ১২ জুলাই, চিলির পারলাল শহরে পরিচিত ছিল কমিউনিষ্ট লেখক হিসেবে ও নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক পাবলো নেরুদার জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৯-১৯৭৩ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে নোবেল পান।
১৯০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি, পশ্চিম বাংলায় দার্শনিক-রাজনীতিবিদ আল্লামা আবুল হাশিমের জন্ম, (১৯৫০ সালে পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিমবিরোধী সা¤প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং এ কারণে ১৯৫০ সালে আবুল হাশিম দেশ ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন) মৃত্যুঃ ০৫-১০-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৫ সালের ৬ মার্চ, ঢাকা জেলার দামরাই উপজেলার বালিয়া গ্রামে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের জন্ম, মৃত্যু-০৭-১২-১৯৯১ তারিখ। ১৯০৫ সালের ১৫ এপ্রিল, বরিশালের গৈলা গ্রামে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী শহীদ তারকেশ্বর সেনগুপ্তের জন্ম, বন্দিশিবির থেকে পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৫-০৯-১৯৩১ তারিখ। ১৯০৫ সালে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার গাজীপুর গ্রামে ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক আবদুল হালিমের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭২ সালে। ১৯০৫ সালে বিপ্লবী নেতা এবং ঐতিহাসিক নক্সালবাড়ী লড়াইয়ের সূচনাকারী শহীদ কমরেড চারু মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৮-০৭-১৯৭২ তারিখ। ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রæয়ারি, বাংলা সিনেমা জগতের বিখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা পাহাড়ী (নরেন্দ্রনাথ) সান্যালের জন্ম, মৃত্যু-১০-০২-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৬ সালের ১ জুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার আড়াইসিধা গ্রামে কবি আবদুল কাদিরের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৯-১২-১৯৮৪ তারিখ। ১৯০৬ সালে পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ূব খাঁনের জন্ম, (আইয়ূব খাঁন ১৯৫১ সালে পাকিস্তান আর্মীর সেনাপ্রধান হন এবং ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ূব খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।) মৃত্যুঃ ২০-০৪-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রসুল্লাবাদ গ্রামে দার্শনিক ও প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমানের জন্ম, মৃত্যু-২৮-০৮-১৯৮৭ তারিখ। ১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবর, সুনামগঞ্জের তেঘরিয়া গ্রামস্থ নানা মরমী কবি হাসন রাজার বাড়িতে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জন্ম, মৃত্যু-০১-১১-১৯৯৯ তারিখ। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর, কুমিল্লার চর্থা গ্রামে উপমহাদেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সুরকার শচীন দেব বর্মণের জন্ম, বোম্বে শহরে মৃত্যুঃ ৩১-১০-১৯৭৫ তারিখ।
১৯০৭ সালের ১ ফেব্রæয়ারি, সিলেট জেলার বিয়ানী বাজারের লাউতা গ্রামে অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেবের জন্ম, ঢাকায় শহীদঃ ১৪-১২-১৯৭১ তারিখ। ১৯০৭ সালের ২ ফেব্রæয়ারি, নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার চানগাঁও গ্রামে তাঁর নানাবাড়িতে খালেকদাদ চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-১৬-১০-১৯৮৫ তারিখ। দুই বাংলাতেই তিনি ছিলেন খ্যাতিমান লেখক। ১৯০৭ সালের ২৫ নভেম্বর, যশোর জেলার আলফাডাঙ্গার বুড়াইচ গ্রামে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক নূরুল মোমেনের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০২-১৯৯০ তারিখ। ১৯০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যালিয়াম সিরিজের ঘুমের বড়ি’র আবিস্কারক লিও স্টার্নবাখের জন্ম, উত্তর ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিলে নিজ বাসভবনে ৯৭ বছর বয়সে পরলোগমন-২৮-০৯-২০০৫ তারিখ। ১৯০৮ সালের ১ ফেব্রæয়ারি, বাগেরহাটের ফকিরহাট থানার সাতশৈয়া গ্রামে আবদুস সবুর খানের জন্ম, মৃত্যু-২৫-০১-১৯৮২ তারিখ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় খুলনা অঞ্চলকে জোর করেই হিন্দুস্থানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেদিন এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে খান এ সবুরের নেতৃত্বেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। যার ফলে তখন খুলনা অঞ্চল ন্যায়সঙ্গতভাবেই পাকিস্তানে রাখা সম্ভব হয়েছিল। ১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রæয়ারি, ভারতের বিশিষ্ট বাংলা শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৬-০৪-২০০৭ তারিখ। ১৯০৮ সালের ১ এপ্রিল, বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা ফরাসি লুসিয়ে লরাঁর জন্ম, মৃত্যু-১১-০৪-২০০৫ তারিখ। ১৯৩০ সালের ১৩ জুলাই, প্রথম বিশ্বকাপ হয়েছিল। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের মোট গোল হয়েছে (২০৬৩)টি।
১৯০৮ সালের ২৯ মে, সাহিত্যক, ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী মানিক বন্ধ্যোপ্যায়ের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৩-১২-১৯৫৬ তারিখ। মাত্র বেঁচেছিলেন ৪৮ বছর। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ২০০ শতের মত উপন্যাস লিখেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জের মালপদিয়া গ্রামে। ১৯০৮ সালে হাইড্রোজেন বোমার জনক এডওয়ার্ড টেনলরের জন্ম, মৃত্যু-০৯-০৯-২০০৩ তারিখ। ১৯০৮ সালে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক নড়াইলের বাকলি গ্রামের কৃষক নেত্রী পরিবালা বিশ্বাসের জন্ম, মৃত্যু-২৫-০৫-২০০৭ তারিখ। ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর, কুমিল্লা শহরে বিখ্যাত বাঙালি কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও সংবাদপত্র সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যুঃ ১৮-০৩-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৮ সালে মাদারীপুর জেলার কালকিনী উপজেলার গোপালপুর কাজী পরিবারে কাজী আশরাফ মাহমুদের জন্ম, মৃত্যু-০৩-১২-১৯৮৩ তারিখ। তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট হিন্দী কবি, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ, মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ১৯০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি, মুঘল ঐতিহ্যের কবি কাজী কাদের নওয়াজের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০১-১৯৮৩ তারিখ। ১৯০৯ সালের ২৯ এপ্রিল, (বাংলা ১৩১৬ সনের ১৬ বৈশাখ) শেরপুর অঞ্চলের তৎকালীন জমিদার রমেশ চন্দ্র নিয়োগীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রবি নিয়োগী, আমৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং মৃত্যু-১০-০৫-২০০২ তারিখ। তাঁর ৯৩ বছরের জীবনে ৪৩ বছরই কেটেছে কারাগারে। ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই, কলকাতার সুবিখ্যাত কলেজ স্ট্রিটের পাশে টেমার লেনে কবি বিঞ্চু দের জন্ম, মৃত্যু-০৩-১২-১৯৮২ তারিখ। বিঞ্চু দের এক বড় পরিচয় তিনি সমাজবাদে বিশ্বাসী, সেই সূত্রে সমাজবদলের সম্ভাবনায় অঙ্গীকৃত। তিনি ছিলেন ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সক্রিয় কর্মী, সংগঠক। ১৯০৯ সালের ১৮ আগষ্ট, উপমহাদেশের প্রখ্যাত সানাইবাদক ওস্তাদ সোনা মিয়ার জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৮-২০১১ তারিখ দিবাগত রাতে ঢাকায়। বরেণ্য এই শিল্পী ভারতবর্ষের স্বনামধন্য সানাইবাদক ওস্তাদ মুন্না খাঁর শিষ্য ছিলেন। ১৯০৯ সারের ১৯ সেপ্টেম্বর, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে গঠিত কমিটিতে নির্বাচিত কমিউনিষ্ট নেতা নেপাল নাগের জন্ম, মৃত্যু-কলকাতায় ০৫-১০-১৯৭৮ তারিখ। ১৯১০ সালের ৭ জানুয়ারি, খ্যাতিসম্পন্ন পানিবিশেষজ্ঞ বি. এম. আব্বাসের জন্ম, ইন্তেকাল-২৭-১২-১৯৯৬ তারিখ।
১৯১০ সালের ৫ ফেব্রæয়ারি, আর্জেন্টিনার প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলোয়াড় ফ্রান্সিসকো ভারাল্লোর জন্ম। তিনি ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ও ছিলেন এবং আর্জেন্টিনার পক্ষে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলে। প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই একমাত্র জীবিত খেলোয়াড়। তিনি ০৯-০৬-২০০৬ তারিখ বিশ্বকাপ খেলায় উপস্থিত ছিলেন। ০৫-০২-২০১০ সালে শতবর্ষ পার করেন। ১৯১০ সালের ২৩ মার্চ, জাপানের টোকিওর এক সিনেমাভক্ত পরিবারে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাপানি চলচ্চিত্রকার, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র সম্পাদক ও প্রয়োজক আকিরা কুরোশাওয়ারের জন্ম, জাপানের টোকিওতে মৃত্যু-০৬-০৯-১৯৯৮ তারিখ। সুগাতা সানশিরো মুক্তি পায় ১৯৪৩ সালে। প্রথম ছবিতেই পরিচালক হিসেবে আকিরা কুরোশাওয়ার প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। এন্টারটেইনমেন্ট উইকলি কর্তৃক নির্বাচিত সর্বকালের সেরা পরিচালকদের মধ্যে আকিরা কুরোশাওয়ার অবস্থান ৬ষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ ৫০ জন চলচ্চিত্রকারের মধ্যে তিনি একমাত্র এশীয় ও আমেরিকানদের বাইরে তাঁর অবস্থান সবার ওপরে। ১৯১০ সালের ২৭ আগষ্টে, যুগো¯øাভিয়ার স্কপজেতে মাদার তেরেসার জন্ম, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির প্রতিষ্ঠাতা মাদার তেরেসার মৃত্যু-০৫-০৯-১৯৯৭ তারিখ কলকাতা শহরে। ১৯১০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বাজালিয়ায় ডা. মনীন্দ্রলাল চক্রবর্তীর জন্ম, মৃত্যু-১৪-০৭-১৯৮৩ তারিখ। স্কুলে থাকতেই তিনি গোপন বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১০ সালের ২০ অক্টোবর, নেত্রকোনা জেলার উলুয়াটি গ্রামে সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুজীবুর রহমান খাঁ’র জন্ম, মৃত্যু-০৫-১০-১৯৮৪ তারিখ। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতের প্রথম গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারি, চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার উত্তর ভূর্ষি গ্রামে বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১০-০৪-২০১৩ তারিখ। তাঁর ১৯২৯ সালে মাস্টারদার সঙ্গে পরিচয় হয়। কয়েকবার সাক্ষাতের পর মাস্টারদা বিপ্লবী দলে ঢোকার অনুমতি দেন বিনোদবিহারীকে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ৪০ বছর পর ১৯৭১ সালে বিনোদবিহারী নিজেকে যুক্ত করেন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। ১৯১১ সালের ১১ জানুয়ারি, বিচারপতি সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুঃ ০৩-০৪-১৯৭৯ তারিখ। ১৯১১ সালের ১১ ফেব্রæয়ারি, পাকিস্তানের পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে আজন্ম বিপ্লবী কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্ম, ১৯৮৩ সালে অসুস্থ হয়ে নিজের দেশ পাকিস্তানের লাহোরে ফিরে আসেন, এখানেই মৃত্যু-১৯-১০-১৯৮৪ তারিখ। ১৯১১ সালের ১৩ মার্চ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৮-১৯৮৮ তারিখ। ১৯১১ সালের ৫ মে, চট্টগ্রামের ধলঘাটের দক্ষিণ সুরমা এলাকায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বীরকন্যা প্রীতিলতার জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৯-১৯৩২ তারিখ। প্রীতিলতা চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের মেয়ে সদস্য ও ছাত্রীদের নিয়ে চক্র গড়েন। ১৯১১ সালের ৩০ মে, দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, কিংবদন্তির এক নায়ক ও দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জন্ম, মৃত্যুঃ ০১-০৬-১৯৬৯ তারিখ। ১৯১১ সালের ৬ জুন, লোহাগড়া (নড়াইল) ইতনা গ্রামের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক ডা. নীহার রঞ্জন রায়ের/গুপ্তের জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৮-১৯৮১ তারিখ। ১৬-বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘রাজকুমারীম্ব’ প্রকাশিত হয়।
১৯১১ সালের ২০ জুন, বাখেরগঞ্জ জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে নানাবাড়িতে বেগম সুফিয়া কামালের জন্ম, মৃত্যুঃ ২০-১১-১৯৯৯ তারিখ। তাঁর বাবারবাড়ি ব্রহ্মণবাড়িয়া জেলার সেন্দুর-সিলাউর গ্রামে। ১৯১১ সালের ৯ জুলাই, ফ্লোরিডার জ্যাকশনভ্যালিতে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের সর্বশেষ সহযোগীদের অন্যতম এবং মার্কিন পদার্থবিদ জন হুইলারের জন্ম, মৃত্যু-১৩-০৪-২০০৮ তারিখ। ‘বø্যাক হোল’ শব্দের প্রবর্তকের মৃত্যু। ১৯১১ সালের ৩১ জুলাই, বরিশালে উপমহাদেশের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ পন্ডিত পান্নালাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২০-০৪-১৯৬০ তারিখ দিলিতে। ১৯১১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় বারডেম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের জন্ম, মৃত্যু-০৬-০৯-১৯৮৯ তারিখ। ১৯১১ সালে অবিভক্ত বাংলার মুসলমান চিত্রশিল্পীদের পথিকৃৎ প্রথম মুসলমান কার্টুনিস্ট এবং শিশু সাহিত্যিক কাজী আবুল কাসেমের জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৭-২০০৪ তারিখ। ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর, মিশরের রাজধানী কায়রোর জামালিয়া কোয়ার্টারের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী আরব ঔপন্যাসিক নাগিব মাহফুজের জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৮-২০০৬ তারিখ। তিনি ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নাগিব মাহফুজ সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান ছিলেন। ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর, ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজনানগাঁয়ে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম নারী ও মানবতাবাদী চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজীর জন্ম, মৃত্যুঃ ০৭-১১-২০০৭ তারিখ। তাঁর পৈতৃক নিবাস মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার গোপালপুর গ্রামে। ১৯১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর, হবিগঞ্জ জেলার মিরাশী গ্রামের এক জমিদার পরিবারে উপমহাদেশের গণসংগীতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম, মৃত্যু-২২-১১-১৯৮৭ তারিখ কলকাতায়। ১৯৮১ সালে যখন ঢাকায় আসেন, তখন দেখেছি হবিগঞ্জের স্মৃতিঘেরা জন্মভূমিকে দেখার জন্য তাঁর ছটফটানি।
১৯১৩ সালের ৪ ফেব্রæয়ারি, আফ্রো-আমেরিকান আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রজন্মের প্রতীক মানবাধিকার নেত্রী রোজা পার্কসের জন্ম, পরলোগমণ ২৪-১০-২০০৫ তারিখ। সবার অধিকার সমান-রোজা পার্কস। আমি গ্রেপ্তার হই ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর। বাসের সামনের দিকে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত বসার স্থান ছেড়ে না দেওয়ার জন্য। ১৯৫৫ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন এমন ছিল কৃঞ্চাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গের জন্য বাসে আলাদা বসার ছিট ছিল। ১৯১৩ সালের ১৯ জুলাই, নড়াইলের আফরা গ্রামে এক জোতদার পরিবারে তেভাগার সংগ্রামী কমরেড অমল সেনের জন্ম, মৃত্যু-১৭-০১-২০০৩ তারিখ। তিনি ১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকমা রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরোর জন্ম, মৃত্যু-০৫-০১-২০০৮ তারিখ। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে এক ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তাঁকে রাজগুরু পদে বরণ করেন। ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার গোকর্ণঘাট গ্রামে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ কালজয়ী ঔপন্যাসের লেখক (এক দরিদ্র জেলে পরিবারে) অদ্বৈত মল্ল বর্মণের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৬-০৪-১৯৫১ তারিখ। ১৯১৪ সালের ৩ এপ্রিল, ভারতের অমৃতসরে ফিল্ড মার্শাল স্যাম হরমুসজি ফ্রামজি জামশেদজি মানেকশ’র জন্ম। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় সামরিক একাডেমির (আইএমএ) প্রথম ব্যাচ থেকে তিনি কমিশন লাভ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ৭ জুন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান হন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর প্রধান ছিলেন। ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাঁকে সম্মানসূচক ফিল্ড মার্শাল উপাধি দেওয়া হয়। স্যাম বাহাদুর নামে পরিচিত মানেকশ চার দশক পর ১৯৭৩ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের অষ্টম সেনাপ্রধান হিসেবে অবসর নেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর মৃত্যু-০১-০৭-২০০৮ তারিখ। ১৯১৪ সালের ১৫ এপ্রিল, কুমিল্লা শহরের পৈত্রিক বাড়িতে ভাষাসৈনিক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি (চিরকুমার) অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের জন্ম, কুমিল্লায় মৃত্যু-২২-১১-১৯৬৯ তারিখ। ১৯১৪ সালের ১৫ মে, এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগের জন্ম, মৃত্যু-মৃত্যু-০৫-০৫-১৯৮৬ তারিখ।
১৯১৪ সালের ৮ জুলাই, কলকাতার হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) একটি বাড়িতে রাজনীতিক ও সাবেক মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্ম, মৃত্যু-১৭-০১-২০১০ তারিখ কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানীয় সময় ১১টা ৪৭ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৩০-এর দশকে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯১৪ সালে কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া মিয়াবাড়িতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের জন্ম, মৃত্যু-২৮-১১-১৯৯৯ তারিখ। ১৯১৪ সালের ১৫ জুলাই, ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরিলীর সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্জাকর্মী, পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলের উদ্ভাবক এবং বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের জন্ম, আমেরিকাতে মৃত্যু-০৯-১০-১৯৯৯ তারিখ। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশভারতের সর্বোচ্চ চাকরি আইসিএস-এ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৩৭-৪৪ সাল পর্যন্ত আই.সি.এস. অফিসার হিসেবে কুমিল্লা, পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, পটুয়াখালী, নওগাঁ ও নেত্রকোনাসহ বিভিন্ন স্থানে এসডিও এবং অন্যান্য উচ্চপদে কাজ করেন। ১৯৪৭-৫০ সাল পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে ড. জাকির হোসেন প্রতিষ্ঠিত জামিয়া মিলিয়াতে মাত্র ১০০ রুপী বেতনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালের এক ক্রান্তিলগ্নে ড. আখতার হামিদ খান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালের ২৭ মে কুমিল্লা একাডেমী (বর্তমানের বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বা বার্ড) নামে কোটবাড়িতে জন্মলাভ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে তাঁকে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তাঁকে আর বাংলাদেশে আসতে দেয়া হয়নি। ১৯৭৮-৭৯ সালে মাত্র সাত মাসের জন্য তিনি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া গ্রামে পশ্চিমবাংলার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের জন্ম, মৃত্যু-০৬-১১-২০১০ তারিখ স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টা ৫০ মিনিটে তিনি দক্ষিণ কলকাতার বেলতলা পার্কের নিজ বাসভবনে। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী ছিল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। ঢাকা শহরের নবদ্বীপ বসাক রোডেও ছিল তাঁদের বাড়ি। তাঁর বাবা সুধীর কুমার রায় ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মায়া রায়ও ব্যারিস্টার ছিলেন। সিদ্ধার্থ শংকর রায় নিঃসন্তান ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁর নানা। ১৯১৪ সালের ১৫ অক্টোবর, আফগানিস্তানের কাবুলে শেষ আফগান বাদশাহ জহীর শাহের জন্ম, ১৯৩৩ সালে তাঁর পিতা (নাদির শাহ) নিহত হওয়ার পর ১৯ বছর বয়সে জহীর শাহ সিংহাসন লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত ৪০ বছর দেশ শাসন করেন এবং শেষ আফগান বাদশাহ জহীর শাহের মৃত্যু-২৩-০৭-২০০৭ তারিখ। ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর, কিশোরগঞ্জ জেলার কেন্দুয়ায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৮-০৫-১৯৭৬ তারিখ। ১৯১৪ সালে রমেন মিত্র বাংলাদেশের নবাবগঞ্জের (বর্তমান চাপাইনবাবগঞ্জ) রামচন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর দু’জনে শুরু করেন তেভাগা আন্দোলন। পূর্ববঙ্গে কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলার অগ্রসেনানী এবং তেভাগা আন্দোলনের নেতা রমেন মিত্র(৯১) বছর বয়সে ২৮-০৬-২০০৫ তারিখ মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর, রাজশাহীর নাচোলের ‘রানি মা’ ও তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের জন্ম, মৃত্যু-১৩-১০-২০০২ সালে। অধ্যাপনা করেছেন ১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত। চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হয়েছেন। ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ইলা মিত্র ছিলেন ক্রীড়াবিদ হিসেবেও তুখোড়। ঢাকায় পুত্র রণেন মিত্র। রণেন মিত্রের জন্ম-১৯৪৮ সালে।
১৯১৫ সালের ২২ আগষ্ট, কলকাতায় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্ম, নিবেদিতপ্রাণ নাট্যব্যক্তিত্বের মৃত্যু-১৮-০৫-১৯৯৭ তারিখ কলকাতায়। ১৯১৫ সালে পাকিস্তানের পেশোয়ারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের জন্ম, মৃত্যু-১৪-০৮-১৯৮০ তারিখ। ১৯১৫ সালে ভারতীয় বাংলা সিনেমার বিখ্যাত নায়িকা ও গায়িকা কানন বালা দেবীর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৭-০৭-১৯৯২ তারিখ। ১৯১৫ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণকারী পূর্ব-পাকিস্তানের কমান্ডার লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজী, ইন্তেকাল-০২-০২-২০০৪ তারিখ ৮৯ বছর বয়সে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে নিয়াজী ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। ১৯১৫ সালে বগুড়াতে প্রখ্যাত সাংবাদিক দৈনিক ইত্তেফাকের আসফ-উদ-দৌলা রেজার জন্ম, ঢাকায় মৃত্যু-১৪-০২-১৯৮৩ তারিখ। ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার নাগাইশ গ্রামে টাইগার গনি নামে পরিচিতি মেজর গনির জন্ম, এবং ১৯৫৭ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানীর ফ্র্যাংকপোর্টে আকস্মিকভাবে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ১৯৪১ সালে বৃটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাইওনিয়ার কোরে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রæয়ারি, তারই অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট। পাক-সরকারের বৈরিতায় ১৯৫৩ সালে তিনি সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত হন প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য। ১৯৮১ সালে মেজর গনিকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে সম্মানিত করা হয়। ১৯১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি, টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার নাগবাড়ির এক জমিদার পরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশের (১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি) রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ০২-০৮-১৯৮৭ তারিখ।
১৯১৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, বর্তমান পাকিস্তানের ঝিলাম জেলায় কালাগুর্জন গ্রামে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা জন্মগ্রহণ করেন এবং ০৩-০৫-২০০৫ তারিখ নয়াদিল্লীর একটি হাসপাতালে সকালে পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইষ্টার্ন কমান্ডের কমান্ডর ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কমান্ডার লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ঢাকায় লে. জেনারেল অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। অরোরা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। ১৯১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার উজানধল গ্রামে বাউলসম্রাট ও কবি শাহ আবদুল করিমের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৯-২০০৯ তারিখ। ১৯১৬ সালের ২১ মার্চ, সানাইয়ের কিংবদন্তী ওস্তাদ ও সুর স্রষ্টা বিসমিল্লাহ খাঁ বিহারের ডুমরাও-এ পেশাদার একটি সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুবরণ করেন-২১-০৮-২০০৬ তারিখ। ১৯৫০ সালে ভারতের প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসে নয়াদিল্লীর ঐতিহাসিক সপ্তদশ শতকের লালকিল্লা থেকে শানাইয়ের ঝঙ্কার তুলে বিখ্যাত হয়ে যান। এ সঙ্গীতজ্ঞ ১৯৯১ সালে সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘ভারতরতœ’ খেতাবে ভূষিত হন। ১৯১৬ সালে বিশ্বখ্যাত ডিএনএ বিজ্ঞানী প্রফেসর উইলকিনসের জন্ম, মৃত্যু-০৮-১০-২০০৪ তারিখ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮-বছর। উইলকিনস আমৃত্যু লন্ডনের কিংস কলেজে অধ্যাপনা করছেন। ১৯১৬ সালে পাকিস্তানের আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা খান আব্দুল ওয়ালী খানের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৫-০১-২০০৬ তারিখ। ১৯১৬ সালে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে বিশ্বখ্যাত শিকারী আবদুল হামিদ ওরফে পচাব্দী গাজীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১২-১০-১৯৯৭ তারিখ। এ শিকারী সর্বোচ্চ ৫৭টি ভয়ঙ্কর মানুষখেকো রয়েল বেঙ্গল বাঘ শিকার করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিকারীদের মাঝে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের (এ দেশের প্রথম সিনেমা মুখ ও মুখোশ-১৯৫৬ সালের ৩ আগষ্ট মুক্তি পায়) পথিকৃৎ আলহাজ্ব আবদুল জব্বার খান বিক্রোমপুরে জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-১২-১৯৯৩ তারিখ। ১৯১৭ সালের ২৯ মে, যুক্তরাষ্টের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির জন্ম, আততায়ীর হাতে মৃত্যু-২২-১১-১৯৬৩ তারিখ। ১৯১৭ সালের ২৭ অক্টোবর, দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী ইস্টার্ন কেপ প্রদেশের বিজানা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ক্যান্টেলো গ্রামে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের এক উজ্জল নক্ষত্র অলিভার টাম্বোর জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৪-১৯৯৩ তারিখ স্ট্রোকে। ১৯১৭ সালের ১৭ নভেম্বর, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম, মৃত্যুঃ ৩১-১০-১৯৮৪ তারিখ নয়াদিল্লীতে দেহরক্ষীর গুলিতে। ১৯১৮ সালের ১৯ জুন, মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল গ্রামে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবি ফররুক আহমদের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৮-১০-১৯৭৪ তারিখ।
১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই, দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবতাবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম, মারা গেছেন ০৫-১২-২০১৩ তারিখ। ১৯৯০ সালের ১১ ফ্রেব্রæয়ারি তাঁর কারামুক্তির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। জীবনের ২৭ বছর জেলে কেটেছে নেলসন মেন্ডেলার। ১৯১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, বঙ্গবীর ও জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০২-১৯৮৪ তারিখ। ১৯১৮ সালের ১ অক্টোবর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার ভেলানগর গ্রামের বড়বাড়িতে মানে তাঁর নানাবাড়িতে (দরিকান্দি গ্রামে তাঁর বাবারবাড়ি) বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, গবেষক, বিশিষ্ট প্রতœতত্তবিদ, ইতিহাসবিদ ও পুঁথি-সাহিত্য বিশারদ, অনুবাদক সাহিত্যিক, মধ্যযুগের ইতিহাস চিন্তাবিদ, ক্রীড়া সংগঠক-বহুমাত্রিক আবুল কালাম মুহাম্মদ যাকারিয়ার জন্ম, ২৪-০২-২০১৬ তারিখ ১১-৫৫ মিনিটে শমরিতা হাসপাতালে বাধ্যর্কজনিত কারণে মারা গেছেন। ১৯১৮ সালের ১৮ অক্টোবর, ঢাকার জিন্দাবাহার লেনে উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেনের জন্ম, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জিন্দাবাহারেই ছিলেন তিনি। জিন্দাবাহার নামে তাঁর বিখ্যাত বইও আছে। ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ সরকারি আর্ট কলেজে পড়তে চলে যান। ২২-১০-২০০৮ তারিখ সোয়া সাতটায় কলকাতার বি. এম. বিড়লা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পর ১৯৭২ সালে পরিতোষ সেন স্বাধীন বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৯১৮ সালে ভিয়েনায় সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্টওয়েল্ডহেইমের জন্ম, মৃত্যু-১৪-০৬-২০০৭ তারিখ। তিনি ১৯৭২-৮২ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর, রাশিয়ার ককেসাসের কিসলোভোদস্ক শহরে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আলেকসান্দর সলঝেনিৎসিনের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৮-২০০৮ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে নোবেল পান। ১৯১৯ সালের ১ মে, কলকাতা শহরে আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দের জন্ম, ২৪-১০-২০১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন ভোর রাত তিনটা ৫০ মিনিটে পরপারে চলে গেলেন প্রবাদপ্রতিম সংগীতশিল্পী মান্না দে। এ ৯০(নব্বই) বছর বয়সেও গান করতে পারছে এবং স¤প্রতি বাংলাদেশে এসেছিলেন। মান্না দে গানই আমার জীবন। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা আমি শুনতে শুনতে নিজেই শিখেছিলাম। ১৯১৯ সালে ২০ জুলাই, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে, পর্বতারোহী ও এভারেষ্ট বিজয়ী স্যার এডমন্ড হিলারির জন্ম, মৃত্যু-১১-০১-২০০৮ তারিখ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকল্যান্ডের একটি হাসপাতালে। তাঁর নামে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ চূড়া এডমুন্ড হিলারির নামে করার প্রস্তাব। ১৯১৯ সালের ১১ অক্টোবর, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারের জন্ম, শহীদঃ ২১-০২-১৯৫২ তারিখ। ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর, লক্ষেèৗ শহরের এক রক্ষণশীল শিয়া মুসলিম পরিবারে নওশাদ আলীর জন্ম, উপমহাদেশের সংগীতের কিংবদন্তি নওশাদ আলীর মৃত্যুঃ ০৫-০৫-২০০৬ তারিখ। ১৯২০ সালের ১৯ জানুয়ারি, বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৯-০১-১৯৯২ তারিখ। ১৯২০ সালের ১৪ ফেব্রæয়ারি, উপমহাদেশের সঙ্গীতজ্ঞ, বাংলাদেশের প্রথম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত বারীণ মজুমদার পাবনা শহরের রাধানগর অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুঃ ০৩-১০-২০০১ তারিখ।
১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৫-০৮-১৯৭৫ তারিখ। ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল, ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে যাঁরা বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবিশংকর অন্যতম, জগদ্বিখ্যাত সেতারবাদক রবিশংকরের (আসল নাম রবীন্দ্র শঙ্কর চৌধুরী) জন্ম, মৃত্যু-১১-১২-২০১২ তারিখ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে আমি আমার বড় ভাই নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের সঙ্গে প্যারিস গিয়েছিলাম। ১৯২০ সালের ১৬ জুন, ফরিদপুর জেলায় বাংলা গানের ভারতীয় বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যুঃ ২৬-০৯-১৯৮৯ তারিখ। ১৯২০ সালের ২৮ জুন, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার ছেদন্দি গ্রামে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের জন্ম, মৃত্যুঃ ১১-০৩-১৯৯১ তারিখ। ১৯২০ সালের ২৬ আগষ্ট, মুন্সীগঞ্জ শহরে এ যুগের সেরা কৌতুকশিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, কলকাতা শহরে মৃত্যু-০৪-০৩-১৯৮৩ তারিখ। ১৯২০ সালে নরসিংদীর বালিয়া গ্রামে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সোমেন চন্দের জন্ম, ঢাকার রাজপথে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও পৈশাচিকভাবে খুন করা হয়-০৮-০৩-১৯৪২ তারিখ। ১৯২০ সালে ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তোর জন্ম, মৃত্যু-২৭-০১-২০০৮ তারিখ। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৬৫ সাল থেকে ক্ষমতা দখল করে এবং ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তো ও তাঁর সেনাবাহিনী ৩২ বছর যাবত একটি লুটপাটের রাজত্ব চালিয়েছে। ১৯২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর, যশোর জেলার সদর থানার খড়কিতে কমিউনিষ্ট নেতা আবদুল হকের জন্ম, মৃত্যু-২২-১২-১৯৯৫ তারিখ। ১৯২১ সালের ২ মে, বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিত রায় (মানিক) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নির্মাণ করেছিলেন অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র ‘পথের পাঁচালি’। ১৯৫৫ সালে নিউইয়র্কে ‘পথের পাঁচালি’ প্রথম প্রদর্শিত হয়। এর কয়েক মাস পর এটি কলকাতায় মুক্তি পায়। ১৯৫৬ সালে সিনেমাটি কান চলচ্চিত্র ঊৎসবে বেস্ট হিউমেন ডকুমেন্টারীর পুরস্কার পায়। এটা বাংলার সমাজ ও গ্রামীণ জীবনকে খুবই হৃদয়গ্রাহীভাবে ফুটিয়ে তোলেন। ১৯২১ সালের ২ ডিসেম্বর, খ্যাতিমান শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানের জন্ম, মৃত্যুঃ ০২-০২-১৯৮৮ তারিখ। ১৯২২ সালের ২ জানুয়ারি, নোয়াখালী জেলায় রাজনীতিবিদ কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহার জন্ম, মৃত্যু-২৯-১১-১৯৮৭ তারিখ। ১৯২২ সালের ১৭ জানুয়ারি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে কিংবদন্তি সরোদশিল্পী (আকবর আলী আকবর খাঁ) ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ’র জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৬-২০০৯ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে নিজের প্রতিষ্ঠিত সংগীত কেন্দ্রে মারা যান। ১৯২২ সালের ১৪ এপ্রিল, কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার বর্ধিঞ্চু গ্রাম এলাহাবাদে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের জন্ম। ১৯৬৭ সালে তিনি ন্যাপ সভাপতি হন। ১৯২২ সালের ৭ নভেম্বর, ঢাকা শহরের লক্ষীবাজারস্থ বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার শাহ সাহেব বাড়ী মাতুলালয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২৩-১০-২০১৪ তারিখ পৌনে ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার প্রতীক গোলাম আযম। ১৯২২ সালে বিখ্যাত অভিনেতা দীলিপ কুমারের জন্ম। (আসল নাম ইউসুফ খাঁন)। দিলীপ কুমার ১৯৪৪ সালে জোয়ার ভাটা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এ সুপুরুষ নায়কের যাত্রা শুরু। ১৯২৩ সালে কলকাতায় ইহুদি পরিবারে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাকব-ফারজ-রাফায়েল জ্যাকবের (জে.এফ.আর.জ্যাকব) জন্ম, ১৩-০১-২০১৬ তারিখ বুধবার সকালে দিল্লির একটি সামরিক হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন। জ্যাকবের পূর্ব পুরুষেরা বাগদাদ থেকে এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লড়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে, মিয়ানমারের পরে সুমাত্রায়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে ভারতীয় বাহিনীর ঢাকা অভিযানের নেতৃত্বে দেন, তাঁর পরিকল্পনাতেই পাকিস্তান সেনবাহিনীকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটি ছিল কার্যত জ্যাকবের নিজস্ব উদ্ভাবন। জেনারেল জ্যাকব তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করতে নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল থেকেও উদ্ধৃতি দেন। নিয়াজি সেখানে বলেন, জ্যাকবই তাঁকে বø্যাকমেইল করে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বিষয়ে পাকিস্তানিরা তাঁদের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের গবেষণায় বিষ্ময়করভাবে ভারতীয় বিজয়ের জন্য কৃতিত্ব নির্দিষ্টভাবে ‘‘মেজর জেনারেল জ্যাকব’’কেই দিয়েছে। ৩১ জুলাই ১৯৭৮ সালে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। ইহুদিদের প্রতি পাকিস্তানের কোনো প্রেম নেই। পাকিস্তানিরা জানত, আমি একজন ইহুদি। ১৯২৩ সালের ১৪ মে, বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা শহরে নন্দিত চলচ্চিত্রনির্মাতা মৃণাল সেনের জন্ম। ০২-০২-২০০৫ তারিখ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য ভারতের ৫১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট এ. পি. জে. আবদুল কালাম মৃণাল সেনের কাছে দাদা সাহেব ফালকে সম্মাননা হস্তান্তর করেন। ১৯২৩ সালের ২৩ মে, বরিশাল জেলার সিদ্ধকাঠি গ্রামে আজকের দুনিয়ায় ইতিহাস সুষ্টিকারী ইতিহাসবিদ, ইতিহাসের দার্শনিক রণজিৎ গুহের জন্ম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কারণে তিনি ভারতে চলে যায়। রণজিৎ গুহকে মার্কসবাদী ধারা ইতিহাসবিদ ধরা হয়। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে ফুসফুসে ক্যান্সার নিয়ে হয়তোবা মৃত্যুর দিকেই যাচ্ছেন বাংলার এ কৃতী সন্তান। মরার আগে আরও পাঁচ বছর বাঁচতে চান, যাতে বাংলায় আরও লিখতে পারেন, যাতে একবারের জন্য হলেও তাঁর জন্মভূমি বরিশালের নদীতে কয়েক মাস ঘুরে বেড়াতে পারেন। রণজিৎ গুহকে প্রাচ্যের তত্ত¡বিদ বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে, ভারতবর্ষ তথা বংলার কৃষককে নূতন আলোয় দেখাতে পেরেছেন। তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় ২০০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর, ৪৫তম কনভোকেশনে এ ক্ষণজন্মা পন্ডিতকে ‘ডক্টর অব লিটারেচার’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে।
১৯২৩ সালের ১০ আগষ্ট, শিল্পী এস. এম. সুলতান জন্মগ্রহণ করেন নড়াইল জেলার মাছিম দিয়া গ্রামে, বরেণ্য শিল্পী মৃত্যুবরণ করেনঃ ১০-১০-১৯৯৪ তারিখ। ১৯২৪ সালের ৮ মে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার শিউড়ী মহকুমার খয়রাদিহি গ্রামে শিল্পী কলিম শরাফীর জন্ম, মৃত্যু-০২-১১-২০১০ তারিখ রাজধানীর বারিধারায় নিজ বাসভবনে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে । ১৯৫০ সালে ঢাকায় চলে এসেছিলেন কলিম শরাফী। ১৯২৪ সালে পাবনা জেলায় ভাষাসৈনিক ও কমরেড আবদুল মতিনের জন্ম। ১৯২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর, পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরের কাছে কোটলা সুলতান সিংয়ে গায়ক সুরকার মোহাম্মদ রফি জন্মগ্রহণ করেন, মুম্বাইয়ে মৃত্যুঃ ৩১-০৭-১৯৮০ তারিখ। তিনি যখন মারা যান মুম্বাইয়ে সর্বকালের সবচেয়ে বড় শোক মিছিল হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ৯ জানুয়ারি, ঝালকাঠির ৫ নম্বর কীর্তিপাশা ইউনিয়নের রুনসী গ্রামে প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিষ্ট, দৈনিক সংবাদের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য সন্তোষ গুপ্তের জন্ম, ০৬-০৮-২০০৫ তারিখ দিবাগত রাত ২-৩০ মিনিটে বারডেম হাসপাতালে পরলোকগমন। ১৯২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ডে কমপিউটার মাউসের জনক ডগলাস অ্যাঙ্গেলবার্টের জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৭-২০১৩ তারিখ। ১৯২৫ সালের ২৪ মার্চ, যশোরে মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামানের (বীর-উত্তম) জন্ম, মৃত্যু-০৬-০৫-২০১১ তারিখ। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভিতে যোগ দেন। ১৯২৫ সালের ৯ এপ্রিল, কেন্দ্রীয় কচি-কাচার মেলার প্রতিষ্ঠাতা ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের জন্ম, তিনি মারা যান ০৩-১২-১৯৯৯ তারিখ। ১৯২৫ সালের ৯ জুলাই, ভারতের বেঙ্গালুরুতে সফল চলচ্চিত্র নির্মাতা গুরু দত্তের জন্ম, মৃত্যু-১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর, মুম্বাইয়ে। ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সাবেক অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর, কেন্দ্রীয় কারাগারে। ১৯২৫ সালের ২৯ নভেম্বর, ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলার মাতুভূঁইয়া ইউনিয়নের লক্ষণপুর গ্রামে ভাষা শহীদ আবদুস সালামের জন্ম, শহীদঃ ২১-০২-১৯৫২ তারিখ। ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর, এ ঢাকা শহরেই দুটি ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। তাঁদেরই একজন পরবর্তী জীবনে বাংলার শিল্পনিষ্ঠ ও স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক, অন্যজন সাত মিনিটের ছোট বোন। অত্যন্ত কৃতী পরিবারের সবচেয়ে অকৃতী অধম সেই যমজ বোনই আমি-প্রতীতি। স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের কলকাতায় মৃত্যু-০৬-০২-১৯৭৬ তারিখ। ঋত্বিক কিন্তু ঢাকাতেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে মা-বাবাকে নিয়ে দাদারা কলকাতায় চলে যান। ঋত্বিক এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু সবার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। ফলে তাকেও যেতে হলো। ঋত্বিক কুমার ঘটকরা নয় ভাই-বোনের মধ্যে সবার কনিষ্ঠ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবী। প্রতীতি দেবীর স্মৃতিচারণায় ভাই ঋত্বিক ঘটক। প্রতীতি দেবী ঢাকায়ই থাকেন।
১৯২৫ সালে ভারতের শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী ও পারমাণবিক কর্মসূচীর জনক রাজা রামান্নার জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৯-২০০৪ তারিখ। ১৯২৫ সালে ব্রিটেনের ম্যানচেস্টারে বিজ্ঞানী রবার্ট এডওয়ার্ডসের জন্ম। ব্রিটিশ অধ্যাপক রবার্ট এডওয়ার্ডসের হাতেই ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই, জন্ম হয় বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব শিশু লুইস ব্রাউনের। তাঁর এ সফলতায় বিশ্বের লাখ লাখ বন্ধ্যা দম্পতি আইডিএফ প্রযুক্তির মাধ্যমে সন্তান লাভ করছে। ১৯২৫ সালে ভারতের শিলংয়ে স্কটিশ বিজ্ঞানী জন শেফার্ড-ব্যারনের জন্ম, মৃত্যু-১৫-০৫-২০১০ তারিখ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৪ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের ইনভারনেস শহরের একটি হাসপাতালে। তিনি এটিএমের উদ্ভাবক জন শেফার্ড-ব্যারন অটোমেটেড টেলর মেশিন (এটিএম)-এর উদ্ভাবক জন শেফার্ড-ব্যারন মারা গেছেন। ব্যাংকিং খাতে টাকা-পয়সা তোলার ক্ষেত্রে এটিএমের ধারণা প্রথম জন শেফার্ড-ব্যারনের ভাবনাতেই আসে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে লন্ডনে প্রথম এটিএম বসানো হয়। জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানে ‘অন দি বাসেস’ থেকে প্রচারের আলোয় আসা অভিনেতা রেগ ভার্নি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি সেই এটিএম থেকে টাকা তুলেছিলেন। পিটিআই। ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি, বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ঢাকায়। লেখার পাশাপাশি দলিত ও আদিবাসী জনজাতিগুলোর কাছে গিয়ে তাদের নিয়ে কাজ করে তিনি একজন প্রতিবাদী লড়াকু কণ্ঠস্বর হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। ১৯২৬ সালে বগুড়া জেলায় আলোর দিশারী বাংলাদেশের মহিলা ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রদূত ছিলেন রাবেয়া খাতুন তালুকদারের জন্ম, মৃত্যু-২০০৯ সালে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন রাবেয়া খাতুন তালুকদার। ১৯২৬ সালে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর জন্ম, তাঁর ফাঁসি হয়-০৪-০৪-১৯৭৯ তারিখ। ১৯২৬ সালে পূর্ববঙ্গের বলিশাল জেলায় ইতিহাসের পন্ডিত অধ্যাপক তপন রায় চৌধুরীর জন্ম। তবে তাঁর মুখ্য কাজের ক্ষেত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। মোগল আমলের ও ব্রিটিশ উপনিবেশের বাংলা তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট, কলকাতায় যে কুৎসিত দাঙ্গার ঘটনাটা ঘটল, ‘আমি এখনো দাঙ্গার ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছি’।
১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি মহানায়ক অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় (উত্তম কুমারের) জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৭-১৯৮০ তারিখ। ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, ভারতের আসাম রাজ্যে গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকার জন্ম, শনিবার স্থানীয় সময় বিকেল চারটা ৩৭ মিনিটে মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন ধিরুভাই আম্বানি হাসপাতালে এই মানবদরদি শিল্পী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন-০৫-১১-২০১১ তারিখ। ‘যাযাবরের’ চিরপ্রস্থান। তিনি আসামী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় গান করতেন। ১৯২৬ সালের ১৩ আগষ্ট, কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম। তিনি ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি, কিউবায় কমিউনিষ্ট বিল্পবের মাধ্যমে কিউবার ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৬ সালের ১৬ আগষ্ট, বিপ্লবী কিশোর কবি সুকান্ত কলকাতা শহরে তাঁর নানাবাড়ি জন্মগ্রহণ করেন; মৃত্যু-১৩-০৫-১৯৪৭ তারিখ কলকাতা শহরে। ফরিদপুর জেলায় তাঁর বাবারবাড়ি। ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি, নোয়াখালী জেলার সেনবাগে বইয়ের মানুষ চিত্তরঞ্জন সাহার জন্ম, মৃত্যু-২৬-১২-২০০৭ তারিখ। চিত্তরঞ্জন সাহাই পুথিঘর লাইব্রেরীর মালিক এবং প্রথম বাংলা একাডেমীতে একুশে ফেব্রæয়ারিতে বইয়ের দেকান দেন। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে ভাষাসৈনিক শহীদ আবুল বরকতের জন্ম, মৃত্যু-২১-০২-১৯৫২ তারিখ ঢাকায়। ১৯২৭ সালের ১৮ জুলাই, ভারতের রাজস্থানের ঝুনঝুন জেলার লুনা গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সংগীত পরিবারে উপমহাদেশের ধ্রæপদ সংগীত ও গজলের ধ্রæবতারা মেহদি হাসানের জন্ম, পাকিস্তানের করাচিতে মৃত্যু-১৩-০৬-২০১২ তারিখ বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ২২ মিনিটে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পরিবারসহ পাকিস্তানের সহিওয়াল জেলার ছিচা ওয়াতনি এলাকায় থিতু হন তাঁরা। ১৯৫৭ সালে ঠুমরি গায়ক হিসেবে পাকিস্তান বেতারে গাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর থেকে আর্থিক সংকট কাটতে থাকে মেহদি হাসানের। ১৯২৮ সালের ২০ মার্চ, কুচবিহারে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের জন্ম। ১৯২৮ সালের ১৪ জুন, আর্জেন্টিনার রোমারি শহরের স্যান্টাক্লারা এলাকায় লাতিন আমেরিকার বিপ্ললী নেতা ও কিউবা বিপ্লবের অন্যতম নায়ক চে গুয়েভারার জন্ম, ১৯৬৭ সালের ৮ অক্টোবর দুজন সহযোদ্ধাসহ বন্দী হন আহত চে। পরে তাকে ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর, বলিবিয়ার এক সার্জেন্ট মারিয়ো তেরান চে গুয়েভারাকে বলিভিয়ার জঙ্গলে কাছ থেকে গুলী করে হত্যা করেন। ১৯৩৭ সালে স্পেনিশ গণযুদ্ধের সময় চে পড়ছেন প্রাইমারী স্কুলে, থার্ড গ্রেডে। ১৯৪৭ সালে আর্জেন্টিনার কমিউনিষ্ট সংঘের তরুণ কর্মী বারতা গিলদা তিতার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মার্কসবাদী দর্শনের নানামুখী আলোচনায় ঝুঁকে পড়েন তিনি। ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি, ফিদেল-চের নেতৃত্বে বিপ্লব সমপন্ন হয় কিউবায়। ১৯২৮ সালের ১১ ডিসেম্বর, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার রামকান্তপুর গ্রামে চলচ্চিত্রকার, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ও অভিনেতা খান আতাউর রহমান খানের জন্ম, মৃত্যু-০১-১২-১৯৯৭ তারিখ। তিনি চলচ্চিত্র অঙ্গনের এক ব্যতিক্রমী পুরুষ। ১৯২৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের, শিকাগো শহরে মার্টিন কুপারের জন্ম। হাতে বহনযোগ্য মোবাইল ফোনের উদ্ভাবক। ৩ এপ্রিল ১৯৭৩, তিনি মোবাইল ফোনে প্রথম কলটি করেন।
১৭৮১ সালের ৯ জুন, রেলওয়ে ইঞ্জিনের নকশাকার ও স্টিম ইঞ্জিনের রূপকার ইংরেজ উদ্ভাবক জর্জ স্টিফেনসনের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৮-১৮৪৮ তারিখ। ১৭৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী মীর নিসার আলীর (শহীদ তিতুমীর) জন্ম, মৃত্যুঃ ১৪-১২-১৮৩১ তারিখ। ১৭৮২ সালের ২১ এপ্রিল, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির উদ্গাতা ফ্রিডরিখ ফ্রোয়েবেলের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৭৯১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, ইংরেজ রসায়ন ও পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৮৬৭ সালে। (১৮৪৫ সালে বিদ্যুৎ আবিস্কারক)। ১৭৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর, যুক্তরাজ্যের লন্ডনে চার্লস ব্যাবেজের জন্ম, মৃত্যু-১৮-১০-১৮৭১ তারিখ। তিনি ১৮২২ সালে ডিফারেন্স মেশিন নামের বিশ্বের প্রথম কমপিউটার তৈরি করেন। ১৭৯৪ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর সুবিদিত ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবসা বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-০১-০৮-১৮৪৬ তারিখ। ১৭৯৫ সালের ৩১ অক্টোবর, ইংরেজ কবি জন কিটসের জন্ম; মৃত্যু-২৩-০২-১৮২১ তারিখ। ১৭৯৭ সালে অযোধ্যার অন্তর্গত খয়রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মৃত্যু-১৮৬১ সালে আন্দামান দ্বীপে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবে মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসনে পাঠায়। ১৭৯৭ সালে ভারতের দিল্লী শহরে উর্দু ও ফার্সি সাহিত্যের মহাকবি কবি মির্জা আসাদ উল্লাহ খান গালিবের জন্ম, ইন্তেকাল-১৫-০২-১৮৬৯ তারিখ। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়েছে। এ বিদ্রোহের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ১৮০৪ সালের ২৮ জুলাই, জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক ল্যুৎদভিগ ফয়েরবাখের জন্ম, মৃত্যু-১৩-০৯-১৮৭২ তারিখ। ১৮০৯ সালের ৪ জানুয়ারি, অন্ধদের পাঠ পদ্ধতির উদ্ভাবক ফরাসী গবেষক লুই ব্রায়ির জন্ম, মৃত্যু-২৮-০৩-১৮৫২ তারিখ। ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রæয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের ষোলতম প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী নেতা আব্রাহাম লিংকনের জন্ম, মৃত্যু-১৫-০৪-১৮৬৫ তারিখ। ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ইংল্যান্ডের শ্রæসবরিতে বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস রবার্ট ডারউইনের জন্ম, মৃত্যু-১৮-০৪-১৮৮২ তারিখ। তাঁর লেখা ‘অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ’ বহুল আলোচিত গ্রন্থটি ১৮৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৮১৫ সালের ১৭ অক্টোবর, আলিগড়ের প্রখ্যাত মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার অগ্রদূত, নেতা, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদের জন্ম, মৃত্যু-১৮৯৮ সালে। ১৮১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর, যুক্তরাজ্য, লন্ডন, অগাষ্টা আডা বায়রনের (আডা লাভলেস) জন্ম, মৃত্যু-২৭-১১-১৮৫২ তারিখ। পৃথিবীর প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার। চার্লস ব্যাবেজ উদ্ভাবিত কমপিউটারের জন্য প্রথম প্রোগ্রাম লেখেন। ১৮১৭ সালের ১৫ মে, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বাংলা গদ্যের লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যুঃ ০৫-০১-১৯০৫ তারিখ। ১৮১৮ সালের ৫ মে, জার্মানে সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের জন্ম; ইংল্যান্ডে মৃত্যু-১৪-০৩-১৮৮৩ তারিখ। ১৮৪৮ সালের ১৮ ফেব্রæয়ারি, কার্ল-মার্কস কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো ঘোষণা করেন। ১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রæয়ারি, কার্ল-মার্কস ও ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৮১৮ সালে ঢাকার নবাব স্যার নওয়াব খাজা আবদুল গনির জন্ম, মৃত্যু-১৮৭৩ সালে। খাজা আবদুল গনি বংশানুক্রমিক নবাব উপাধি লাভ করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১৮৬৫ সালে। ১৮২০ সালের ১২ মে, ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে ইংরেজ সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জন্ম, ১৩-০৮-১৯১০ তারিখ, এ মানব দরদী মহীয়সী নারীর মৃত্যু। ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম; মৃত্যুঃ ২৯-০৭-১৮৯১ তারিখ। ১৮৪০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র ‘‘বিদ্যাসাগর’’ উপাধি পান। ১৮৮০ সালে বিদ্যাসাগর সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর, জার্মানে এঙ্গেলসের জন্ম, ইংল্যান্ডে মৃত্যু-১৮৯৫ সালে। ১৮২০ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মহারাষ্ট্রে সিপাহী বিপ্লবের আপসহীন নেত্রী ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাই’র জন্ম, মৃত্যু-১৭-০৬-১৮৫৮ তারিখ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাণ। ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর, ফরাসী রসায়নবিদ ও অনুজীব বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৯-১৮৯৫ তারিখ। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি, যশোরের সাগর দাঁড়ির দত্ত পরিবারের একমাত্র পুত্র মহাকবি ও সাহিত্যক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-০৬-১৮৭৩ তারিখ কলকাতার আলীপুর হাসপাতালে।
১৮২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, রাজনৈতিক দাদাভাই নওরোজির জন্ম, মৃত্যু-১৯১৭ সালের ৩০ জুন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম এশীয় সদস্য দাদাভাই নওরোজীর মৃত্যু। ১৮২৬ সালের ২৪ জানুয়ারি, অবিভক্ত ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার গণেন্দ্রমোহন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-০৫-০১-১৮৯০ তারিখ। ১৮২৭ সালের ৫ এপ্রিল, পচনরোধী ওষুধের আবিষ্কারক ইংরেজ চিকিৎসক যোসেফ লিস্টারের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৮২৮ সালের ৮ মে, রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনান্ট সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৯১০ সালের ৩০ অক্টোবর। ১৮২৮ সালের ২৮ আগষ্ট, মানবতাবাদী লেখক ও রাশিয়ার বিপ্লবী সাহিত্যিক লেভ টলষ্টয়ের জন্ম; মৃত্যু-২০-১১-১৯১০ তারিখ। ১৮২৮ সালের ৩১ অক্টোবর, বৃটিশ রসায়নবিদ ও বিদ্যুৎ বাতির উদ্ভাবক জোসেফ সোয়ানের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৮২৮ সালে নবাব আব্দুল লতিফ ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ১৮৪৮ সালে কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী ও আরবী বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন, ১৮৬২ সালে নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে প্রথমবঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৮৪ সালে নবাব আব্দুল লতিফ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন, মৃত্যুঃ ১০-০৭-১৮৯৩ তারিখ। ১৮৩২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার চিতওয়া গ্রামে ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর জন্ম, ঢাকায় মৃত্যু-০৯-০২-১৮৮৫ তারিখ।
১৮৩৩ সালের ২০ জুলাই, কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কুন্ডুপাড়ার এক দরিদ্র পরিবারে গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৎ উনিশ শতকের সংবাদপত্র গ্রামবার্তা প্রকাশিকার সম্পাদক কাঙাল হরিণাথ মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০৪-১৮৯৬ তারিখ। ১৮৬৩ সালে কুমারখালী বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক কাঙাল হরিণাথ মজুমদার মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রকাশ করেন। ১৮৩৩ সালের ২১ অক্টোবর, সুইডেনের রাজধানী স্কটহোমে জন্মগ্রহণ করেন আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল, মৃত্যু-১০-১২-১৮৯৬ তারিখ। তিনি সুইডেনের একজন খ্যাতিমান শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, যিনি বিশ্বের সেরা এই পুরস্কারের প্রবর্তক, যা তাঁর নিজ নামে সন্নিহিত তথা নোবেল প্রাইজ রুপে বিশ্ববিশ্রুত। ১৮৬৭ সালে পেটেন্টকৃত আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেলের বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবিস্কার ‘ডিনামাইট’ জগৎ জুড়ে শিল্প উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর অবদান রেখে আসছে। ১৯০১ সালে প্রথমবার নোবেল প্রাইজ প্রদানের পর থেকে অদ্যাবধি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় তা নোবেল কমিটি কর্তৃক প্রকাশের পূর্বে কেউই নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে এ পুরস্কার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। ১৮৩৪ সালের ১৪ মে, নরসিংদীর সদর উপজেলার মেহেরপাড়ায় কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক গিরিশ চন্দ্র সেনের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৫-০৮-১৯১০ তারিখ। তিনি ১৮৮০ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত টানা সাত বছর কাজ করে কোরআন শরিফের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার হোমনাবাদ পরগনার পশ্চিমগাঁও-এ নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৯-১৯০৩ তারিখ। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কুমিল্লা জেলার প্রথম নবাব উপাধি পান। ১৮৩৮ সালের ২৬ ফেব্রæয়ারি, মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘরের পশ্চিম ঘোষপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন প্রতিথযশা এ আইনবিদ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, মৃত্যু-জানা নেই। ১৯০৬ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন, বাংলা উপন্যাসিক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম; মৃত্যু-০৮-০৪-১৮৯৪ তারিখ। ১৮৪০ সালের ১১ মার্চ, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবি, দার্শনিক, গনিতজ্ঞ, বাংলা শর্টহ্যান্ড ও স্বরলিপির উদ্ভাবক, চিত্রশিল্পী ও স্বদেশ প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যু-১৯-০১-১৯২৬ তারিখ।
১৮৪০ সালে হুগলি জেলা নিবাসি দেলোয়ার হোসেন আহমেদ বা মির্যা দেলোয়ার হোসেনের জন্ম (মুসলমানের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৩ সালে) মৃত্যু-১৯১৬ সালে। ১৮৪০ সালে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার অমৃতবাজার গ্রামে সংবাদপত্রের জগতের কিংবদন্তি শিশির কুমার ঘোষের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১০-০১-১৯১১ তারিখ। ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রæয়ারি, প্রকাশ করেন ‘সাপ্তাহিক অমৃতবাজার’ পত্রিকা । ১৮৭১ সালে সপরিবারে কলকাতায় গিয়ে সেখান থেকেই ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ বের করতে থাকেন। ১৮৯১ সালে পত্রিকা দৈনিক হিসেবে প্রকাশ হতে থাকে। ১৮৪৪ সালের ২৮ ফেব্রæয়ারি, নাট্যকার, পরিচালক ও বাংলা নাটকের লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম, মৃত্যু-১০-০১-১৯১১ তারিখ। ১৮৪৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার পেয়ারাকান্দি গ্রামের কাজী বাড়িতে নবাব সিরাজুল ইসলামের জন্ম, মৃৃত্যু-১৯২৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে নবাব সিরাজুল ইসলাম ১৮৬৮ সালে বি. এ. পাশ করেন (কুমিল্লা জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট) এবং কিছুকাল তিনি পোগোজ হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত থাকেন। পরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী চলে যাবার পর কলকাতা আইন কলেজ থেকে আইন পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজী শিক্ষিত প্রথম মুসলমান এডভোকেট ছিলেন। সিরাজুল ইসলাম ১৯০৬ সালে ‘নবাব’ উপাধি পান। ১৮৪৬ সালে ঢাকার নবাব স্যার খাজা আহসান-উল্লাহর জন্ম, মৃত্যু-১৬-১২-১৯০১ তারিখ। ১৮৪৭ সালের ১১ ফেব্রæয়ারি, কানাডার মিলানে মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের জন্ম এবং মৃত্যু-১৮-১০-১৯৩১ তারিখ। ১৮৪৭ সালের ৩ মার্চ, এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ডে, আলেকজান্ডার গ্রাহামবেলের জন্ম, মৃত্যু-০২-০৮-১৯২২ তারিখ। ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর, কুষ্টিয়া জেলার গৌরী নদীর তীরে লাহিনীপাড়া গ্রামে ‘বিষাদসিন্ধু’র রচয়িতা ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেনের জন্ম, মৃত্যুঃ ১০-১২-১৯১২ তারিখ।
১৮৪৯ সালের ৬ এপ্রিল, উড়িষ্যার কটকে বিচারপতি স্যার সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম; মৃত্যু-০৩-০৮-১৯২৮ তারিখ লন্ডনে। ১৮৭৩ সালে সৈয়দ আমীর আলী ব্যারিস্টার হন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রিভি কাউনসিল হন সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৯০ সালের ২ জানুয়ারি, সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের মুসলমানের মধ্যে প্রথম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৮ সালে এম. এ. (ইতিহাস)-এ পাস করেন হুগলি কলেজ থেকে, তিনি বাঙালি মুসলমানের মধ্যে প্রথম এম. এ. পাস এবং প্রথম ব্যারিস্টারও তিনি। ১৮৪৯ সালে বিক্রমপুরের গাড়ডুগা গ্রামে প্রখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক রাজকুমার সেনের জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। পদার্থ বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনাসহ জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৮৫৪ সালের ২১ ডিসেম্বর, সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী গ্রামের বিখ্যাত জমিদার, বাংলার মরমী কবি ও সাধক হাছন রাজার জন্ম, মৃত্যুঃ ০৭-১২-১৯২২ তারিখ। মরমী কবি হাছন রাজা হলো দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নানা। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই, ইংল্যান্ডের ভুবলিন শহরে নোবেল বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ’র জন্ম, মৃত্যু-০২-১১-১৯৫০ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯২৫ সালে নোবেল পান। ১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারি, বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার অন্তর্গত বাটোজোর একটি ছোট গ্রামের সচ্ছল কায়স্থ ভূম্যধিকারী পরিবারে জনহিতৈষী ও জাতীয়তাবাদী নেতা এডভোকেট অশিনীকুমার দত্তের জন্ম, মৃত্যু-০৭-১১-১৯২৩ তারিখ। ১৮৫৬ সালে পেনসিলভানিয়ার ক্রেসনে উত্তর মেরুজয়ী মার্কিন অভিযাত্রী রবার্ট পিয়েরির জন্ম, ১৯২০ সালে মারা যান। ১৯১১ সালে রিয়ার এডমিরাল হিসেবে অবসর নেন পিয়েরি। ১৯০৯ সালের ৬ এপ্রিল, বহু দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী ম্যাথু হ্যানসন ও চারজন দুঃসাহসী এস্কিমো নিয়ে প্রথম পা রাখলেন আর্কটিকের উত্তর মেরুতে রবার্ট পিয়েরি। উত্তর মেরুজয়ের ১০০ বছর পুরো হবে ০৬-০৪-২০০৯ তারিখ। ১৮৫৭ সালের ৮ নভেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের সাদক ফকির আফতাব উদ্দিন খাঁর জন্ম, মৃত্যু-২৫-০১-১৯৩৩ তারিখ। ১৮৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর, যুক্তরাষ্টের ২৬তম প্রেসিডেন্ট থিডোর রুজবেল্টের জন্ম, ১৯১৯ সালের ৬ জানুয়ারি, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের মৃত্যু।
১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর, বিজ্ঞানী স্যার জগদীস চন্দ্র বসু ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন (মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের রাড়িখাঁল গ্রামে বাবার বাড়ি), ২৩-১১-১৯৩৭ তারিখ গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন ফরিদপুরের একটি স্কুলে। তারপর ১১ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে সেন্ট জিভিয়ার্স স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১৮৭৫ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৭৯ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৮৯৬ সালে লন্ডন ভার্সিটি থেকে ‘ডক্টর অব সাইন্স’ উপাধি পান। ১৮৫৮ সালে বাঙ্গালী ঐতিহ্য ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ইরানী বংশোদ্ভূত বাংলাকাব্যের মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ, মৃত্যুবরণঃ ২১-০৭-১৯৫১ তারিখ। ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বিটঘর গ্রামে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-১৯৪৩ সালে। মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আর্থানুকূলে ২৫টির অধিক উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব পরিচালিত হয়। উনার বাবার নামে কুমিল্লা ইশ্বর পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৮ সালে উপমহাদেশের নন্দিত গণিতসম্রাট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার কামারচন্দ্র থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২৬-১১-১৯২৩ তারিখ। তিনি ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স, ১৮৭৮ সালে এফ. এ., ১৮৮০ সালে বি.এ. পাস করেন এবং ১৮৮৬ সালে গণিতে এম. এ. পাস করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। বি. এ. পাস করার পর ১৮৮১ সালে ছয় বছর মিশন কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৭ থেকে একাদিক্রমে ২৮ বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯১৫ সালে অবসর নেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৮৫৯ সালের ১১ জানুয়ারি, ভারতের ভাইসরয় লর্ড জর্জ কার্জন জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২০-০৩-১৯২৫ তারিখ। ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক, শার্লক হোমসের রচয়িতা স্যার আর্থার বোনান ডয়েলের জন্ম, মৃত্যু-১৯৩০ সালে। ১৮৫৯ সালের ২৩ অক্টোবর, যশোরের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের জন্ম, মৃত্যু-২৪-১০-১৯৩২ তারিখ। ১৮৮১ সালে এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দীর্ঘকাল ছিলেন যশোর পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান, যশোর জেলা বোর্ডের প্রথম মনোনীত চেয়ারম্যানও।
১৮৬১ সালের ৭ মে, (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বাংলা) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যু-০৭-০৮-১৯৪১ তারিখ। ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মৃণানিলী দেবীর বিয়ে হয়। তিনি ১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর, নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙ্গালীদের মন জয় করেছিলেন। ১৮৬১ সালের ১৮ জুলাই, প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর জন্ম, (১৮৮৬ সালে প্রথম ভারতীয় ডিগ্রিপ্রাপ্ত নারী চিকিৎসক ছিলেন) মৃত্যুঃ ০৩-১০-১৯২৩ তারিখ। ১৮৬১ সালে ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগনার নরসিংদী গ্রামে কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য্যরে জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৫-১৯৪১ তারিখ। ১৮৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, ভারতের কাশ্মীরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনীতিবিদ পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর জন্ম, মৃত্যুঃ ০৬-০২-১৯৩১ তারিখ। ১৮৬২ সালের ১০ নভেম্বর, ইংল্যান্ডের উম্বারল্যান্ডের হেপসকট শহরে রমনা-নিসর্গের স্থপতি রবার্ট লুইস প্রাউডলকের জন্ম, মৃত্যু-১৯৩৬ সালের পরে হবে, জানা নেই। প্রায় ১০০ বছর আগে তিনি রাজধানী শহর ঢাকাকে উদ্যানের নগর হিসেবে গড়ে তুলতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, সেই অসামান্য অবদানের জন্য তিনি আমাদের কাছে নমস্য হয়ে থাকবেন। ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার, নবীনগর উপজেলার, শিবপুর গ্রামে সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ’র জন্ম, মৃত্যু-মাইসুর, কলকাতাঃ ০৬-০৯-১৯৭২ তারিখ। ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারি, আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার ‘জনক’ তিনি হলেন ফ্রান্সের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ব্যারন পিয়ের দ্য কুব্যাঁর্ত্যাের জন্ম, মৃত্যু-০২-০৯-১৯৩৭ তারিখ। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি, হিন্দুধর্ম ও সমাজ সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, ০২-০৭-১৯০২ তারিখ ৯টা ৫০মিনিটের সময় মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৬৩ সালের ১০ মে, কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার মাছূয়া গ্রামের রায় পরিবারে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ২০-১২-১৯১৫ তারিখ। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ছিলেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু। উপেন্দ্র কিশোর রায় ১৮৯৪ সালের দিকে কলকাতায় বইছাপা কারখানা দেন এবং পরে নিজেই পাবলিসারস হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৬৩ সালে ফেনী জেলার শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক খান বাহাদুর আবদুল আজীজের জন্ম, মৃত্যু-১৯২৬ সালে। তাঁর পিতা আমজাদ আলী ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী। আবদুল আজীজ ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বি.এ. পাস করে। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। পরিচয় হলোঃ কবি হাবিবুল্ল¬াহ বাহার ও কবি শামসুন নাহারের নানা। ১৮৬৩ সালে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিখ্যাত চিকিৎসক এবং শিক্ষাবিদ ডা. হাকিম আজমল খানের জন্ম, মৃত্যু-১৯২৭ সালে। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং অল ইন্ডিয়া খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।
১৮৬৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল, নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৭-০৪-১৯২৯ তারিখ। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম মন্ত্রী, বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন, প্রধান বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় কলকাতা মলঙ্গা লেনের এক বাসাবাড়িতে এবং ২৫-০৫-১৯২৪ সালে পাটনায় হঠাৎ-ই পরলোগমন করেন। ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর ঝালকাঠি জেলার বাসন্ডা গ্রামে কবি কামিনী রায়ের জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৯-১৯৩৩ তারিখ। তিনি ১৫ বছর বয়সেই লিখেছেন প্রথম কবিতাগ্রন্থ “আলো ও ছায়া”। ১৮৬৬ সালে নাছিরনগর উপজেলার গোকর্ণ গ্রামে নবাব স্যার সৈয়দ শামসূল হুদার জন্ম, (সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন) মৃত্যু-১৯২২ সালে। ১৮৬৬ সালে চীনা জাতীয়তাবাদী নেতা সানইয়াৎ সেনের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৩-১৯২৫ তারিখ। ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর, ওয়রশতে পোলিশ বংশোদ্ভূত ফরাসি রসায়নবিদ ও বিশ্বের প্রথম তেজস্ক্রিয় মৌল পোলোনিয়ামের আবিস্কারক মেরি কুরীর জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৭-১৯৩৪ তারিখ। ১৮৯৮ সালে প্যারিসে খনিজ পিচবেøন্ড থেকে-পোলোনিয়াম নিস্কাশন করেন। পরবর্তী সময় একই বছরেই তিনি রেডিয়াম নামের আরেকটি তেজস্ক্রিয় মৌল আবিস্কার করেন। ১৮৬৭ সালে সিলেট জেলায় গজনফর আলী খানের জন্ম (গজনফর আলী খান ১৮৯৭ সালে অবিভক্ত ভারতের প্রথম বাঙালি মুসলিম আই.সি.এস. অফিসার ছিলেন) মৃত্যু-২৬-০৩-১৯৫৯ তারিখ। ১৮৬৭ সালের ১৬ এপ্রিল, অরবিল রাইট আমেরিকান ইন্ডিয়ানা প্রদেশে জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৫-১৯১২ তারিখ। ১৮৭১ সালে উইলবার রাইট আমেরিকান ইন্ডিয়ানা প্রদেশে জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৫-১৯৪৮ তারিখ। ১৯০৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাদের নির্মিত উড়োজাহাজের সফল উড্ডয়ন ঘটান। এরা দুই-ভাই বিমান উৎপাদন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। ১৮৬৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলায় বাংলা চলচ্চিত্রের জনক ও প্রবাল পুরুষ হীরালাল সেনের জন্ম, মৃত্যু-২৯-১০-১৯১৭ তারিখ। ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল, বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।
১৮৬৮ সালের ২৮ মার্চ, রাশিয়ায় বিপ্লবী সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম, মৃত্যু-১৮-০৬-১৯৩৬ তারিখ। ১৮৬৮ সালের ৭ জুন, পশ্চিম বাংলার উত্তর ২৪(চব্বিশ) পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ’র জন্ম, ১৯৬৮ সালের ১৮ আগষ্ট, তিনি ঢাকাতে ইন্তেকাল করেন। ১৯০৩ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে তিনি দৈনিক আজাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ সালের ৩০ এপ্রিল, ভারতের সিনেমা জগতের অগ্রদূত দাদা সাহেব ফালকে’র জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। ১৯১২ সালে ভারতের বোম্বে প্রথম সিনেমা তৈরী করেন দাদা সাহেব ফালকে। ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর, গুজরাটে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম, আততায়ীর গুলিতে নিহতঃ ৩০-০১-১৯৪৮ তারিখ। ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল, রুশ বিপ্লবের নেতা ও মার্কসবাদের রুপকার ভøাদিমির ইলিচ মহামতি লেনিনের জন্ম, মৃত্যু-২২-০১-১৯২৪ তারিখ। ১৮৭০ সালের ৭ জুন, নবাব স্যার সলিমুল্লাহর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০১-১৯১৫ তারিখ। (রাত আড়াই ঘটিকায় কলকাতায় চৌরঙ্গীস্থ বাসভবনে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। পরদিন ১৭ জানুয়ারি, বিকেলে বিশেষ স্টীমারযোগে নবাবের মরদেহ ঢাকায় আনা হয় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বেগম বাজারস্থ পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। ১৯০৩ সালে দিল্লীর দরবারে সপ্তম অ্যাডওয়ার্ডের মুকুট পরিধান উৎসবে সলিমুল্লাহকে নবাব বাহাদুর উপাধি প্রদান করে ইংরেজ সরকার। ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর, মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার তেলিরবাগ গ্রামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম; মৃত্যুঃ ১৬-০৬-১৯২৫ তারিখ।
১৮৭০ সালে ড. স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন সোহরাওয়ার্দীর জন্ম, মৃত্যু-১৯৩৫ সালে কলকাতায়। তিনি ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী বাঙালি মুসলমান। ১৮৭১ সালের ৭ আগষ্ট, কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৫-১২-১৯৫১ তারিখ। ১৮৭১ সালের ১০ অক্টোবর, চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিশিষ্ট পুঁথি সংগ্রাহক ও লেখক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ৩০-০৯-১৯৫৩ তারিখ। ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর, ঢাকায় কবি, গীতিকার ও গায়ক অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম, লক্ষেèৗয়ে মৃত্যুঃ ২৬-০৮-১৯৩৪ তারিখ। ১৮৭২ সালের ৪ এপ্রিল, গুজরাটের বস্ত্র শিল্প অধ্যুষিত সুরাট নগরে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর জন্ম, (আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ১৮৯৫ সালে অবিভক্ত ভারতের প্রথম মুসলিম আই. সি. এস. অফিসার ছিলেন) মৃত্যু-১০-১২-১৯৫৩ তারিখ লন্ডনে। ২৩ বছর বয়সে তরুণ ইউসুফ আলী ভারতের নতুন আই. সি. এস. অফিসার হিসেবে, ১৮৯৬ সালে যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুরে এ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদেন। ১৮৭২ সালের ১৮ মে, ইংল্যান্ডের মনমর্ডিথশায়ারের রাভেনস্ক্রফ্ট শহরে নোবেল জয়ী সাহিত্যিক, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ বারট্রান্ড রাসেলের জন্ম, মৃত্যু-০২-০২-১৯৭০ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৫০ সালে নোবেল পান। ১৮৭২ সালের ১৫ আগষ্ট, কলকাতায় জাতীয়তাবাদী নেতা, আধ্যাত্মিক সাধক ও দার্শনিক অরবিন্দু ঘোষের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৫-১২-১৯৫০ তারিখ। ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার গুনিয়ক গ্রামে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, বি. সি. এল.-এর জন্ম, লন্ডনে মৃত্যুঃ ৩১-০৭-১৯১৭ তারিখ। তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা। ১৮৭২ সালের ১৬ অক্টোবর, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার খাসপুর গ্রামে সাহিত্য চর্চা, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক ও সাংবাদিক আবদুল গফুর সিদ্দিকীর জন্ম, মৃত্যু-১৯৫৯ সালে। ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাকেরগঞ্জের সাতুরিয়া গ্রামে তাঁর মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন, ঢাকায় মৃত্যু-২৭-০৪-১৯৬২ তারিখ। চাখারে তিনি একটি একতলা ইটের বাংলো বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালের ৩০ নভেম্বর, ইংল্যান্ডে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক উইনষ্টন চার্চিল জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২৪-০১-১৯৬৫ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে নোবেল পান। ১৮৭৫ সালের ৩০ অক্টোবর, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয়তাবাদী নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম, মৃত্যু-১৫-১২-১৯৫০ তারিখ। ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, বিখ্যাত কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম, মৃত্যু-১৬-০১-১৯৩৮ তারিখ।
১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর, করাচিতে (জিন্নার বাবা-মায়ের নাম ছিল জেনাভাই ঠক্কর এবং মিঠাভাই) জেনাভাই এবং মিঠাভাইয়ের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথা অনুসারে জেনাভাই নাম স্থির করেন, মিঠাভাই সম্মতি জানান। মুহম্মদ আলি জেনাভাই। মামলায় সম্পত্তি হারানোর পর ১৮৯৩ সালের জানুয়ারিতে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা আদায় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুহম্মদ আলি জেনাভাই ইংল্যান্ডে জিন্নাহ নাম ধারণ করে। করাচি থেকে ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে বম্বের দুর্গা মহল্লাতে থাকতে শুরু করেন মুহম্মদ আলি জিন্নাহর বাবা ও মা। জায়গাটা বম্বের কেল্লার ঠিক বাইরে। জিন্না খোজা মুসলিম ছিলেন। তিনি শিয়া গোষ্ঠীর ইথনা আশারি স¤প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। হিন্দু লোহানা, জাতি থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন খোজা স¤প্রদায়। যার মধ্যে হিন্দু-মুসলিম দুয়েরই মিশ্রণ। ভারতের গুজরাত প্রদেশে কাথিয়াবাড়ের অবস্থান, কচ্ছের বৃহৎ রানের তলায়। পশ্চিমে আরব সাগর তাকে ঘিরে রয়েছে, প্রসারিত হয়েছে স্থলের দিকে, উর্বর এবং সুজলা ‘একশো রাজত্বের’ ভূমি, ভাল নাম সৌরাষ্ট্র। কাথিয়াবাড় অর্থাৎ কাথিদের ভূমি, যেখানে পাওয়া যায় উত্তম কাথিয়াবাড়ি ঘোড়া, সুন্দরী-কাথি নারী, বিচক্ষণ বণিক এবং বহু ধনী বণিক পরিবার, হিন্দু এবং মুসলিম। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন-১১-০৯-১৯৪৮ তারিখ করাচিতে। তিনি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তবে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুর আচরণে তিনি আলাদা রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, এমনকি পাকিস্তানের জন্মের পরও জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তান কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না এবং এ রাষ্ট্র হবে সকলের জন্য সমান। জিন্নাহ এবং সরোজিনী নাইডু ইংল্যান্ডে একই সময়ে ছিলেন। জিন্না মঞ্চাভিনয় করার চেষ্টা করেছিলেন, হয়তো তা পেশা হিসেবে নেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। জিন্নাহ ও সরোজিনী নাইডু দুজনেই শিল্পে আগ্রহী ছিলেন, সরোজিনী কবি ও লেখক হিসেবে, জিন্না নাটকে। জিন্না ভারতবর্ষে একমাত্র ব্যক্তি জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একসাথে প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর, সাতক্ষিরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা গ্রামে শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লাহ’র জন্ম, মৃত্যু-০৯-০২-১৯৬৫ তারিখ। তিনি পরীক্ষায় রোল নম্বর সিস্টেম করেন, এর আগে পরীক্ষায় নাম লেখা থাকত। ১৮৭৭ সালের ৯ মে (বাংলা ১২৮৪ সালের ২৫ বৈশাখ) চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার গোমদন্ডী গ্রামে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীলের জন্ম, মৃত্যু-০৬-০৪-১৯৬৭ তারিখ। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কবিগানের আসরে রমেশ চন্দ্র শীলকে ‘বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল’ উপাধি দেন উদ্যোক্তারা। ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর, বিখ্যাত উর্দু মহাকবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে জন্ম এবং মৃত্যু-২১-০৪-১৯৩৮ তারিখ। ১৮৭৮ সালের ২৫ জানুয়ারি (বাংলা-১০ মাঘ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ), বি-বাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সাতমোড়া গ্রামে সাধক ও কবি মহর্ষি মনোমোহন দত্তের জন্ম, মৃত্যু-০৫-১০-১৯১০ তারিখ (বাংলা-২০ আশ্বিন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। মহর্ষি মনোমোহন দত্ত বেঁচেছিলেন ৩১ বছর ৮ মাস ১০ দিন। মানবতাবাদী মহর্ষি মনোমোহন দত্ত তাঁর স্বল্প আয়ুতে ২০টিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যার মধ্যে মলয়া (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) সবচেয়ে আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মলয়া কাব্যগ্রন্থে গানের সংখ্যা সর্বমোট ৪২৬টি। এর মধ্যে প্রথম খন্ডে ২৮৭ এবং দ্বিতীয় খন্ডে ১৩৯টি মরমি গান লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত এ মরমিসংগীত মলয়ার প্রতিটি গানের সুরারোপ করেছেন মনোমোহনের আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম সাথি ও শিষ্য ফকির আফতাব উদ্দিন খাঁ। এ ছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, যোগপ্রণালী, উপাসনা প্রণালী, উপবন, তপোবন, লীলারহস্য, আরাধনা, গিরিজা মালতি, প্রেম পরিজাত, পথিক, পাথেয়, দেববাণী প্রভৃতি। ১৮৭৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, বিক্রমপুরে বানাড়ি গ্রামে চারণ কবি, গায়ক, নাট্যকার, সমাজসেবক, অভিনেতা ও পরিচালক মুকুন্দ দাসের জন্ম এবং কলকাতায় মৃত্যু-১৮-০৫-১৯৩৫ তারিখ। ১৮৭৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর, সোভিয়েত নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান জোসেফ স্তালিনের জন্ম, মৃত্যু-০৫-০৩-১৯৫৩ তারিখ। ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ব্রাহ্মণগাঁও, বিক্রমপুরে ভারতের কবি, রাজনীতিবিদ, বাগ্মী, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী ও ‘প্রাচ্যের বুলবুল’ সরোজিনী নাইডুর জন্ম, লক্ষেèৗ গভর্নর হাউসে মৃত্যু-০১-০৩-১৯৪৯ তারিখ। তিনি ১৮৯১ সালে বার বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাস। সরোজিনী নাইডু ১৯৪৫ সালে অল-ইন্ডিয়া ওমেন্স কনফারেন্স এ সভাপতি নির্বাচিত হন। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত ১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু এ পদে দায়িত্ব পালন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ব্রাহ্মণগাঁও। তাঁর পিতার নাম ড. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিজামের শিক্ষা উপদেষ্টা। ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ, জার্মানে আপেক্ষিকতাবাদের জনক বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম এবং মৃত্যু-১৮-০৪-১৯৫৫ তারিখ আমেরিকাতে। ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই, সিরাজগঞ্জে মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতিক, কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম, মৃত্যু-১৭-০৭-১৯৩১ তারিখ। ১৮৮০ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ি উপজেলার রাউথভোগ গ্রামে হতদরিদ্র ঘরে সূর্য কুমার বসুর জন্ম, মৃত্যু-জানা নেই। এ কৃতীপুরুষ পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম ১৯২২ সালে ‘ঢাকেশ্বরী কটন মিলস’ নামে বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর, রংপুর জেলার পায়রা বন্ধ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম এবং মৃত্যু কলকাতায় ভোর রাতে-০৯-১২-১৯৩২ তারিখ। ১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সাথে। ১৯১৬ সালে কলকাতায় ‘আঞ্জুমানে খাদেমুন ইসলাম’ নামে মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করেন। ১৯২৯ সালে তিনি কলকাতায় প্রথম মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ সালের ২৫ অক্টোবর, বিশ্বখ্যাত স্পেনীয় চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর জন্ম, মৃত্যু-০৮-০৪-১৯৭৩ তারিখ। ১৮৮১ সালের ১৯ মে, আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা, স্থপতি ও মহান নেতা মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক পাশার জন্ম, ইন্তেকাল-১০-১১-১৯৩৮ তারিখ। ১৮৮২ সালের ৩০ জানুয়ারি, যুক্তরাষ্টের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৪-১৯৪৫ তারিখ। ১৮৮২ সােেলর ৯ এপ্রিল, লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা বাজার গ্রামে কবি ও সাহিত্যিক শেখ ফজলুল করিমের জন্ম, ইন্তেকাল ২৮-০৯-১৯৩৬ তারিখ। ১৮৮২ সালে ইংরেজী সাহিত্যের এক দিকপাল ভার্জিনিয়া উলফের জন্ম, আত্মহত্যা করেন-২৮-০৩-১৯৪১ তারিখ। ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন কেইনসের জন্ম, মৃত্যু-১৯৬৩ সালে। ১৮৮৩ সালে ইতালীর স্বৈরশাসক বেনিত্তো মুসোলিনির জন্ম, (স্ত্রীর নাম ছিল ক্লারেটা) সস্ত্রীক নিহত হন-২৮-০৪-১৯৪৫ সালে। ১৮৮৩ সালে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার উলানিয়া জমিদার পরিবারে মুসলিম ঐতিহ্য ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-০৩-০২-১৯৮১ তারিখ। ১৮৮৪ সালের ১২ মার্চ, টাঙ্গাইল জেলার বিল্লাইক গ্রামে আইনজীবী ও সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের জন্ম, মৃত্যু-১২-০২-১৯৬১ তারিখ। ১৮৮৪ সালের ৬ এপ্রিল, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার শ্রীকাইল গ্রামে নরেন্দ্রনাথ দত্তের (ক্যাপ্টেন দত্ত নামে সুপরিচিত) জন্ম, মৃত্যু-২১-০৯-১৯৪৯ তারিখ। তিনি শ্রীকাইল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪১ সালে। ১৮৮৪ সালের ২০ এপ্রিল, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার মিজিতলা গ্রামে বৌদ্ধ ধর্মগুরু ও সপ্তম সংঘনায়ক অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের জন্ম, মৃত্যু-০১-০৭-১৯৭৪ তারিখ। ১৮৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুর খাঁ পরিবারে উজ্জল রতœ ও সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ’র জন্ম, মৃত্যুঃ ০২-০৯-১৯৬৭ তারিখ। ১৮৮৪ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নাগবাড়ী গ্রামে সাবেক বঙ্গীয় আইন সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এবং বছরখানেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন (১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) এবং (১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতায় তদানীন্তন পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন) ও প্রাদেশিক পরিষদের সাবেক স্পীকার (১৯৬২-১৯৬৮) আব্দুল হামিদ চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৯-১৯৬৯ তারিখ। ১৮৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কালীকচ্ছ গ্রামের বাঘবাড়িতে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৭-০৫-১৯৬৫ তারিখ। ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় শিক্ষাবিদ, পন্ডিত, বহু ভাষাবিদ ও মনীষী ইমিরিটাস অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ’র জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ১৩-০৭-১৯৬৯ তারিখ। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত সালের জুন মাসে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান করে ২৩ বছর অধ্যাপনা করে ১৯৪৪ সালে (অব.)। ১৮৮৫ সালের ১২ ডিসেম্বর, পাবনা জেলা সিরাজগঞ্জ শহরের কিছু দূরে এবং যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ধানগড়া গ্রামে মওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৭-১১-১৯৭৬ তারিখ। ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ভাসানচরে এক বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে ‘‘ভাসানী’’ শব্দটি যুক্ত হয়।
১৮৮৬ সালের ২ নভেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে রামরাইল গ্রামে আইনজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিক শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের জন্ম, ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পাক আর্মী কুমিল্লার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং গুলিতে মৃত্যু-১৪-০৪-১৯৭১ তারিখ। উনি একমাত্র ব্যক্তি প্রথম পাকিস্তানের জাতীয় গণ-পরিষদে বলেছিলেন, বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর, কলকাতা শহরে শিশু সাহিত্যিক ও কবি সুকুমার রায়ের জন্ম, মৃত্যুঃ ১০-০৯-১৯২৩ তারিখ। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও কবি এবং ছড়াকার, শিশুদের জন্য। ১৮৮৭ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের জন্ম, মৃত্যু-০৮-০১-১৯৭৬ তারিখ। ১৮৮৭ সালের ৩১ অক্টোবর, চীনা যোদ্ধা এবং জাতীয়তাবাদী চীনের (বর্তমান তাইওয়ান) প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেকের জন্ম, মৃত্যু-০৫-০৪-১৯৭৫ তারিখ। ১৮৮৭ সালের ২২ অক্টোবর, দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের লেখক ও সাংবাদিক জন রীডের জন্ম, মৃত্যু-১৯..? ১৮৮৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার শ্যামগ্রাম গ্রামে রাখাল চন্দ্র রায়ের জন্ম, মৃত্যু-০২-১১-১৯৮৯ তারিখ ১০২(একশত দুই) বছর বয়সে। উনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর, ঢাকার ভাগ্যকুলে সংস্কৃত পন্ডিত, গবেষক ও শিক্ষাবিদ অমরেশ্বর ঠাকুরের জন্ম, মৃত্যু-২৪-০১-১৯৭৯ তারিখ। ১৮৮৮ সালের ১ জানুয়ারি, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার কাঞ্চনা গ্রামে রায় সাহেব কামিনীকুমার ঘোষের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে। কলকাতা থেকে ফিরে এসে চাঁচা বঙ্গচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ১৯১৩ সাল থেকে আইন পেশায় নিযুক্ত হন। বিয়ের পর ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর ভারত শাসন আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে আইন পেশা ছাড়েন এবং আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি, বিক্রমপুরে রোহিনীকান্তের ঔরসে ও শরৎকামিনী দেবীর গর্ভে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর জন্ম, মৃত্যু-০৬-০২-১৯৪৭ তারিখ। ১৫৫৭ সালে মুঘল-পাঠানদের যুদ্ধের সময় কেদার রায়ের রাজ্যে বিক্রমপুর চলে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন টঙ্গীবাড়ি উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামেই বাস করত বাৎস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবার-ভট্টশালীরা। ১৮৮৮ সালের ২০ নভেম্বর, চাঁদপুর জেলার পাইকারদী গ্রামে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ‘সওগাত’ সম্পাদক ও বেগম পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের জন্ম, মৃত্যু-২১-০৫-১৯৯৪ তারিখ। ১৯১৭ সালে কলকাতা শহরে ‘সওকাত’ পত্রিকা প্রকাশ করে।
১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর, মক্কায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম, মৃত্যু-২২-০২-১৯৫৮ তারিখ (১৮৯০ সালে বাবা সপরিবারে কলকাতায় আসেন)। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পূর্বপুরুষেরা বাবরের আমলে হেরাট থেকে ভারতে আসেন। প্রথমে তাঁরা ডেরা বাধেন আগ্রায়; পরে ওঠে চলে যান দিল্লীতে। আলেমউলেমাদের এই পরিবারের মাওলানা জামালউদ্দিন ছিলেন আকবরের সময়ের একজন নামজাদা ধর্মগুরু। এ পরিবারের অনেকেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হন। শাহজাহানের আমলে মহম্মদ হাদীকে আগ্রার দুর্গাধিপতি করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবার মাতামহ ছিলেন মৌলানা মুনাবরউদ্দিন। তিনি ছিলেন মোগল যুগের অন্যতম শেষ রুকন-উল-মুদারসসিন। প্রথম শাহজাহানের সময়ে এ পদটির সৃষ্টি হয়। লেখাপড়া আর বিদ্যাচর্চার প্রসারে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের তদারকি করা ছিল এর উদ্দেশ্য। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবা মৌলানা খয়রুদ্দিন যখন খুবই ছোট তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পিতামহের মৃত্যু হয়। সুতরাং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবা তাঁর মাতামহের কাছে মানুষ হন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবার বয়স তখন পঁচিশ। তিনি সোজা মক্কায় চলে গিয়ে সেখানেই থেকে যান। নিজের একটি বাসভবন তৈরি করে শেখ মোহাম্মেদ জাহের বতবির কন্যাকে তিনি বিয়ে করেন। শেখ মোহাম্মেদ জাহের ছিলেন মদিনার একজন বড় তত্ত¡জ্ঞ। আরবদেশের বাইরেও তাঁর নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। মিশর থেকে দশ খন্ডের আরবী কেতাব বেরোবার পর ইসলামিক দুনিয়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবাও খ্যাতিমান হন। তিনি বহুবার বোম্বাইতে এবং একবার কলকাতায় আসেন। দু জায়গাতেই তাঁর বিস্তর ভক্ত আর শারগেদ ছিল। বাবা ইরাক, সিরিয়া আর তুরস্কেও ব্যাপকভাবে ঘুরেছেন।
১৮৮৮ সালের ৪ ডিসেম্বর, ফরিদপুর জেলার খন্দরপাড়ায় শিক্ষাবিদ ও বাঙালি ঐতিহাসিকদের পুরোধা অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ১২-০২-১৯৮০ তারিখ ভারতে। ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার গ্রামে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীর জন্ম এবং ১৯০৮ সালে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ১৮৮৯ সালের ১৬ এপ্রিল, যুক্তরাজ্যে ইংরেজ অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম, আমেরিকায় মৃত্যু-২৫-১২-১৯৭৭ তারিখ। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক রিলের নির্বাক ‘‘মেকিং এ লিভিং’’ দিয়ে মহান চলচ্চিত্রশিল্পী চ্যাপলিনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল, জার্মান ফ্যাসীবাদী একনায়ক এডলফ হিটলারের জন্ম হয় অস্ট্রিয়ায়, ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল, চুড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে ভূ-গর্ভস্থ বাঙ্কারে এডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন। (মৃত্যু-১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল ইংলিশ চ্যানেলের ওপর ব্রিটিশ বৈমানিকের গুলিতে হিটলারকে বহনকারী বিমান ভূপাতিত। হিটলার নিহত হয়েছেন, তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে লন্ডনে। ২১ বছর বয়সী হ্যারিকেন জেট ফাইটার প্লেনের বৈমানিকের গুলিতে ফুয়েরারকে জার্মান বিমানটি ভূপাতিত হয় ইংলিশ চ্যানেলের ওপর। ধারনা করা হচ্ছে, জার্মান নেতা দ্বীপরাষ্ট্র ইংল্যান্ড আক্রমণের অগ্রগতি সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার অনির্ধারিত অভিযানে ছিলেন।) হিটলারের জার্মান নাগরিত্ব বাতিল করা হয়। হিটলার নিজেই ইহুদি এবং উত্তর আফ্রিকান বংশোদ্ভুত।
১৮৮৯ সালের ৫ আগষ্ট, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি-১৯২০) কমরেড মুজাফফর আহমদের জন্ম নোয়াখালী জেলার স›দ্বীপে, মৃত্যুঃ ১৮-১২-১৯৭২ তারিখ কলকাতায়। ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৫-১৯৬৪ তারিখ। ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনিপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে বিপ্লবী ক্ষুধিরাম বসুর জন্ম, পালাবার সময় ক্ষুধিরাম গ্রেফতার হন এবং ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী ক্ষুধিরামের ফাঁসি কার্যকর হয়-১১-০৮-১৯০৮ তারিখ। ক্ষুধিরাম বড় লাটকে মারতে যেয়ে মেরে ফেলে ভারতবাসীকে। ১৮৮৯ সালে ভারতের জলপাইগুড়িতে শিক্ষাবিদ স্যার আহমদ ফজলুর রহমানের জন্ম, মৃত্যু-১৯৪৫ সালে। উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৮৯০ সালে চারসাদ্দাই তহশিল, জেলা পেশোয়ারে সীমান্ত গান্ধীর নাম, ভারত-রতœ বাদশা খান বা খান আবদুর গফফার খানের জন্ম, ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবাদ পুরুষ মৃত্যু-২০-০১-১৯৮৮ তারিখ। (তাঁর আসল বয়স-এর চাইতে অনেক বেশি বা কেউ মনে করে যে, ১৮৮০ সালে প্রকৃত জন্ম)। তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক। ১৮৯০ সালের ১৯ মে, ভিয়েতনামের বিপ্লবী জন নেতা হো. চি. মিনের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৯-১৯৬৯ তারিখ। ১৮৯০ সালের ২ অক্টোবর, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম, তাসখন্দে মৃত্যুঃ ২৩-০৯-১৯৬৫ তারিখ। ১৮৯০ সালে ফদিপুরে অবিভক্ত বাংলার অন্যতম তেজস্বী মুসলিম লীগ নেতা, প্রথম মুসলমান সরকারী কৌসুলি, ফরিদপুর আইনজীবী সমিতির সুদীর্ঘকালের সভাপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একদা প্রবীণতম আইনজ্ঞ খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইলের জন্ম, মৃত্যু-ঢাকায় ০৮-০৫-১৯৮১ তারিখ। ১৮৯০ সালে পাঁচবাগ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী রাজবন্দী (জাতীয় সংসদে স্বীকৃত) এবং একাধারে তিন দশক ধরে নির্বাচিত এম.এল.এ. ও এম.এন.এ. হয়রত মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী(রহ.)’র জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৯-১৯৮৮ তারিখ। ১৮৯০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামে নবাব কে. জি. ফারুকীর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৯৮৪ সালে। তিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবাংলার মেদেনীপুরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ০৫-১২-১৯৬৩ তারিখ। ১৮৯২ সালের ২৭ নভেম্বর, বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক ও লেখক স্যার আজিজুল হকের জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৩-১৯৪৭ তারিখ। ১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল, বিপ্লবী রাহুল সাংকৃত্যায়ণের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৪-০৬-১৯৬৩ তারিখ। ১৮৯৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নূরুল আমীনের জন্ম, পাকিস্তানে মৃত্যুঃ ০২-১০-১৯৭৪ তারিখ। ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বংশাই নদীর তীরে শেওরাতলী গ্রামে দারিদ্রপীড়িত এক পরিবারে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ মেঘনাথ সাহার জন্ম, মৃত্যু-১৯৫৬ সালে বিখ্যাত এই জ্যোতিঃ পদার্থবিদ মৃত্যুবরণ করেন। দোকানদার বাবার ছেলে হিসেবে সবাই ভেবেছিল ছেলেটিও দোকানি হবে। ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স ও ১৯১১ সালে এফ. এ. পাস করেন। তিনি জগৎ বিখ্যাত পদার্থ ও অংক শাস্ত্রবিদ। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
১৮৯৪ সালের ১৯ জুলাই, ঢাকায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের জন্ম, রাজনীতিবিদ খাজা নাজিমুদ্দিনের ইন্তেকাল-২২-১০-১৯৬৪ তারিখ। খাজা নাজিমউদ্দিনকে ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে উৎখাত করেন গোলাম মোহাম্মদ ও আইয়ূব খানের সহযোগিতায় তখনকার পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। মীর জাফরের বংশধর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। ইরানি বংশদ্ভূত এস. পি. টুনি মির্যার ছেলে হলো মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। ইস্কান্দার মির্যার জন্ম বাংলায় ছিল। সেনাবাহিনীর সহায়তায় ১৯৫৫ সালে ইস্কান্দার মির্যা পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদ দখল করেন। আর বরখাস্ত করেন মোহাম্মদ আলীকে। ১৯৫৬ সালে আরেক বাঙালি রাজনীতিক হোসেন শহীদ সোহওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। আর নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা দেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করে ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর, প্রধান সেনাপতি আইয়ূব খানকে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যাকে দেশত্যাগে বাধ্য করে নিজে জেনারেল আইয়ূব খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। আবার ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ, জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। সে বছরই সাবেক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যা লন্ডনে মারা যান। কিন্তু তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্টকে নিজ দেশে দাফনের অনুমতি দেননি। তাই লন্ডন থেকে ইস্কান্দারের মরদেহ ইরানে নেওয়া হয় এবং পরে তেহরানে তাঁকে দাফন করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের সাথে এটি ছিল সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে বারবার রাজনীতিতে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করেছে। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন। তারপর আবার ১৯৯৮ সাল থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন জেনারেল (অব.) পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৯ সালে ইস্কান্দার মির্যাকে তেহরানে দাফন করা হলেও তাঁর প্রেতাত্মা এখনো জীবিত। শুধু নাম বদল হয়েছে, কিন্তু চরিত্র বদলায়নি। জেনারেল আইয়ূব খান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল জিয়াউল হক এবং জেনারেল পারভেজ মোশাররফ হোসেন হয়ে বেঁচে ছিলেন।
১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট নেতা ও কমরেড মাও সে তুং-এর জন্ম, মৃত্যু-০৯-০৯-১৯৭৬ তারিখ। ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ, চট্টগ্রামে মাস্টার দা সূর্যসেনের জন্ম, ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নায়ক মাষ্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি হয়। ১৮৯৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার বিরামদি গ্রামে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ’র জন্ম, ইন্তেকাল-২৯-০৩-১৯৭৮ তারিখ। ১৮৯৪ সালে রংপুরে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রি আবু হোসেন সরকারের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৭-০৪-১৯৬৯ তারিখ। ১৮৯৪ সালে নোয়াখালীতে বিট্রিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও সমাজসেবিকা আশালতা সেনের জন্ম, মৃত্যু-দিল্লীতে ০৩-০২-১৯৮৬ তারিখ। ১৮৯৬ সালে পূর্ব পাঞ্জাবের কার্নায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের জন্ম, রাওয়ালপিন্ডিতে জনসভায় বক্তৃতাকালে আততায়ীর গুলিতে নিহতঃ ১৬-১০-১৯৫১ তারিখ। ১৮৯৬ সালের ৪ নভেম্বর, রনদা প্রসাদ সাহার জন্ম, মির্জাপুর (টাংগাইল), যার নাম আরপি সাহা। ১৯৩৮ সালে ৭৫০(সাতশত পঞ্চাশ) শয্যাবিশিষ্ট বিখ্যাত কুমুদিনী হাসপাতাল স্থাপন করেন। ০৭-০৫-১৯৭১ তারিখ, গভীর রাতে পাক বাহিনী রনদা প্রসাদ সাহা ও তার একমাত্র পুত্র রবিকে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। ১৮৯৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, বি-বাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মরিচাকান্দি গ্রামে বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে প্রথম ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মিজানুর রহমানের জন্ম, মৃত্যু-১৫-০৮-১৯৮১ তারিখ। তিনি ১৯২৬ সালে প্রথম বি. সি. এস. লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসুর জন্ম, নেতাজি মৃত্যুবরণ করেছেনঃ ১৮-০৮-১৯৪৫ তারিখ রাত ১১টা ২০মিনিটের সময় তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায়। ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই, কুষ্টিয়ার কুুমারখালী উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের মাতুলালয়ে বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস, ইমিরিটাস অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম, মৃত্যুঃ০৯-১০-১৯৮১ তারিখ। তার ছোটবেলা কেটেছে রাজবাড়ী (ফরিদপুর) জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামের পৈত্রিক নিবাসে। ১৮৯৭ সালের ৩ নভেম্বর, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৩-১৯৭৮ তারিখ। ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বর, বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার নরোত্তমপুর গ্রামে উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, নারীপ্রগতি ও মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ মনোরমা বসুর জন্ম, মৃত্যু-১৯৯০ সালে।
১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর, কিশোরগঞ্জ জেলায় “বাঙ্গালী থাকিব না মানুষ হইব’’ বইয়ের লেখক নিরুদ চন্দ্র চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-১৯৯৯ সালে লন্ডন শহরে। ১৮৯৭ সালের ২১ ডিসেম্বর, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম, মৃত্যুঃ ১৩-১০-১৯৬৪ তারিখ। ১৮৯৮ সালের ১ মে, চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ গ্রামে কথাশিল্পী মাহবুব-উল-আলমের জন্ম, ১৯৮১ সালের ৭ আগষ্ট কাজীর দেউড়ীস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের জন্ম, ইন্তেকাল-১৮-০৩-১৯৭৯ তারিখ। ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই, বাংলা সাহিত্যির দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭২ সালে। ১৮৯৮ সালে বরিশালের সন্তান অকুতোভয় পাইলট ইন্দ্রনীল রায়ের জন্ম, মৃত্যু-১৮-০৭-১৯১৮ তারিখ। পাইলট ইন্দ্রনীল রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ রাখেন যে-বাঙ্গালীরা বীরের জাতি। ১৯১৬ সালে বিশ্বে প্রথম বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় ‘‘ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীতে ক্যাডেট পাইলট হিসাবে তিনি লাভ করেন কিংস কমিশন’’। ১৮ জুলাই তাঁর জঙ্গী বিমানটি ফের গুলি বিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হয়। বিধবস্ত বিমানের সাথে তিনি প্রাণ হারান। মাত্র ২০(বিশ) বছর আয়ু পেয়েছিলেন। ‘‘পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য, তাদের মধ্যে ইন্দ্রনীল রায় একজন…এ অঞ্চলের একমাত্র ফাইটার এইস পাইলট হিসাবে তিনি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।’’ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রæয়ারি, বরিশাল জেলায় বাংলা আধুনিক কাব্যবিক জীবনানন্দ দাশের জন্ম, ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর, কলকাতায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু।
১৮৯৯ সালের ২৫ মে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-০৭-১৯৭৬ তারিখ বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা বেজে ১০ মিনিটে। ১৯২১ সালের ১৭ জুন, নজরুলের সঙ্গে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের সৈয়দা নার্গিস আসর খানম ওরফে সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয়। অজ্ঞাত কারণে বিয়ের রাতেই শেষ হয়ে যায় এ সম্পর্ক। পরে ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল, প্রমীলাকে বিয়ে করেন নজরুল। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই থেকে কবি আলজাইমার্স ডিজিজে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ। মা জাহিদা খাতুন। ১৯১৭ সালে করাচীতে গিয়ে তিনি সৈনিকের খাতায় নাম লেখান। তিনি ১৯২০ সালে সেখান থেকে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজকে উৎসর্গ করেন। কবি-পতœী প্রমীলা নজরুল ইসলাম কলকাতায় ইন্তেকালঃ ৩০-০৬-১৯৬২ তারিখ। কবি-পতœীর ইন্তেকালের প্রায় এক দশক পর কবিকে ঢাকায় আনা হয়েছিল ২৪ মে, ১৯৭২ সালে। ১৮৯৯ সালের ২৮ জুন, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার হুমায়ূনপুর গ্রামে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনয়েম খানের জন্ম, মৃত্যু-১৪-১০-১৯৭১ তারিখ। গভর্নর ছিলেন ২৮-১০-১৯৬২ তারিখ থেকে ২৩-০৩-১৯৬৯ তারিখ পর্যন্ত। ১৮৯৯ সালে যশোর জেলার ঝিনাইদহের অধিবাসী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের রোমান্সকর ব্যক্তিত্ব বাঘা যতীন দাসের জন্ম, ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, ৬৩ দিন অনশনের পর লাহোর কারাগারে মারা যান। ১৯০০ সালের ১৯ মার্চ, নোবেল বিজয়ী ফরাসী পদার্থবিদ ফ্রেদেরিক জুলিও কুরির জন্ম, ১৯৫৬ সালের ১৭ মার্চ, নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ জোলিও কুরির মৃত্যু।
১৯০০ সালের ৮ মে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মাড় গ্রামের মাতুলালয়ে স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার জন্ম, ঢাকায় মৃত্যুঃ ০৩-১১-১৯৭৭ তারিখ। ১৯০০ সালে সিলেটে আদর্শিক বাবা-মায়ের পরিবারে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিকন্যা, নারীনেত্রী ও দেশব্রতী লীলা রায়ের (নাগ) জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১১-০৬-১৯৭০ তারিখ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। ১৯০০ সালের ১৭ মে, ইরানের খোমেইন শহরে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু ও রাজনৈতিক নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনীর (রহ.) জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৬-১৯৮৯ তারিখ। ১৯০০ সালের ২৭ নভেম্বর, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত হাটিকুমরুল ইউনিয়নের তারুটিয়া নামক গ্রামের সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে কিংবদন্তী পুরুষ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের জন্ম, মৃত্যুঃ ২০-০৮-১৯৮৬ তারিখ। ১৯০০ সালে দিনাজপুর জেলার সুলতানপুর গ্রামে কৃষকনেতা ও রাজনীতিক হাজী মোহাম্মদ দানেশের জন্ম, মৃত্যু-২৮-০৬-১৯৮৬ তারিখ। ১৯০০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে বেহালাবাদক, কন্ঠশিল্পী, সুরকার ও সঙ্গীত শিক্ষক ওস্তাদ মতিউর রহমানের জন্ম, মৃত্যুঃ ০১-০২-১৯৬৭ তারিখ। ১৯০০ সালে বরিশাল জেলায় বিপ্লবী লেখক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম, মৃত্যু-১৯৮৫ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিন খন্ড রচনা সমগ্র প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর লেখা-লেখি করার ওপর বিধিনিষেধ করেছিলেন। ১৯০০ সালের ৮ ডিসেম্বর, রাজস্থানের উদয়পুরে নৃত্যলোকের রাজপুত্র উদয়শংকরের জন্ম, মৃত্যুঃ২৬-০৯-১৯৭৭ তারিখ। তিনিই প্রথম বাঙালি, যিনি জগৎসভায় নৃত্যকলা প্রদর্শন ও প্রচার করে প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন। উদয়শংকরের আদি নিবাস বাংলাদেশের যশোরের কালিয়া গ্রামে। ১৯০১ সালের ৬ জুন, আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার স্থপতি ড. আহমদ সুকর্নোর জন্ম, মৃত্যু-২১-০৬-১৯৭০ তারিখ। ১৯০১ সালের ২৮ জুলাই, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহের জন্ম, মৃত্যুঃ ৩১-১২-১৯৯০ তারিখ। মাতৃকুল ছিলেন নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুরের জমিদার। ১৯০১ সালে ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার রামনগর গ্রামে সাংবাদিক ও রাজনীতিক হামিদুল হক চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৮-০১-১৯৯২ তারিখ। ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর, কুচবিহারের বলরামপুর গ্রামে মরমী শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের জন্ম, মৃত্যুঃ ৩০-১২-১৯৫৯ তারিখ। শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের পিতা জাফর আলী আহমেদ তুফানগঞ্জ আদালতের উকিল ছিলেন। ১৯০২ সালের ১৭ জানুয়ারি, তুরস্কের ছোট্ট শহর আলেপ্লোয় এক নিঃসঙ্গ বিপ্লবী ও বিখ্যাত তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৬-১৯৬৩ তারিখ। ১৯০২ সালের ১ জুলাই, ভারতের পশ্চিম বাংলায় রম্য সাহিত্যিক ও বহু ভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম, ঢাকায় ইন্তেকাল ১১-০২-১৯৭৪ তারিখ।
১৯০২ সালে বর্তমান চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার এক সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক, পাকিস্তানের প্রথম এফআরসিপি (ইউ. কে.) ও বাঙালী মুসলমানদের চিকিৎসা পেশার অগ্রদুত ডা. নওয়াব আলীর জন্ম এবং ঢাকায় ইন্তেকাল-০৪-০৭-১৯৭৭ তারিখ। ১৯০২ সালে পশ্চিমবাংলায় বাংলা সিনেমা জগতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ও নাঠ্যাভিনেতা ছবি (শচীন্দ্রনাথ) বিশ্বাসের জন্ম, মৃত্যু-১১-০৬-১৯৬২ তারিখ মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি, পল্লী কবি জসিমউদ্দীনের জন্ম, মৃত্যু ১৪-০৩-১৯৭৬ তারিখ। ১৯০৩ সালের ১৪ জানুয়ারি, বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় শিক্ষক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. নীহাররঞ্জন রায়ের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-৩০-০৮-১৯৭৮ তারিখ। তাঁর সৃষ্টি বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব। ১৯০৩ সালের ১ জুলাই, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত কেওচিয়া গ্রামে শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক মনস্বী আবুল ফজলের জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৫-১৯৮৩ তারিখ। ১৯০৩ সালের ২৯ অক্টোবর, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ইলমদী গ্রামে সাবেক জাতীয় পরিষদের সদস্য (এম.এন.এ.), ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, কবি ও সাংবাদিক বে-নজীর আহমেদের জন্ম, মৃত্যু-১২-০২-১৯৮৩ তারিখ। ১৯০৩ সালে ভারতের হায়দারাবাদ রাজ্যের আওরংগবাদ শহরে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদীর জন্ম, আমেরিকায় মৃত্যু-২২-০৯-১৯৭৯ তারিখ পাকিস্তান সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা পৌঁনে ছ’টায়। তিনি ১৯৪১ সালের ২৬ আগষ্ট, লাহোরে ৭৫ জন লোক নিয়ে ‘জামায়াতে ইসলামী’ নামে একটি আদর্শবাদী দল গঠন। ১৯০৩ সালের ১ ডিসেম্বর, চট্টগ্রামে বিপ্লবী (চট্টগ্রাম অস্্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম নায়ক এবং রাজনীতিবিদ) অনন্ত সিং-এর জন্ম, মৃত্যুঃ ২৫-০১-১৯৭৯ তারিখ। ১৯০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি, পাবনা জেলার সুজানগর থানার মুরারিপুর গ্রামে শিক্ষাবিদ ও লোকসংস্কৃতি বিশেযজ্ঞ মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের জন্ম, ঢাকার শান্তিনগরে মৃত্যু-১৯-০৯-১৯৮৭ তারিখ। ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ, অন্নদা শংকর রায়ের জন্ম, মৃত্যু-২৮-১০-২০০২ তারিখ। তিনি ১৯২৯ সালে আই.সি.এস. পাশ করেন। কবি, সাহিত্যক, ছড়াকার এবং ১৯২৯ সালে বিলেত গিয়েছিলেন। ১৯০৪ সালের ১২ জুলাই, চিলির পারলাল শহরে পরিচিত ছিল কমিউনিষ্ট লেখক হিসেবে ও নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক পাবলো নেরুদার জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৯-১৯৭৩ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে নোবেল পান।
১৯০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি, পশ্চিম বাংলায় দার্শনিক-রাজনীতিবিদ আল্লামা আবুল হাশিমের জন্ম, (১৯৫০ সালে পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিমবিরোধী সা¤প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং এ কারণে ১৯৫০ সালে আবুল হাশিম দেশ ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন) মৃত্যুঃ ০৫-১০-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৫ সালের ৬ মার্চ, ঢাকা জেলার দামরাই উপজেলার বালিয়া গ্রামে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের জন্ম, মৃত্যু-০৭-১২-১৯৯১ তারিখ। ১৯০৫ সালের ১৫ এপ্রিল, বরিশালের গৈলা গ্রামে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী শহীদ তারকেশ্বর সেনগুপ্তের জন্ম, বন্দিশিবির থেকে পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৫-০৯-১৯৩১ তারিখ। ১৯০৫ সালে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার গাজীপুর গ্রামে ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক আবদুল হালিমের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭২ সালে। ১৯০৫ সালে বিপ্লবী নেতা এবং ঐতিহাসিক নক্সালবাড়ী লড়াইয়ের সূচনাকারী শহীদ কমরেড চারু মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৮-০৭-১৯৭২ তারিখ। ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রæয়ারি, বাংলা সিনেমা জগতের বিখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা পাহাড়ী (নরেন্দ্রনাথ) সান্যালের জন্ম, মৃত্যু-১০-০২-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৬ সালের ১ জুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার আড়াইসিধা গ্রামে কবি আবদুল কাদিরের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৯-১২-১৯৮৪ তারিখ। ১৯০৬ সালে পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ূব খাঁনের জন্ম, (আইয়ূব খাঁন ১৯৫১ সালে পাকিস্তান আর্মীর সেনাপ্রধান হন এবং ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ূব খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।) মৃত্যুঃ ২০-০৪-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রসুল্লাবাদ গ্রামে দার্শনিক ও প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমানের জন্ম, মৃত্যু-২৮-০৮-১৯৮৭ তারিখ। ১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবর, সুনামগঞ্জের তেঘরিয়া গ্রামস্থ নানা মরমী কবি হাসন রাজার বাড়িতে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জন্ম, মৃত্যু-০১-১১-১৯৯৯ তারিখ। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর, কুমিল্লার চর্থা গ্রামে উপমহাদেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সুরকার শচীন দেব বর্মণের জন্ম, বোম্বে শহরে মৃত্যুঃ ৩১-১০-১৯৭৫ তারিখ।
১৯০৭ সালের ১ ফেব্রæয়ারি, সিলেট জেলার বিয়ানী বাজারের লাউতা গ্রামে অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেবের জন্ম, ঢাকায় শহীদঃ ১৪-১২-১৯৭১ তারিখ। ১৯০৭ সালের ২ ফেব্রæয়ারি, নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার চানগাঁও গ্রামে তাঁর নানাবাড়িতে খালেকদাদ চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যু-১৬-১০-১৯৮৫ তারিখ। দুই বাংলাতেই তিনি ছিলেন খ্যাতিমান লেখক। ১৯০৭ সালের ২৫ নভেম্বর, যশোর জেলার আলফাডাঙ্গার বুড়াইচ গ্রামে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক নূরুল মোমেনের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০২-১৯৯০ তারিখ। ১৯০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যালিয়াম সিরিজের ঘুমের বড়ি’র আবিস্কারক লিও স্টার্নবাখের জন্ম, উত্তর ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিলে নিজ বাসভবনে ৯৭ বছর বয়সে পরলোগমন-২৮-০৯-২০০৫ তারিখ। ১৯০৮ সালের ১ ফেব্রæয়ারি, বাগেরহাটের ফকিরহাট থানার সাতশৈয়া গ্রামে আবদুস সবুর খানের জন্ম, মৃত্যু-২৫-০১-১৯৮২ তারিখ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় খুলনা অঞ্চলকে জোর করেই হিন্দুস্থানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেদিন এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে খান এ সবুরের নেতৃত্বেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। যার ফলে তখন খুলনা অঞ্চল ন্যায়সঙ্গতভাবেই পাকিস্তানে রাখা সম্ভব হয়েছিল। ১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রæয়ারি, ভারতের বিশিষ্ট বাংলা শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৬-০৪-২০০৭ তারিখ। ১৯০৮ সালের ১ এপ্রিল, বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা ফরাসি লুসিয়ে লরাঁর জন্ম, মৃত্যু-১১-০৪-২০০৫ তারিখ। ১৯৩০ সালের ১৩ জুলাই, প্রথম বিশ্বকাপ হয়েছিল। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের মোট গোল হয়েছে (২০৬৩)টি।
১৯০৮ সালের ২৯ মে, সাহিত্যক, ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী মানিক বন্ধ্যোপ্যায়ের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৩-১২-১৯৫৬ তারিখ। মাত্র বেঁচেছিলেন ৪৮ বছর। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ২০০ শতের মত উপন্যাস লিখেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জের মালপদিয়া গ্রামে। ১৯০৮ সালে হাইড্রোজেন বোমার জনক এডওয়ার্ড টেনলরের জন্ম, মৃত্যু-০৯-০৯-২০০৩ তারিখ। ১৯০৮ সালে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক নড়াইলের বাকলি গ্রামের কৃষক নেত্রী পরিবালা বিশ্বাসের জন্ম, মৃত্যু-২৫-০৫-২০০৭ তারিখ। ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর, কুমিল্লা শহরে বিখ্যাত বাঙালি কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও সংবাদপত্র সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যুঃ ১৮-০৩-১৯৭৪ তারিখ। ১৯০৮ সালে মাদারীপুর জেলার কালকিনী উপজেলার গোপালপুর কাজী পরিবারে কাজী আশরাফ মাহমুদের জন্ম, মৃত্যু-০৩-১২-১৯৮৩ তারিখ। তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট হিন্দী কবি, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ, মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ১৯০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি, মুঘল ঐতিহ্যের কবি কাজী কাদের নওয়াজের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০১-১৯৮৩ তারিখ। ১৯০৯ সালের ২৯ এপ্রিল, (বাংলা ১৩১৬ সনের ১৬ বৈশাখ) শেরপুর অঞ্চলের তৎকালীন জমিদার রমেশ চন্দ্র নিয়োগীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রবি নিয়োগী, আমৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং মৃত্যু-১০-০৫-২০০২ তারিখ। তাঁর ৯৩ বছরের জীবনে ৪৩ বছরই কেটেছে কারাগারে। ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই, কলকাতার সুবিখ্যাত কলেজ স্ট্রিটের পাশে টেমার লেনে কবি বিঞ্চু দের জন্ম, মৃত্যু-০৩-১২-১৯৮২ তারিখ। বিঞ্চু দের এক বড় পরিচয় তিনি সমাজবাদে বিশ্বাসী, সেই সূত্রে সমাজবদলের সম্ভাবনায় অঙ্গীকৃত। তিনি ছিলেন ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সক্রিয় কর্মী, সংগঠক। ১৯০৯ সালের ১৮ আগষ্ট, উপমহাদেশের প্রখ্যাত সানাইবাদক ওস্তাদ সোনা মিয়ার জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৮-২০১১ তারিখ দিবাগত রাতে ঢাকায়। বরেণ্য এই শিল্পী ভারতবর্ষের স্বনামধন্য সানাইবাদক ওস্তাদ মুন্না খাঁর শিষ্য ছিলেন। ১৯০৯ সারের ১৯ সেপ্টেম্বর, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে গঠিত কমিটিতে নির্বাচিত কমিউনিষ্ট নেতা নেপাল নাগের জন্ম, মৃত্যু-কলকাতায় ০৫-১০-১৯৭৮ তারিখ। ১৯১০ সালের ৭ জানুয়ারি, খ্যাতিসম্পন্ন পানিবিশেষজ্ঞ বি. এম. আব্বাসের জন্ম, ইন্তেকাল-২৭-১২-১৯৯৬ তারিখ।
১৯১০ সালের ৫ ফেব্রæয়ারি, আর্জেন্টিনার প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলোয়াড় ফ্রান্সিসকো ভারাল্লোর জন্ম। তিনি ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ও ছিলেন এবং আর্জেন্টিনার পক্ষে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলে। প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই একমাত্র জীবিত খেলোয়াড়। তিনি ০৯-০৬-২০০৬ তারিখ বিশ্বকাপ খেলায় উপস্থিত ছিলেন। ০৫-০২-২০১০ সালে শতবর্ষ পার করেন। ১৯১০ সালের ২৩ মার্চ, জাপানের টোকিওর এক সিনেমাভক্ত পরিবারে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাপানি চলচ্চিত্রকার, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র সম্পাদক ও প্রয়োজক আকিরা কুরোশাওয়ারের জন্ম, জাপানের টোকিওতে মৃত্যু-০৬-০৯-১৯৯৮ তারিখ। সুগাতা সানশিরো মুক্তি পায় ১৯৪৩ সালে। প্রথম ছবিতেই পরিচালক হিসেবে আকিরা কুরোশাওয়ার প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। এন্টারটেইনমেন্ট উইকলি কর্তৃক নির্বাচিত সর্বকালের সেরা পরিচালকদের মধ্যে আকিরা কুরোশাওয়ার অবস্থান ৬ষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ ৫০ জন চলচ্চিত্রকারের মধ্যে তিনি একমাত্র এশীয় ও আমেরিকানদের বাইরে তাঁর অবস্থান সবার ওপরে। ১৯১০ সালের ২৭ আগষ্টে, যুগো¯øাভিয়ার স্কপজেতে মাদার তেরেসার জন্ম, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির প্রতিষ্ঠাতা মাদার তেরেসার মৃত্যু-০৫-০৯-১৯৯৭ তারিখ কলকাতা শহরে। ১৯১০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বাজালিয়ায় ডা. মনীন্দ্রলাল চক্রবর্তীর জন্ম, মৃত্যু-১৪-০৭-১৯৮৩ তারিখ। স্কুলে থাকতেই তিনি গোপন বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১০ সালের ২০ অক্টোবর, নেত্রকোনা জেলার উলুয়াটি গ্রামে সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুজীবুর রহমান খাঁ’র জন্ম, মৃত্যু-০৫-১০-১৯৮৪ তারিখ। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতের প্রথম গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারি, চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার উত্তর ভূর্ষি গ্রামে বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১০-০৪-২০১৩ তারিখ। তাঁর ১৯২৯ সালে মাস্টারদার সঙ্গে পরিচয় হয়। কয়েকবার সাক্ষাতের পর মাস্টারদা বিপ্লবী দলে ঢোকার অনুমতি দেন বিনোদবিহারীকে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ৪০ বছর পর ১৯৭১ সালে বিনোদবিহারী নিজেকে যুক্ত করেন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। ১৯১১ সালের ১১ জানুয়ারি, বিচারপতি সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুঃ ০৩-০৪-১৯৭৯ তারিখ। ১৯১১ সালের ১১ ফেব্রæয়ারি, পাকিস্তানের পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে আজন্ম বিপ্লবী কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্ম, ১৯৮৩ সালে অসুস্থ হয়ে নিজের দেশ পাকিস্তানের লাহোরে ফিরে আসেন, এখানেই মৃত্যু-১৯-১০-১৯৮৪ তারিখ। ১৯১১ সালের ১৩ মার্চ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৮-১৯৮৮ তারিখ। ১৯১১ সালের ৫ মে, চট্টগ্রামের ধলঘাটের দক্ষিণ সুরমা এলাকায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বীরকন্যা প্রীতিলতার জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৯-১৯৩২ তারিখ। প্রীতিলতা চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের মেয়ে সদস্য ও ছাত্রীদের নিয়ে চক্র গড়েন। ১৯১১ সালের ৩০ মে, দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, কিংবদন্তির এক নায়ক ও দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জন্ম, মৃত্যুঃ ০১-০৬-১৯৬৯ তারিখ। ১৯১১ সালের ৬ জুন, লোহাগড়া (নড়াইল) ইতনা গ্রামের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক ডা. নীহার রঞ্জন রায়ের/গুপ্তের জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৮-১৯৮১ তারিখ। ১৬-বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘রাজকুমারীম্ব’ প্রকাশিত হয়।
১৯১১ সালের ২০ জুন, বাখেরগঞ্জ জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে নানাবাড়িতে বেগম সুফিয়া কামালের জন্ম, মৃত্যুঃ ২০-১১-১৯৯৯ তারিখ। তাঁর বাবারবাড়ি ব্রহ্মণবাড়িয়া জেলার সেন্দুর-সিলাউর গ্রামে। ১৯১১ সালের ৯ জুলাই, ফ্লোরিডার জ্যাকশনভ্যালিতে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের সর্বশেষ সহযোগীদের অন্যতম এবং মার্কিন পদার্থবিদ জন হুইলারের জন্ম, মৃত্যু-১৩-০৪-২০০৮ তারিখ। ‘বø্যাক হোল’ শব্দের প্রবর্তকের মৃত্যু। ১৯১১ সালের ৩১ জুলাই, বরিশালে উপমহাদেশের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ পন্ডিত পান্নালাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২০-০৪-১৯৬০ তারিখ দিলিতে। ১৯১১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় বারডেম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের জন্ম, মৃত্যু-০৬-০৯-১৯৮৯ তারিখ। ১৯১১ সালে অবিভক্ত বাংলার মুসলমান চিত্রশিল্পীদের পথিকৃৎ প্রথম মুসলমান কার্টুনিস্ট এবং শিশু সাহিত্যিক কাজী আবুল কাসেমের জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৭-২০০৪ তারিখ। ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর, মিশরের রাজধানী কায়রোর জামালিয়া কোয়ার্টারের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী আরব ঔপন্যাসিক নাগিব মাহফুজের জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৮-২০০৬ তারিখ। তিনি ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নাগিব মাহফুজ সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান ছিলেন। ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর, ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজনানগাঁয়ে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম নারী ও মানবতাবাদী চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজীর জন্ম, মৃত্যুঃ ০৭-১১-২০০৭ তারিখ। তাঁর পৈতৃক নিবাস মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার গোপালপুর গ্রামে। ১৯১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর, হবিগঞ্জ জেলার মিরাশী গ্রামের এক জমিদার পরিবারে উপমহাদেশের গণসংগীতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম, মৃত্যু-২২-১১-১৯৮৭ তারিখ কলকাতায়। ১৯৮১ সালে যখন ঢাকায় আসেন, তখন দেখেছি হবিগঞ্জের স্মৃতিঘেরা জন্মভূমিকে দেখার জন্য তাঁর ছটফটানি।
১৯১৩ সালের ৪ ফেব্রæয়ারি, আফ্রো-আমেরিকান আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রজন্মের প্রতীক মানবাধিকার নেত্রী রোজা পার্কসের জন্ম, পরলোগমণ ২৪-১০-২০০৫ তারিখ। সবার অধিকার সমান-রোজা পার্কস। আমি গ্রেপ্তার হই ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর। বাসের সামনের দিকে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত বসার স্থান ছেড়ে না দেওয়ার জন্য। ১৯৫৫ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন এমন ছিল কৃঞ্চাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গের জন্য বাসে আলাদা বসার ছিট ছিল। ১৯১৩ সালের ১৯ জুলাই, নড়াইলের আফরা গ্রামে এক জোতদার পরিবারে তেভাগার সংগ্রামী কমরেড অমল সেনের জন্ম, মৃত্যু-১৭-০১-২০০৩ তারিখ। তিনি ১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকমা রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরোর জন্ম, মৃত্যু-০৫-০১-২০০৮ তারিখ। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে এক ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তাঁকে রাজগুরু পদে বরণ করেন। ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার গোকর্ণঘাট গ্রামে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ কালজয়ী ঔপন্যাসের লেখক (এক দরিদ্র জেলে পরিবারে) অদ্বৈত মল্ল বর্মণের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৬-০৪-১৯৫১ তারিখ। ১৯১৪ সালের ৩ এপ্রিল, ভারতের অমৃতসরে ফিল্ড মার্শাল স্যাম হরমুসজি ফ্রামজি জামশেদজি মানেকশ’র জন্ম। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় সামরিক একাডেমির (আইএমএ) প্রথম ব্যাচ থেকে তিনি কমিশন লাভ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ৭ জুন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান হন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর প্রধান ছিলেন। ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাঁকে সম্মানসূচক ফিল্ড মার্শাল উপাধি দেওয়া হয়। স্যাম বাহাদুর নামে পরিচিত মানেকশ চার দশক পর ১৯৭৩ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের অষ্টম সেনাপ্রধান হিসেবে অবসর নেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর মৃত্যু-০১-০৭-২০০৮ তারিখ। ১৯১৪ সালের ১৫ এপ্রিল, কুমিল্লা শহরের পৈত্রিক বাড়িতে ভাষাসৈনিক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি (চিরকুমার) অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের জন্ম, কুমিল্লায় মৃত্যু-২২-১১-১৯৬৯ তারিখ। ১৯১৪ সালের ১৫ মে, এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগের জন্ম, মৃত্যু-মৃত্যু-০৫-০৫-১৯৮৬ তারিখ।
১৯১৪ সালের ৮ জুলাই, কলকাতার হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) একটি বাড়িতে রাজনীতিক ও সাবেক মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্ম, মৃত্যু-১৭-০১-২০১০ তারিখ কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানীয় সময় ১১টা ৪৭ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৩০-এর দশকে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯১৪ সালে কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া মিয়াবাড়িতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের জন্ম, মৃত্যু-২৮-১১-১৯৯৯ তারিখ। ১৯১৪ সালের ১৫ জুলাই, ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরিলীর সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্জাকর্মী, পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলের উদ্ভাবক এবং বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের জন্ম, আমেরিকাতে মৃত্যু-০৯-১০-১৯৯৯ তারিখ। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশভারতের সর্বোচ্চ চাকরি আইসিএস-এ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৩৭-৪৪ সাল পর্যন্ত আই.সি.এস. অফিসার হিসেবে কুমিল্লা, পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, পটুয়াখালী, নওগাঁ ও নেত্রকোনাসহ বিভিন্ন স্থানে এসডিও এবং অন্যান্য উচ্চপদে কাজ করেন। ১৯৪৭-৫০ সাল পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে ড. জাকির হোসেন প্রতিষ্ঠিত জামিয়া মিলিয়াতে মাত্র ১০০ রুপী বেতনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালের এক ক্রান্তিলগ্নে ড. আখতার হামিদ খান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালের ২৭ মে কুমিল্লা একাডেমী (বর্তমানের বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বা বার্ড) নামে কোটবাড়িতে জন্মলাভ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে তাঁকে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তাঁকে আর বাংলাদেশে আসতে দেয়া হয়নি। ১৯৭৮-৭৯ সালে মাত্র সাত মাসের জন্য তিনি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া গ্রামে পশ্চিমবাংলার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের জন্ম, মৃত্যু-০৬-১১-২০১০ তারিখ স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টা ৫০ মিনিটে তিনি দক্ষিণ কলকাতার বেলতলা পার্কের নিজ বাসভবনে। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী ছিল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। ঢাকা শহরের নবদ্বীপ বসাক রোডেও ছিল তাঁদের বাড়ি। তাঁর বাবা সুধীর কুমার রায় ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মায়া রায়ও ব্যারিস্টার ছিলেন। সিদ্ধার্থ শংকর রায় নিঃসন্তান ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁর নানা। ১৯১৪ সালের ১৫ অক্টোবর, আফগানিস্তানের কাবুলে শেষ আফগান বাদশাহ জহীর শাহের জন্ম, ১৯৩৩ সালে তাঁর পিতা (নাদির শাহ) নিহত হওয়ার পর ১৯ বছর বয়সে জহীর শাহ সিংহাসন লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত ৪০ বছর দেশ শাসন করেন এবং শেষ আফগান বাদশাহ জহীর শাহের মৃত্যু-২৩-০৭-২০০৭ তারিখ। ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর, কিশোরগঞ্জ জেলার কেন্দুয়ায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৮-০৫-১৯৭৬ তারিখ। ১৯১৪ সালে রমেন মিত্র বাংলাদেশের নবাবগঞ্জের (বর্তমান চাপাইনবাবগঞ্জ) রামচন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর দু’জনে শুরু করেন তেভাগা আন্দোলন। পূর্ববঙ্গে কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলার অগ্রসেনানী এবং তেভাগা আন্দোলনের নেতা রমেন মিত্র(৯১) বছর বয়সে ২৮-০৬-২০০৫ তারিখ মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর, রাজশাহীর নাচোলের ‘রানি মা’ ও তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের জন্ম, মৃত্যু-১৩-১০-২০০২ সালে। অধ্যাপনা করেছেন ১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত। চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হয়েছেন। ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ইলা মিত্র ছিলেন ক্রীড়াবিদ হিসেবেও তুখোড়। ঢাকায় পুত্র রণেন মিত্র। রণেন মিত্রের জন্ম-১৯৪৮ সালে।
১৯১৫ সালের ২২ আগষ্ট, কলকাতায় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্ম, নিবেদিতপ্রাণ নাট্যব্যক্তিত্বের মৃত্যু-১৮-০৫-১৯৯৭ তারিখ কলকাতায়। ১৯১৫ সালে পাকিস্তানের পেশোয়ারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের জন্ম, মৃত্যু-১৪-০৮-১৯৮০ তারিখ। ১৯১৫ সালে ভারতীয় বাংলা সিনেমার বিখ্যাত নায়িকা ও গায়িকা কানন বালা দেবীর জন্ম, কলকাতায় মৃত্যু-১৭-০৭-১৯৯২ তারিখ। ১৯১৫ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণকারী পূর্ব-পাকিস্তানের কমান্ডার লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজী, ইন্তেকাল-০২-০২-২০০৪ তারিখ ৮৯ বছর বয়সে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে নিয়াজী ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। ১৯১৫ সালে বগুড়াতে প্রখ্যাত সাংবাদিক দৈনিক ইত্তেফাকের আসফ-উদ-দৌলা রেজার জন্ম, ঢাকায় মৃত্যু-১৪-০২-১৯৮৩ তারিখ। ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার নাগাইশ গ্রামে টাইগার গনি নামে পরিচিতি মেজর গনির জন্ম, এবং ১৯৫৭ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানীর ফ্র্যাংকপোর্টে আকস্মিকভাবে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ১৯৪১ সালে বৃটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাইওনিয়ার কোরে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রæয়ারি, তারই অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট। পাক-সরকারের বৈরিতায় ১৯৫৩ সালে তিনি সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত হন প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য। ১৯৮১ সালে মেজর গনিকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে সম্মানিত করা হয়। ১৯১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি, টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার নাগবাড়ির এক জমিদার পরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশের (১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি) রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্ম, মৃত্যুঃ ০২-০৮-১৯৮৭ তারিখ।
১৯১৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, বর্তমান পাকিস্তানের ঝিলাম জেলায় কালাগুর্জন গ্রামে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা জন্মগ্রহণ করেন এবং ০৩-০৫-২০০৫ তারিখ নয়াদিল্লীর একটি হাসপাতালে সকালে পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইষ্টার্ন কমান্ডের কমান্ডর ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কমান্ডার লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ঢাকায় লে. জেনারেল অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। অরোরা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। ১৯১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার উজানধল গ্রামে বাউলসম্রাট ও কবি শাহ আবদুল করিমের জন্ম, মৃত্যু-১২-০৯-২০০৯ তারিখ। ১৯১৬ সালের ২১ মার্চ, সানাইয়ের কিংবদন্তী ওস্তাদ ও সুর স্রষ্টা বিসমিল্লাহ খাঁ বিহারের ডুমরাও-এ পেশাদার একটি সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুবরণ করেন-২১-০৮-২০০৬ তারিখ। ১৯৫০ সালে ভারতের প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসে নয়াদিল্লীর ঐতিহাসিক সপ্তদশ শতকের লালকিল্লা থেকে শানাইয়ের ঝঙ্কার তুলে বিখ্যাত হয়ে যান। এ সঙ্গীতজ্ঞ ১৯৯১ সালে সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘ভারতরতœ’ খেতাবে ভূষিত হন। ১৯১৬ সালে বিশ্বখ্যাত ডিএনএ বিজ্ঞানী প্রফেসর উইলকিনসের জন্ম, মৃত্যু-০৮-১০-২০০৪ তারিখ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮-বছর। উইলকিনস আমৃত্যু লন্ডনের কিংস কলেজে অধ্যাপনা করছেন। ১৯১৬ সালে পাকিস্তানের আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা খান আব্দুল ওয়ালী খানের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৫-০১-২০০৬ তারিখ। ১৯১৬ সালে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে বিশ্বখ্যাত শিকারী আবদুল হামিদ ওরফে পচাব্দী গাজীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১২-১০-১৯৯৭ তারিখ। এ শিকারী সর্বোচ্চ ৫৭টি ভয়ঙ্কর মানুষখেকো রয়েল বেঙ্গল বাঘ শিকার করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিকারীদের মাঝে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের (এ দেশের প্রথম সিনেমা মুখ ও মুখোশ-১৯৫৬ সালের ৩ আগষ্ট মুক্তি পায়) পথিকৃৎ আলহাজ্ব আবদুল জব্বার খান বিক্রোমপুরে জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-১২-১৯৯৩ তারিখ। ১৯১৭ সালের ২৯ মে, যুক্তরাষ্টের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির জন্ম, আততায়ীর হাতে মৃত্যু-২২-১১-১৯৬৩ তারিখ। ১৯১৭ সালের ২৭ অক্টোবর, দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী ইস্টার্ন কেপ প্রদেশের বিজানা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ক্যান্টেলো গ্রামে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের এক উজ্জল নক্ষত্র অলিভার টাম্বোর জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৪-১৯৯৩ তারিখ স্ট্রোকে। ১৯১৭ সালের ১৭ নভেম্বর, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম, মৃত্যুঃ ৩১-১০-১৯৮৪ তারিখ নয়াদিল্লীতে দেহরক্ষীর গুলিতে। ১৯১৮ সালের ১৯ জুন, মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল গ্রামে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবি ফররুক আহমদের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৮-১০-১৯৭৪ তারিখ।
১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই, দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবতাবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম, মারা গেছেন ০৫-১২-২০১৩ তারিখ। ১৯৯০ সালের ১১ ফ্রেব্রæয়ারি তাঁর কারামুক্তির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। জীবনের ২৭ বছর জেলে কেটেছে নেলসন মেন্ডেলার। ১৯১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, বঙ্গবীর ও জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর জন্ম, মৃত্যুঃ ১৬-০২-১৯৮৪ তারিখ। ১৯১৮ সালের ১ অক্টোবর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার ভেলানগর গ্রামের বড়বাড়িতে মানে তাঁর নানাবাড়িতে (দরিকান্দি গ্রামে তাঁর বাবারবাড়ি) বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, গবেষক, বিশিষ্ট প্রতœতত্তবিদ, ইতিহাসবিদ ও পুঁথি-সাহিত্য বিশারদ, অনুবাদক সাহিত্যিক, মধ্যযুগের ইতিহাস চিন্তাবিদ, ক্রীড়া সংগঠক-বহুমাত্রিক আবুল কালাম মুহাম্মদ যাকারিয়ার জন্ম, ২৪-০২-২০১৬ তারিখ ১১-৫৫ মিনিটে শমরিতা হাসপাতালে বাধ্যর্কজনিত কারণে মারা গেছেন। ১৯১৮ সালের ১৮ অক্টোবর, ঢাকার জিন্দাবাহার লেনে উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেনের জন্ম, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জিন্দাবাহারেই ছিলেন তিনি। জিন্দাবাহার নামে তাঁর বিখ্যাত বইও আছে। ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ সরকারি আর্ট কলেজে পড়তে চলে যান। ২২-১০-২০০৮ তারিখ সোয়া সাতটায় কলকাতার বি. এম. বিড়লা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পর ১৯৭২ সালে পরিতোষ সেন স্বাধীন বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৯১৮ সালে ভিয়েনায় সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্টওয়েল্ডহেইমের জন্ম, মৃত্যু-১৪-০৬-২০০৭ তারিখ। তিনি ১৯৭২-৮২ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর, রাশিয়ার ককেসাসের কিসলোভোদস্ক শহরে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আলেকসান্দর সলঝেনিৎসিনের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৮-২০০৮ তারিখ। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে নোবেল পান। ১৯১৯ সালের ১ মে, কলকাতা শহরে আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দের জন্ম, ২৪-১০-২০১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন ভোর রাত তিনটা ৫০ মিনিটে পরপারে চলে গেলেন প্রবাদপ্রতিম সংগীতশিল্পী মান্না দে। এ ৯০(নব্বই) বছর বয়সেও গান করতে পারছে এবং স¤প্রতি বাংলাদেশে এসেছিলেন। মান্না দে গানই আমার জীবন। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা আমি শুনতে শুনতে নিজেই শিখেছিলাম। ১৯১৯ সালে ২০ জুলাই, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে, পর্বতারোহী ও এভারেষ্ট বিজয়ী স্যার এডমন্ড হিলারির জন্ম, মৃত্যু-১১-০১-২০০৮ তারিখ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকল্যান্ডের একটি হাসপাতালে। তাঁর নামে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ চূড়া এডমুন্ড হিলারির নামে করার প্রস্তাব। ১৯১৯ সালের ১১ অক্টোবর, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারের জন্ম, শহীদঃ ২১-০২-১৯৫২ তারিখ। ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর, লক্ষেèৗ শহরের এক রক্ষণশীল শিয়া মুসলিম পরিবারে নওশাদ আলীর জন্ম, উপমহাদেশের সংগীতের কিংবদন্তি নওশাদ আলীর মৃত্যুঃ ০৫-০৫-২০০৬ তারিখ। ১৯২০ সালের ১৯ জানুয়ারি, বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৯-০১-১৯৯২ তারিখ। ১৯২০ সালের ১৪ ফেব্রæয়ারি, উপমহাদেশের সঙ্গীতজ্ঞ, বাংলাদেশের প্রথম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত বারীণ মজুমদার পাবনা শহরের রাধানগর অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুঃ ০৩-১০-২০০১ তারিখ।
১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম, মৃত্যুঃ ১৫-০৮-১৯৭৫ তারিখ। ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল, ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে যাঁরা বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবিশংকর অন্যতম, জগদ্বিখ্যাত সেতারবাদক রবিশংকরের (আসল নাম রবীন্দ্র শঙ্কর চৌধুরী) জন্ম, মৃত্যু-১১-১২-২০১২ তারিখ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে আমি আমার বড় ভাই নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের সঙ্গে প্যারিস গিয়েছিলাম। ১৯২০ সালের ১৬ জুন, ফরিদপুর জেলায় বাংলা গানের ভারতীয় বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, কলকাতায় মৃত্যুঃ ২৬-০৯-১৯৮৯ তারিখ। ১৯২০ সালের ২৮ জুন, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার ছেদন্দি গ্রামে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের জন্ম, মৃত্যুঃ ১১-০৩-১৯৯১ তারিখ। ১৯২০ সালের ২৬ আগষ্ট, মুন্সীগঞ্জ শহরে এ যুগের সেরা কৌতুকশিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, কলকাতা শহরে মৃত্যু-০৪-০৩-১৯৮৩ তারিখ। ১৯২০ সালে নরসিংদীর বালিয়া গ্রামে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সোমেন চন্দের জন্ম, ঢাকার রাজপথে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও পৈশাচিকভাবে খুন করা হয়-০৮-০৩-১৯৪২ তারিখ। ১৯২০ সালে ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তোর জন্ম, মৃত্যু-২৭-০১-২০০৮ তারিখ। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৬৫ সাল থেকে ক্ষমতা দখল করে এবং ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তো ও তাঁর সেনাবাহিনী ৩২ বছর যাবত একটি লুটপাটের রাজত্ব চালিয়েছে। ১৯২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর, যশোর জেলার সদর থানার খড়কিতে কমিউনিষ্ট নেতা আবদুল হকের জন্ম, মৃত্যু-২২-১২-১৯৯৫ তারিখ। ১৯২১ সালের ২ মে, বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিত রায় (মানিক) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নির্মাণ করেছিলেন অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র ‘পথের পাঁচালি’। ১৯৫৫ সালে নিউইয়র্কে ‘পথের পাঁচালি’ প্রথম প্রদর্শিত হয়। এর কয়েক মাস পর এটি কলকাতায় মুক্তি পায়। ১৯৫৬ সালে সিনেমাটি কান চলচ্চিত্র ঊৎসবে বেস্ট হিউমেন ডকুমেন্টারীর পুরস্কার পায়। এটা বাংলার সমাজ ও গ্রামীণ জীবনকে খুবই হৃদয়গ্রাহীভাবে ফুটিয়ে তোলেন। ১৯২১ সালের ২ ডিসেম্বর, খ্যাতিমান শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানের জন্ম, মৃত্যুঃ ০২-০২-১৯৮৮ তারিখ। ১৯২২ সালের ২ জানুয়ারি, নোয়াখালী জেলায় রাজনীতিবিদ কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহার জন্ম, মৃত্যু-২৯-১১-১৯৮৭ তারিখ। ১৯২২ সালের ১৭ জানুয়ারি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে কিংবদন্তি সরোদশিল্পী (আকবর আলী আকবর খাঁ) ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ’র জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৬-২০০৯ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে নিজের প্রতিষ্ঠিত সংগীত কেন্দ্রে মারা যান। ১৯২২ সালের ১৪ এপ্রিল, কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার বর্ধিঞ্চু গ্রাম এলাহাবাদে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের জন্ম। ১৯৬৭ সালে তিনি ন্যাপ সভাপতি হন। ১৯২২ সালের ৭ নভেম্বর, ঢাকা শহরের লক্ষীবাজারস্থ বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার শাহ সাহেব বাড়ী মাতুলালয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২৩-১০-২০১৪ তারিখ পৌনে ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার প্রতীক গোলাম আযম। ১৯২২ সালে বিখ্যাত অভিনেতা দীলিপ কুমারের জন্ম। (আসল নাম ইউসুফ খাঁন)। দিলীপ কুমার ১৯৪৪ সালে জোয়ার ভাটা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এ সুপুরুষ নায়কের যাত্রা শুরু। ১৯২৩ সালে কলকাতায় ইহুদি পরিবারে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাকব-ফারজ-রাফায়েল জ্যাকবের (জে.এফ.আর.জ্যাকব) জন্ম, ১৩-০১-২০১৬ তারিখ বুধবার সকালে দিল্লির একটি সামরিক হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন। জ্যাকবের পূর্ব পুরুষেরা বাগদাদ থেকে এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লড়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে, মিয়ানমারের পরে সুমাত্রায়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে ভারতীয় বাহিনীর ঢাকা অভিযানের নেতৃত্বে দেন, তাঁর পরিকল্পনাতেই পাকিস্তান সেনবাহিনীকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটি ছিল কার্যত জ্যাকবের নিজস্ব উদ্ভাবন। জেনারেল জ্যাকব তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করতে নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল থেকেও উদ্ধৃতি দেন। নিয়াজি সেখানে বলেন, জ্যাকবই তাঁকে বø্যাকমেইল করে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বিষয়ে পাকিস্তানিরা তাঁদের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের গবেষণায় বিষ্ময়করভাবে ভারতীয় বিজয়ের জন্য কৃতিত্ব নির্দিষ্টভাবে ‘‘মেজর জেনারেল জ্যাকব’’কেই দিয়েছে। ৩১ জুলাই ১৯৭৮ সালে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। ইহুদিদের প্রতি পাকিস্তানের কোনো প্রেম নেই। পাকিস্তানিরা জানত, আমি একজন ইহুদি। ১৯২৩ সালের ১৪ মে, বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা শহরে নন্দিত চলচ্চিত্রনির্মাতা মৃণাল সেনের জন্ম। ০২-০২-২০০৫ তারিখ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য ভারতের ৫১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট এ. পি. জে. আবদুল কালাম মৃণাল সেনের কাছে দাদা সাহেব ফালকে সম্মাননা হস্তান্তর করেন। ১৯২৩ সালের ২৩ মে, বরিশাল জেলার সিদ্ধকাঠি গ্রামে আজকের দুনিয়ায় ইতিহাস সুষ্টিকারী ইতিহাসবিদ, ইতিহাসের দার্শনিক রণজিৎ গুহের জন্ম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কারণে তিনি ভারতে চলে যায়। রণজিৎ গুহকে মার্কসবাদী ধারা ইতিহাসবিদ ধরা হয়। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে ফুসফুসে ক্যান্সার নিয়ে হয়তোবা মৃত্যুর দিকেই যাচ্ছেন বাংলার এ কৃতী সন্তান। মরার আগে আরও পাঁচ বছর বাঁচতে চান, যাতে বাংলায় আরও লিখতে পারেন, যাতে একবারের জন্য হলেও তাঁর জন্মভূমি বরিশালের নদীতে কয়েক মাস ঘুরে বেড়াতে পারেন। রণজিৎ গুহকে প্রাচ্যের তত্ত¡বিদ বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে, ভারতবর্ষ তথা বংলার কৃষককে নূতন আলোয় দেখাতে পেরেছেন। তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় ২০০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর, ৪৫তম কনভোকেশনে এ ক্ষণজন্মা পন্ডিতকে ‘ডক্টর অব লিটারেচার’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে।
১৯২৩ সালের ১০ আগষ্ট, শিল্পী এস. এম. সুলতান জন্মগ্রহণ করেন নড়াইল জেলার মাছিম দিয়া গ্রামে, বরেণ্য শিল্পী মৃত্যুবরণ করেনঃ ১০-১০-১৯৯৪ তারিখ। ১৯২৪ সালের ৮ মে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার শিউড়ী মহকুমার খয়রাদিহি গ্রামে শিল্পী কলিম শরাফীর জন্ম, মৃত্যু-০২-১১-২০১০ তারিখ রাজধানীর বারিধারায় নিজ বাসভবনে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে । ১৯৫০ সালে ঢাকায় চলে এসেছিলেন কলিম শরাফী। ১৯২৪ সালে পাবনা জেলায় ভাষাসৈনিক ও কমরেড আবদুল মতিনের জন্ম। ১৯২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর, পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরের কাছে কোটলা সুলতান সিংয়ে গায়ক সুরকার মোহাম্মদ রফি জন্মগ্রহণ করেন, মুম্বাইয়ে মৃত্যুঃ ৩১-০৭-১৯৮০ তারিখ। তিনি যখন মারা যান মুম্বাইয়ে সর্বকালের সবচেয়ে বড় শোক মিছিল হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ৯ জানুয়ারি, ঝালকাঠির ৫ নম্বর কীর্তিপাশা ইউনিয়নের রুনসী গ্রামে প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিষ্ট, দৈনিক সংবাদের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য সন্তোষ গুপ্তের জন্ম, ০৬-০৮-২০০৫ তারিখ দিবাগত রাত ২-৩০ মিনিটে বারডেম হাসপাতালে পরলোকগমন। ১৯২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ডে কমপিউটার মাউসের জনক ডগলাস অ্যাঙ্গেলবার্টের জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৭-২০১৩ তারিখ। ১৯২৫ সালের ২৪ মার্চ, যশোরে মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামানের (বীর-উত্তম) জন্ম, মৃত্যু-০৬-০৫-২০১১ তারিখ। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভিতে যোগ দেন। ১৯২৫ সালের ৯ এপ্রিল, কেন্দ্রীয় কচি-কাচার মেলার প্রতিষ্ঠাতা ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের জন্ম, তিনি মারা যান ০৩-১২-১৯৯৯ তারিখ। ১৯২৫ সালের ৯ জুলাই, ভারতের বেঙ্গালুরুতে সফল চলচ্চিত্র নির্মাতা গুরু দত্তের জন্ম, মৃত্যু-১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর, মুম্বাইয়ে। ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সাবেক অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের জন্ম, মৃত্যু-১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর, কেন্দ্রীয় কারাগারে। ১৯২৫ সালের ২৯ নভেম্বর, ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলার মাতুভূঁইয়া ইউনিয়নের লক্ষণপুর গ্রামে ভাষা শহীদ আবদুস সালামের জন্ম, শহীদঃ ২১-০২-১৯৫২ তারিখ। ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর, এ ঢাকা শহরেই দুটি ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। তাঁদেরই একজন পরবর্তী জীবনে বাংলার শিল্পনিষ্ঠ ও স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক, অন্যজন সাত মিনিটের ছোট বোন। অত্যন্ত কৃতী পরিবারের সবচেয়ে অকৃতী অধম সেই যমজ বোনই আমি-প্রতীতি। স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের কলকাতায় মৃত্যু-০৬-০২-১৯৭৬ তারিখ। ঋত্বিক কিন্তু ঢাকাতেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে মা-বাবাকে নিয়ে দাদারা কলকাতায় চলে যান। ঋত্বিক এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু সবার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। ফলে তাকেও যেতে হলো। ঋত্বিক কুমার ঘটকরা নয় ভাই-বোনের মধ্যে সবার কনিষ্ঠ ঋত্বিক কুমার ঘটক ও প্রতীতি দেবী। প্রতীতি দেবীর স্মৃতিচারণায় ভাই ঋত্বিক ঘটক। প্রতীতি দেবী ঢাকায়ই থাকেন।
১৯২৫ সালে ভারতের শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী ও পারমাণবিক কর্মসূচীর জনক রাজা রামান্নার জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৯-২০০৪ তারিখ। ১৯২৫ সালে ব্রিটেনের ম্যানচেস্টারে বিজ্ঞানী রবার্ট এডওয়ার্ডসের জন্ম। ব্রিটিশ অধ্যাপক রবার্ট এডওয়ার্ডসের হাতেই ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই, জন্ম হয় বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব শিশু লুইস ব্রাউনের। তাঁর এ সফলতায় বিশ্বের লাখ লাখ বন্ধ্যা দম্পতি আইডিএফ প্রযুক্তির মাধ্যমে সন্তান লাভ করছে। ১৯২৫ সালে ভারতের শিলংয়ে স্কটিশ বিজ্ঞানী জন শেফার্ড-ব্যারনের জন্ম, মৃত্যু-১৫-০৫-২০১০ তারিখ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৪ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের ইনভারনেস শহরের একটি হাসপাতালে। তিনি এটিএমের উদ্ভাবক জন শেফার্ড-ব্যারন অটোমেটেড টেলর মেশিন (এটিএম)-এর উদ্ভাবক জন শেফার্ড-ব্যারন মারা গেছেন। ব্যাংকিং খাতে টাকা-পয়সা তোলার ক্ষেত্রে এটিএমের ধারণা প্রথম জন শেফার্ড-ব্যারনের ভাবনাতেই আসে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে লন্ডনে প্রথম এটিএম বসানো হয়। জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানে ‘অন দি বাসেস’ থেকে প্রচারের আলোয় আসা অভিনেতা রেগ ভার্নি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি সেই এটিএম থেকে টাকা তুলেছিলেন। পিটিআই। ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি, বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ঢাকায়। লেখার পাশাপাশি দলিত ও আদিবাসী জনজাতিগুলোর কাছে গিয়ে তাদের নিয়ে কাজ করে তিনি একজন প্রতিবাদী লড়াকু কণ্ঠস্বর হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। ১৯২৬ সালে বগুড়া জেলায় আলোর দিশারী বাংলাদেশের মহিলা ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রদূত ছিলেন রাবেয়া খাতুন তালুকদারের জন্ম, মৃত্যু-২০০৯ সালে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন রাবেয়া খাতুন তালুকদার। ১৯২৬ সালে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর জন্ম, তাঁর ফাঁসি হয়-০৪-০৪-১৯৭৯ তারিখ। ১৯২৬ সালে পূর্ববঙ্গের বলিশাল জেলায় ইতিহাসের পন্ডিত অধ্যাপক তপন রায় চৌধুরীর জন্ম। তবে তাঁর মুখ্য কাজের ক্ষেত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। মোগল আমলের ও ব্রিটিশ উপনিবেশের বাংলা তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট, কলকাতায় যে কুৎসিত দাঙ্গার ঘটনাটা ঘটল, ‘আমি এখনো দাঙ্গার ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছি’।
১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি মহানায়ক অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় (উত্তম কুমারের) জন্ম, মৃত্যু-২৪-০৭-১৯৮০ তারিখ। ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, ভারতের আসাম রাজ্যে গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকার জন্ম, শনিবার স্থানীয় সময় বিকেল চারটা ৩৭ মিনিটে মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন ধিরুভাই আম্বানি হাসপাতালে এই মানবদরদি শিল্পী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন-০৫-১১-২০১১ তারিখ। ‘যাযাবরের’ চিরপ্রস্থান। তিনি আসামী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় গান করতেন। ১৯২৬ সালের ১৩ আগষ্ট, কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম। তিনি ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি, কিউবায় কমিউনিষ্ট বিল্পবের মাধ্যমে কিউবার ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৬ সালের ১৬ আগষ্ট, বিপ্লবী কিশোর কবি সুকান্ত কলকাতা শহরে তাঁর নানাবাড়ি জন্মগ্রহণ করেন; মৃত্যু-১৩-০৫-১৯৪৭ তারিখ কলকাতা শহরে। ফরিদপুর জেলায় তাঁর বাবারবাড়ি। ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি, নোয়াখালী জেলার সেনবাগে বইয়ের মানুষ চিত্তরঞ্জন সাহার জন্ম, মৃত্যু-২৬-১২-২০০৭ তারিখ। চিত্তরঞ্জন সাহাই পুথিঘর লাইব্রেরীর মালিক এবং প্রথম বাংলা একাডেমীতে একুশে ফেব্রæয়ারিতে বইয়ের দেকান দেন। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে ভাষাসৈনিক শহীদ আবুল বরকতের জন্ম, মৃত্যু-২১-০২-১৯৫২ তারিখ ঢাকায়। ১৯২৭ সালের ১৮ জুলাই, ভারতের রাজস্থানের ঝুনঝুন জেলার লুনা গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সংগীত পরিবারে উপমহাদেশের ধ্রæপদ সংগীত ও গজলের ধ্রæবতারা মেহদি হাসানের জন্ম, পাকিস্তানের করাচিতে মৃত্যু-১৩-০৬-২০১২ তারিখ বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ২২ মিনিটে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পরিবারসহ পাকিস্তানের সহিওয়াল জেলার ছিচা ওয়াতনি এলাকায় থিতু হন তাঁরা। ১৯৫৭ সালে ঠুমরি গায়ক হিসেবে পাকিস্তান বেতারে গাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর থেকে আর্থিক সংকট কাটতে থাকে মেহদি হাসানের। ১৯২৮ সালের ২০ মার্চ, কুচবিহারে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের জন্ম। ১৯২৮ সালের ১৪ জুন, আর্জেন্টিনার রোমারি শহরের স্যান্টাক্লারা এলাকায় লাতিন আমেরিকার বিপ্ললী নেতা ও কিউবা বিপ্লবের অন্যতম নায়ক চে গুয়েভারার জন্ম, ১৯৬৭ সালের ৮ অক্টোবর দুজন সহযোদ্ধাসহ বন্দী হন আহত চে। পরে তাকে ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর, বলিবিয়ার এক সার্জেন্ট মারিয়ো তেরান চে গুয়েভারাকে বলিভিয়ার জঙ্গলে কাছ থেকে গুলী করে হত্যা করেন। ১৯৩৭ সালে স্পেনিশ গণযুদ্ধের সময় চে পড়ছেন প্রাইমারী স্কুলে, থার্ড গ্রেডে। ১৯৪৭ সালে আর্জেন্টিনার কমিউনিষ্ট সংঘের তরুণ কর্মী বারতা গিলদা তিতার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মার্কসবাদী দর্শনের নানামুখী আলোচনায় ঝুঁকে পড়েন তিনি। ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি, ফিদেল-চের নেতৃত্বে বিপ্লব সমপন্ন হয় কিউবায়। ১৯২৮ সালের ১১ ডিসেম্বর, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার রামকান্তপুর গ্রামে চলচ্চিত্রকার, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ও অভিনেতা খান আতাউর রহমান খানের জন্ম, মৃত্যু-০১-১২-১৯৯৭ তারিখ। তিনি চলচ্চিত্র অঙ্গনের এক ব্যতিক্রমী পুরুষ। ১৯২৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের, শিকাগো শহরে মার্টিন কুপারের জন্ম। হাতে বহনযোগ্য মোবাইল ফোনের উদ্ভাবক। ৩ এপ্রিল ১৯৭৩, তিনি মোবাইল ফোনে প্রথম কলটি করেন।১৯২৯ সালের ২১ জানুয়ারি, গায়ক, নায়ক ও পরিচালক কিশোর কুমারের জন্ম; মৃত্যুঃ ১৯-১০-১৯৮৬ তারিখ। ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ, কলকাতায় কিংবদন্তী নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক উৎপল দত্তের জন্ম, মৃত্যু-১৯-০৮-১৯৯৩ তারিখ কলকাতায়। তাঁদের পূর্ব-পুরুষের পিতৃভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর সংলগ্ন গৌতম পাড়া গ্রামের দত্ত পরিবারে। থিয়েটার এবং সিনেমা দুটো মাধ্যমেই তিনি বিচরণ করেছেন দাপটের সঙ্গে। শুরুটা মঞ্চ দিয়েই। ‘‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’’। ১৯২৯ সালের ৩ এপ্রিল, ঢাকার শিবচরে স্থপতি, বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য প্রকৌশলী স্যার ড. ফজলুর রহমান খানের জন্ম, মৃত্যু-১৯৮২ সালে। ১৯৭৪ সালে নির্মিত-১১০ তলার সিয়ার্স টাওয়ারটি ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচ টাওয়ার। উঁচু ভবনের নকশা তৈরির এই পথিকৎকে বলা হয় স্থাপত্য প্রকৌশলের আইনস্টাইন। ১৯২৯ সালের ১ জুন, ভারতের পশ্চিম বাংলার কলকাতা শহরে চলচিত্র তারকা ও হিন্দি সিনেমার নায়িকা নার্গিসের জন্ম, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ-১৯৮৬ সালে। ১৯২৯ সালের ৯ আগষ্ট, বিশিষ্ট সাংবাদিক চরমপত্র খ্যাত, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষাসৈনিক এম. আর. আখতার মুকুলের জন্ম, মৃত্যু-২৬-০৬-২০০৪ তারিখ বারডেম হাসপাতালে। ১৯২৯ সালের ২৪ আগষ্ট, কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত, মৃত্যু-১১-১১-২০০৪ তারিখ বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৮.৩০ টায়। ইয়াসির আরাফাত-যার পুরো নাম মোহাম্মদ আবদেন রউফ আরাফাত ওরফে কুদবা আল হোসাইনী। ইয়াসির আরাফাত ১৯৬৪ সাল থেকে ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, ভারতের ইন্দোরে বিখ্যাত গায়িকা ও জীবিত সঙ্গীত কিংবদন্তী লতা মুঙ্গেসকরের জন্ম। লতা তাঁর ছয় দশাধিক বছরের ক্যারিয়ারে ৫০,০০০ হাজারেরও বেশী গান গেয়েছেন এবং এখনও গেয়ে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্র বিশ্বে বিশেষ অবদানের জন্য ফরাসী সরকার সর্বোচ্চ সম্মাননা দেন। ১৯২৯ সালে মার্কিন বিপ্লবী মার্টির লুথার কিং জুনিয়রের জন্ম, মৃত্যু-১৯৬৮ সালে। ১৯৩০ সালের ২১ ফেব্রæয়ারি, অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার বনগাঁ কবি গোবিন্দ হালদারের জন্ম, তিনি বর্তমানে কলকাতায় অবসর জীবন কাটানো অবস্থায় কলকাতার মানিকতলার জিতেন্দ্র নাথ রায় হাসপাতালে মারা গেছেন-১৭-০১-২০১৫ তারিখ। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না এবং আরো কয়েকটি গানের লেখক ছিলেন।
১৯৩০ সালে স্বরূপকাঠিতে চিত্তরঞ্জন সুতারের জন্ম, মৃত্যুঃ ২৯-১১-২০০২ তারিখ দিল্লীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমণ করেন ৭২ বছর বয়সে। ১৯৫৮ সালে তিনি ভারতের লোক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের সাথে কাজ করেছেন। ১৯৭৩ সালে তিনি তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের স্বরূপকাঠি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের আগষ্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার আগেই তিনি কলকাতায় চলে যান। চিত্তরঞ্জন সুতার উনিই বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি দুই দেশে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল, বাংলাদেশের (পাবনা জেলার) বর্তমান সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানার সলক ইউনিয়নের ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে নানাবাড়িতে পশ্চিমবাংলার বাংলা সিনেমার কিংবদন্তি মহানায়িকা (রমা দাশগুপ্ত কৃষ্ণা) সূচিত্রা সেনের জন্ম। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিল পাবনা শহরের দিলালপুর মহল্লায়। সূচিত্রা সেন প্রথম অভিনয় করেন ১৯৫২ সালে আর সর্বশেষ অভিনয় করেছেন ১৯৭৮ সালে। ১৯৮০ সালে উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর খুব অল্প সময়ের জন্য মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে দু-এক ঝলক, ভরত মহারাজের মৃত্যুর পর মুহূর্তের উপস্থিতি এবং ১৯৯৫ সালে একবার ভোটার পরিচয়পত্রের ছবি তুলতে সামনে আসেন। ২০০৮ সালে অসুস্থ হয়ে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি হলে লুকিয়ে এক ফটোসাংবাদিক সুচিত্রা সেনের ছবি তোলেন। কেন এই স্বেচ্ছানির্বাসন? এমন প্রশ্নের জবাবে সূচিত্রা সেন ঘনিষ্ঠজনদের নাকি বলেন, ‘একসময় বাসনার রূপ ছিলাম, এখন তাই সরিয়ে নিয়েছি নিজেকে, ওই চোখগুলো থেকে অনেক দূরে। ১৯৩১ সালের ২২ জুলাই, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে পল্লী গানের পাখি আবদুল আলীমের জন্ম, মৃত্যুঃ ০৫-০৮-১৯৭৪ তারিখ। ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর, ভারতের তামিলনাড়–র প্রত্যন্ত এক গ্রামে ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী (এ) আবুল (পি) পাকির (জে) জয়নাল আবেদীন আবদুল কালামের জন্ম, মৃত্যু-২৭-০৭-২০১৫ তারিখ। ঠিক করো, কীভাবে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখবে। উনি ভারতের ১১নং রাষ্টপ্রতি ছিলেন। ১৯৩২ সালের ২৭ ফেব্রæয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত হলিউড কিংবদন্তি অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের জন্ম, মৃত্যু-২৩-০৩-২০১১ তারিখ লস অ্যাঞ্জেলেসের সিডার-সিনাই হাসপাতালে। আটবার বিয়ে করেছেন এলিজাবেথ টেলর এবং সাত স্বামী। ১০ বছর বয়সে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। ১০০শত কোটি ডলারের মালিক তিনি এবং বিশ্বের ১৪ জন নারীর মধ্যে একজন। ১৯৩২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রভাবশালী কেনেডি পরিবারের সন্তান সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির জন্ম, মৃত্যু-২৬-০৮-২০০৯ তারিখ। ১৯৭২ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রæয়ারি বাংলাদেশে সফরে আসে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সামনের বট গাছটি ১৪ ফেব্রæয়ারি তিনি লাগিয়েছিলেন, কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আগের বট গাছটি কেটে ফেলেছে পাকিস্তানীরা। জন. এফ. কেনেডির ছোট ভাই এডওয়ার্ড কেনেডি।
১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর, কলকাতায় জন্ম হয় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের। অমর্ত্য সেনের প্রথম স্কুল ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয় তারপর কলকাতায় শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী। ১৯৯৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি বলেন শিক্ষা সবকিছু বদলে দেয়। তাঁর বাবারবাড়ি বাংলাদেশের মানিগঞ্জে এবং নানাবাড়ি বিক্রমপুরে। ১৯৪৯ সালে মেট্রিক, ১৯৫১ সালে আই. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি ভর্তি হন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৩৩ সালের ১৯ নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্বনামধন্য টেলিভিশন ও রেডিও ব্যক্তিত্ব ল্যারি কিং-এর জন্ম। ১৯৩৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর, বরিশাল জেলায় আলতাফ মাহমুদের জন্ম, মৃত্যু-৩০-০৮-১৯৭১ তারিখ পাকবাহিনীর হাতে। আমরা কি ভুলিতে পারি…। ১৯৩৪ সালের ১৩ জুন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে লিউনার্ড ক্লেইনরকের জন্ম। ১৯৬৯ সালের ২৯ অক্টোবর, অ্যাপ্রানেটের মাধ্যমে প্রথম এক কমপিউটার থেকে আরেক কমপিউটারে উপাত্ত পাঠাতে সক্ষম হন। জন্ম হয় ইন্টারনেটের। ১৯৩৪ সালের ১৭ ফেবুয়ারি, কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের টামনী ভূঁইয়াপাড়া গ্রামের ভূঁইয়াবাড়িতে জনমুক্তি পার্টির সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাজমূল হোসেন ভূঁইয়ার (মাহফ‚জ ভাইয়ের) জন্ম, ১০-০২-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭টার সময় মারা গেছেন ঢাকার ধানমন্ডিতে। ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মাইজপাড়া গ্রামে (বর্তমান মাদারীপুর) বাংলা সাহিত্যের দিকপাল, কবি ও ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (মাদারীপুর জেলার আমগাঁও গ্রামে তাঁর বাবারবাড়ি) জন্মগ্রহণ করেন, গত সোমবার স্থানীয় সময় দিবাগত রাত দুইটা ৫ মিনিটে ২৩-১০-২০১২ তারিখ দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের বাড়িতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
১৯৩৪ সালে ভারতের পশ্চিমবাংলার নদীয়ার শান্তিপুরে কিংবদন্তি বাচিকশিল্পী ও আকাশবাণীর সংবাদপাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, কলকাতায় নিজ বাড়িতে পরলোকগমন করেন-০২-০৬-২০১১ তারিখ। ১৯৬০ সালে তিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে যোগ দেন। ১৯৭১ সাালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল আকাশবাণী আর বিবিসি রেডিও। এ আকাশবাণীতেই তাঁর পরিবেশনায় সংবাদ, সংবাদ-সমীক্ষা ও সংবাদ-পরিক্রমা ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। ১৯৩৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, রোমে এক দরিদ্র পরিবারে সোফিয়া লোরেনের জন্ম। মাত্র ১৪ বছর বয়সে এক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জয়ের মাধ্যমে তার খ্যাতির সূচনা হয়। ১৬ বছর বয়সে তিনি ‘কু ভাদিস’ নামের একটি চলচ্চিত্রে ছোট চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর, বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া গ্রামের জমিদার বংশ চৌধুরীবাড়িতে সাংবাদিক ও কলামিষ্ট আবদুল গাফফার চৌধুরীর জন্ম। ১৯৩৫ সালের ১৯ জানুয়ারি, নদিয়ার কৃষ্ণনগরে টালিউডের আদর্শবান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপ্যাধায়ের জন্ম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে পড়াশোনা করেন। ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসারের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে। তাঁর বাবারবাড়ি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কয়া গ্রামে। ১৯৩৫ সালের ৯ ফেব্রæয়ারি, নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার সোনাপুর গ্রামে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ মামলার আসামী শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের জন্ম, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গুলিতে মৃত্যু-১৫-০২-১৯৬৯ তারিখ। ১৯৩৫ সালের ১৯ জুলাই, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সফল চরিত্র মাসুদ রানার জনক বিপুল জনপ্রিয় সেবা প্রকাশনীর প্রাণপুরুষ কাজী আনোয়ার হোসেনের জন্ম। ৪০০-এর ঘর পার করেছে মাসুদ রানা সিরিজ। তার স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেন। ১৯৩৫ সালের ৬ জুন, নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত তিব্বতের আধ্যাত্বিক নেতা দালাই লামার জন্ম। ১৯৫৯ সালে তিব্বত থেকে চীন সরকার আধ্যাত্বিক নেতা দালাই লামাকে নির্বাসিত করে। ১৯৩৫ সালের ১৯ আগষ্ট, যুক্তরাষ্ট্রে নাসার বিজ্ঞানী ও নভোচারী ষ্টোরি মাসগ্রেভের জন্ম। নাসার ছয়টি স্পেস শাটলের সব কয়টিতেই চড়েছেন তিনি। মহাশূন্যে কাটিয়েছেন মোট ১২০০ ঘন্টা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাসগ্রেভ। ১৯৩৫ সালের ২৪ অক্টোবর, কলকাতার টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিবিসির সাংবাদিক স্যার মার্ক টালির জন্ম। ১৯৬৪ সালে বিবিসিতে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ভারত সংবাদদাতা হিসেবে দিল্লিতে আসেন। বিবিসির ৩০ বছরের চাকরিজীবনে তিনি ২০ বছর ছিলেন দিল্লি ব্যুরোপ্রধান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় স্যার মার্ক টালি ছিলেন বিবিসির দক্ষিণ এশীয় বিষয়ক ভাষ্যকার। যিনি পরে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দিল্লীতে বিবিসির দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৪ সালে বিবিসি ত্যাগ করার পর থেকে মার্ক টালি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। ৪০ বছর সাংবাদিকতা করার পর অবসরে যান, তিনি ভারতের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও ২০০২ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাইট উপাধি পান। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাঁকে ‘ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার’ সম্মাননা প্রদান করেন। ২০১১ সালের ৮ ডিসেম্বর, তিনি ভারতের ইনস্টিটিউট অব স্মল এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে এই বক্তব্য দেন। ‘‘ক্ষুদ্র উদ্যোগেই হোক শুরু’’। ১৯৩৫ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার আরসোলা গ্রামে ৬(ছয়) বার ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাসের জন্ম, মৃত্যু-০১-০৬-১৯৯৮ তারিখ। ১৯৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে প্রণব কুমার মুখার্জির জন্ম। ষাটের দশকে বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজনীতিতে উঠে আসেন তিনি। যদিও ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি লোকসভায় একবারও জিততে পারেননি। রাজ্যসভায় তিনি কংগ্রেস থেকে বেশ কয়েকবার নির্বাচিত হন। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা নেয়া-এ রাজনীতিক অর্থনীতিও যে ভালো বোঝেন, তার প্রমাণ ১৯৮৪ সালে বিখ্যাত ইউরোমানি সাময়িকীর জরিপে বিশ্বের সেরা অর্থমন্ত্রী বিবেচিত হওয়া। ২০০৯ সালেও কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রীর পদ ছাড়লেন। ১৯ জুলাই, ভারতের ১৩তম রাষ্ট্রপতি হয়েছেন প্রণব কুমার মুখার্জি। ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৮৮২ জন ভোটার দেন। প্রথম বাঙালী রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির প্রয়োজন ছিল পাঁচ লাখ ৪৯ হাজার ৪৪২ ভোট তিনি পেয়েছেন সাত লাখ ১৩ হাজার ৭৬৩ ভোট পেয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (ইউপিএ) সরকারের ‘ক্রাইসিস ম্যানেজার’ প্রণব মুখার্জি। এতে প্রণব ৬৯ শতাংশ ভোট পেয়ে বিরোধী জোট জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার (এনডিএ) প্রার্থী সাংমাকে পরাজিত করেন। তাঁর প্রতিপক্ষ পূর্ণ অ্যাজিটক (পি.এ.) সাংমার পক্ষে ভোটের মূল্যায়ন তিন লাখ ১৫ হাজার ৯৮৭। ২৫ জুলাই, ২০১২ তারিখ ১১টা ৩০ মিনিটে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে রাইসিনা হিলসের রাষ্ট্রপতির ভবনে শুরু হচ্ছে প্রণবের নতুন জীবন। নয়াদিল্লীর ঐতিহাসিক দিল্লি গেটের অপর প্রান্তে রাইসিনা হিলস-এ অবস্থিত এই রাষ্ট্রপতি ভবন। ৩৩০ একর জমির ওপর এই রাষ্ট্রপতি ভবন। ঐতিহাসিক ভবনটি ব্রিটিশ আমলে ছিল ভাইসরয়দের বাসভবন। ভবনের বিশালত্ব এবং শিল্পসৌন্দর্য একে বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রাসাদের মর্যাদা দিয়েছে। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে এই প্রাসাদটি গড়ে ওঠে ব্রিটিশ স্থপতি স্যার এডুইন লিউটেনসের পরিকল্পনায়। চারতলার এই প্রাসাদে রয়েছে ৩৪০টি কক্ষ। এখানে মোগল, হিন্দু, বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য স্থাপত্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভবনের মূল গম্বুজটি বৌদ্ধ আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে আর অলিন্দ হিন্দু মন্দিরের আদলে। রয়েছে দরবার হল, যা অশোকা হল নামে পরিচিত। আছে ১৩০ হেক্টর জায়গাজুড়ে মোগল উদ্যান।
১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি, বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের জন্ম, মৃত্যু ৩০-০৫-১৯৮১ তারিখ। ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, নড়াইল জেলার মহেষখোলা গ্রামে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখের জন্ম, মৃত্যু-০৫-০৯-১৯৭১ তারিখ যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার গোয়ালহাটি গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হন। ১৯৩৬ সালের ৩১ মার্চ, ভূপাল, মধ্যপ্রদেশে ড. আবদুল কাদির খানের জন্ম। ড. আবদুল কাদির খান, পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক। কিন্তু তার প্রকৃত জন্ম তারিখ ২৭ এপ্রিল, ১৯৩৬ সাল। ১৯৩৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর, সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় আগা খান প্রিন্স করিম আল-হোসাইনির জন্ম। ২০ বছর বয়সে চতুর্থ আগা খান হিসেবে নিজারি ইসমাইলিয়াদের আধ্যাত্মিক নেতার দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর পূর্বসূরি হলেন দাদা তৃতীয় আগা খান স্যার সুলতান মুহাম্মদ শাহ আগা খান। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রিন্স করিম আল-হোসাইনি ইসমাইলিয়া স¤প্রদায়ের ৪৯তম ইমাম। প্রিন্স আলী খান তাঁর বাবা, মা প্রিন্সেস তাজউদ্দৌলা আলী খান। ১৮৪৩ সালে ইরান থেকে প্রথম আগা খান আগা হাসান আলী ভারতে চলে আসেন। ১৮৭৭ সালে আগা খান খেতাবটি ব্রিটিশরাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। ইসমাইলিয়া স¤প্রদায়ের ৪৬তম ইমাম আগা হাসান আলী শাহ প্রথম ‘‘আগা খান’’ খেতাব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমনে তৎকালীন আগা খান সহযোগিতার জন্য আসে এ স্বীকৃতি। দ্বিতীয় আগা খান মাত্র চার বছর নিজ স¤প্রদায়ের ইমামতি করতে পেরেছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি মারা যান। আগা খানের আয়ের অন্যতম উৎস বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশে বসবাসরত ইসমাইলি স¤প্রদায়ের ১.৫০(এক কোটি পঁঞ্চশ লক্ষ) লোক। প্রতিবছর তাঁরা ইমামের তহবিলে অর্থ জোগান। সব মিলিয়ে সারা বিশ্বে ৯০টির বেশি ব্যবসা রয়েছে তাঁর। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে ৩৬ হাজার কর্মী। ইসমাইলিয়া স¤প্রদায়ের বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফাতিমিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাস। মহানবী হজরত মোহাম্মদ(স.) মেয়ে হজরত ফাতিমিদ(রা.)-এর নাম থেকে ফাতিমিদ নামের উৎপত্তি। সেই সূত্রে ইসমাইলিরা সরাসরি মহানবীর বংশধর। ২০০৮ সালে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ২০ একর জমির ওপর গড়ে তোলা হবে আগা খান একাডেমি। এতে ব্যয় হবে ৫(পাঁচ) কোটি ডলার। ১৯৩৭ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার রালেগাঁও সিদ্ধিতে গান্ধীবাদী সমাজকর্মী আন্না হাজারের জন্ম। তিন দাবি মেনে নিল পার্লামেন্ট। এক-কেন্দ্র ও রাজ্য পর্যায়ে লোকপাল প্রবর্তন, দুই-কনিষ্ঠ সরকারি আমলারা এর জবাবদিহির আওতায় থাকবেন এবং তিন-সব সরকারি দপ্তরের সামনে ওই দপ্তরের দায়িত্ব উলেখ করে ‘সিটিজেন চার্টার’ টাঙানো থাকবে। দুর্নীতিবিরোধী লোকপাল বিল আন্দোলনে বিজয়ী হলেন ১২ দিন ধরে অনশনের পর ২৭-০৮-২০১১ তারিখ নয়াদিল্লির রামলীলা ময়দানে আন্না হাজারে।
১৯৩৭ সালের ২৮ এপ্রিল, ইরাকের মরু এলাকা তিকরিতের আল আওজা গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে সাদ্দাম হোসেনের জন্ম, ফাঁসিতে মৃত্যু-৩০-১২-২০০৬ তারিখ। সাদ্দাম হোসেন বন্দী ১৪-১২-২০০৩ তারিখঃ খামার বাড়ির গর্তে লুকিয়েছিলেন তিনি-ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় নিশ্চিত-বিরোধীদের উল্লাস। ১৯৩৮ সালের ৮ এপ্রিল, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের জন্ম। তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ২০০১ সালে। ১৯৩৮ সালের ১৪ নভেম্বর, ভারতের আসামের বদরপুরে ময়মনসিংহে সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল আবু তাহেরের জন্ম, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসীতে মৃত্যু-২১-০৭-১৯৭৬ তারিখ। তাঁর পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার কাজলা গ্রামে। সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর, তিনি সিপাহি-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর, গ্রেপ্তার হন। (সূত্র ঃ বাংলাপিডিয়া)। ১৯৩৯ সালের ২৪ অক্টোবর, ফটোসাংবাদিক রশীদ তালুকদারের জন্ম। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ‘পাইওনিয়ার ফটোগ্রাফার অ্যাওয়ার্ড’-২০১০ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর, দোনা-দনদিনহোর গরিব সংসারে ঘর আলো করে ব্রাজিল দলের বিশ্বকাপ ৩ বার চ্যাম্পিয়ন (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) ফুটবলার পেলের (এডসন) জন্ম। ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরতলীর বশিরহাটে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্ম। ১৯৪০ সালের ২৭ নভেম্বর, প্রখ্যাত মার্শাল আর্টের প্রবাল পুরুষ ও কুংফু কিংবদন্তী ব্রæস লী’র সানফ্রানসিসকোতে জন্ম, ১৯৭৩ সালের ২১ জুলাই এক ধরনের ষ্ট্রোকে মারা যান। ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি শহরে পার্সোনাল কম্পিউটারের জনক হেনরি এডওয়ার্ড রবার্টসের জন্ম, মৃত্যু-০১-০৪-২০১০ তারিখ। ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর, (তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামে) পুরাতন ঢাকার ১০৯, আগাসাদেক রোডের বাসায় বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের জন্ম, ১৯৭১ সালের ২১ আগষ্ট, করাচীর ওই মাশরুর বিমান ঘাঁটি থেকেই একটি টি-৩৩ বিমান নিয়ে উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পাকিস্তানী পাইলট রাশেদ মিনহাজ। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান মিনহাজকে ক্লোরফরম প্রয়োগে কাবু করে বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন এবং আকাশে উঠে যান। ইতিমধ্যে মিনহাজ সংজ্ঞা ফিরে পেলে বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দু’জনের মধ্যে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। ফলশ্রæতিতে বিমানটি সিন্দু প্রদেশের থাট্টা এলাকার জিন্দা নামক একটি গ্রামে বিমানটি বালিয়ারিতে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ২৫-০৬-২০০৬ তারিখ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মাতৃভূমিতেই ঠাঁই হলো বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের ৩৫ বছর পর তাঁর দেহবশেষ বাংলাদেশে পুনঃদাপনসম্পন্ন। ১৯৪১ সালে রংপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর গ্রামে জেনারেল (অব.) মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের জন্ম, মৃত্যু-০৩-০৮-২০০৮ তারিখ। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম জেনারেল।
১৯৪২ সালের ৮ জনুয়ারি, যেদিন ইংল্যান্ডে পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংকের জন্ম, ঠিক এর তিনশত বছর আগে ইতালিতে মারা যান গ্যালিলিও গ্যালিলি। ২১ বছর বয়সে হকিং আক্রান্ত হন সøায়ুরোগে, যা এএলএস ডিডিজ নামে পরিচিত। ২০০৯ সালের দিকে এসে তিনি পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছেন। তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে এ যাবত এএলএস রোগে আক্রান্ত কেউ বেঁচে আছেন, এমন কোনো রেকর্ড নেই। স্টিফেন হকিং ঃ রোগ তাঁর চলৎশক্তি কেড়ে নিলেও তাঁর মেধা, মনন, দৃষ্টিকে কেড়ে নিতে পারেনি। ১৯৪২ সালের ১৭ জানুয়ারি, লুইসভিল, কেনটাকি, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-সেরা বক্সার ও কিংবদন্তির নায়ক মোহাম্মদ আলীর জন্ম, ০৪-০৬-২০১৬ তারিখ মারা গেছেন। ১৯৬০ সালের ২৯ অক্টোবর রোম অলিম্পিকে জেতেন লাইট হেভিওয়েট স্বর্ণপদক। অপেশাদার জীবনে ১০০ জয়ের বিপরীতে তাঁর পরাজয় মোটে পাঁচটি। কিংবদন্তির নায়ক মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা খেতাব অর্জণ করেণ ২৯-১০-১৯৭৪ তারিখ। ১৯৮১ সালে শেষ লড়াইয়ে নামেন আলী। হার মানেন ট্রেভর বারবিকের কাছে। পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ-জীবনে এ শেষ হারসহ মোট পাঁচবার হারলেন আলী, বিপরীতে জিতেছেন ৫৬ বার। নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ আলী ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় আফ্রো-আমেরিকান, বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত পাঁচটি চেহারার একটি। ১৯৪২ সালের ১১ অক্টোবর, বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের জন্ম। অমিতাভ ১৯৬৯ সালে প্রথম ‘সাত হিন্দুস্থানী’ ছবির মাধ্যমে অভিনয় শুরু করে। ২০০৪ সালের ৬৩তম জন্মদিনে ২ কি. মি. দীর্ঘ বার্থ ডে কার্ডে ঐ কোম্পানীর প্রায় ছয় লাখ খুচরা বিক্রেতার স্বাক্ষর থাকছে। সহস্রাব্দের সেরা অভিনেতার ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ‘‘লিজিয়ন ডি অনার’’ খেতাব অর্জন। ১৪০টিরও বেশী পূর্ণ দৈর্ঘ্য সিনেমায় অভিনয় করেছেন এবং এটা তাঁর ৬০তম পুরস্কার। ১৯৪৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি, লিভারপুলের ওয়েভারটির গায়ে গা ঠেকিয়ে থাকা কয়েকটি বাড়ির একটি ১২ আর্নল্ড গ্রোভ। এ বাড়িতেই জন্ম নিলেন বাংলার বন্ধু জর্জ হ্যারিসন, মৃত্যু-২৯-১১-২০০৮ তারিখ। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-বাংলাদেশ জর্জ হ্যারিসন। ১৯৪৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, ফরিদপুরের রাজবাড়িতে জন্ম (বাবার নিবাস ফরিদপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার লাকার্তা গ্রামে)। পিতা-আবদুর রাজ্জাক সিকদার, মাতা-বেগম বেলাতেন নেসা। ভাই-বোন ঃ ছয় ভাই, দুই বোন। সিরাজ সিকদার দ্বিতীয়। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ১৯৫৯ সালে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক; বি. এম. কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক; ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে মেধা তালিকায় নবম হয়ে বি.এস-সি. ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। ১৯৬৭ সালেই কর্মজীবন শুরু। ১৯৬৭ সালেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারার প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকার মালিবাগে ‘মাও সেতুং চিন্তাধারা গবেষণা কেন্দ্র’ স্থাপনা। ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি ‘পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন’ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩ জুন ‘পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি’ নামে বিপ্লবী সংগঠন গঠন। মৃত্যুঃ ২ জানুয়ারি, ১৯৭৫ সালের বৃহস্পতিবার দিন। জীবনকালঃ ৩০ বছর ৩ মাস ৫ দিন। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগষ্ট, দিনাজপুর শহরে বি.এন.পি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্ম। ১৯৪৬ সালের ১৯ আগষ্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম জেফারসন (বিল) ক্লিনটনের জন্ম। ১৯৪৬ সালের ৮ ডিসেম্বর, কলকাতায় বাংলা ও হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের জন্ম। ১৯৫৯ সালে সত্যজিত রায়ের ‘অপুর সংসারের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে যাত্রা শুরু। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর, ইতালীর তুরিন শহরের কাছে অরবাসানো গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সোনিয়া মাইনো জন্মগ্রহণ করেন। রাজীব গান্ধীর স্ত্রী হিসাবে তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সোনিয়া মাইনোর পরিবর্তে সোনিয়া গান্ধী। ১৯৮৩ সালে তিনি ভারতীয় নাগরীকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন, ১৯৯৯ সালে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী নির্বাচিত হন। ২২-০৫-২০০৪ তারিখ থেকে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বিদেশিনী হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্তেও তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হননি। ড. মনমোহন সিংকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। আবার ২২-০৫-২০০৯ তারিখ থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্তেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি, এবারও ড. মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন।
১৯৪৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, টুঙ্গিপাড়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্ম। ১৯৪৯ সালের ১০ জুলাই, ভারতের ক্রিকেট খেলোয়ার সুনীল গাভাস্কারের জন্ম। দেখুন ভারতের ক্রিকেট ইতিহাস ১৯৩৫ সাল থেকে। ১৯৫০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, দিল্লিতে শাবানা আজমি জন্মগ্রহণ করেন। (বাবা বিখ্যাত উর্দু কবি কাইফি আজমি। মা আইপিটিএর অভিনেত্রী শৌকত।) তিনি অভিনয়ের ওপর একাডেমিক পড়াশোনাটা শেষ করেন ১৯৭২ সালে। ১২৭টির মতো ছবিতে অভিনয় করেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন বলেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ১০ জন অভিনেত্রীর মধ্যে তিনি একজন। অভিনেত্রী ও পরিচালক অপর্ণা সেনের মতে, শ্রেষ্ঠ পাঁচজনের একজন তিনি। শ্যাম বেনেগাল, যাঁর অনেক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন, তাঁর রায় এ রকম ঃ না, ভারতীয় চলচ্চিত্রাঙ্গনে তাঁর মতো অভিনেত্রীর পূর্বসূরি নেই। তুলনা টানার জন্য যেতে হবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, ইনগ্রিড থুলিন, লিভ উলম্যান বা মেরিল স্ট্রিপের কাছে। হ্যাঁ, শাবানা আজমির কথাই বলা হচ্ছে। ১৯৫২ সালের ২৫ নভেম্বর, লাহোরে পাকিস্তান ক্রিকেটের কিংবদন্তী তারকা ইমরান খানের জন্ম। ১৯৯২ সালে ৩৯ বছর বয়সে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপ জয়। ১৯৯৫ সালে ব্রিটিশ ধনকুবের জেমস গোল্ডস্মিথের মেয়ে জেমাইমা গোল্ডস্মিথকে বিয়ে করেন। ২০০৪ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এ দম্পতির দুই ছেলে আছে। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মায়ের মৃত্যু তাঁর জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। ইমরানের ভাষায়, ওই ঘটনাই তাঁকে মানুষের জন্য কাজ করতে এবং রাজনীতিতে নামতে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মসম্মান বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। ১৯৯৬ সালে ইমরান খান ‘পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ’ (পিটিআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের ১৬ মার্চ, নিউইয়র্কে স্টলম্যানের জন্ম। নিজের জীবনের প্রায় সবটুকু তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর গণমানুষের জন্য সফটওয়ার দর্শন, প্রচার ও বিকাশের জন্য। তাঁর কারণেই উন্মুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি বিকাশের সোপান। ১৯৫৩ সালের ২১ জুন, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের করাচিতে বেনজির ভুট্টো জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু-২৭-১২-২০০৭ তারিখ। রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় ভাষণ শেষে গাড়িতে ওঠার পরপরই সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং মুহূর্তের মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়। এতেই তিনি নিহত হন। ১৯৫৪ সালের ২৯ জানুয়ারি, আমেরিকার মিসিসিপির একটি দরিদ্র পরিবারে অপরাহ উইনফ্রের জন্ম। অপরাহ উইনফ্রে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী, ধনী ও কৃষাঙ্গ উপস্থাপক। তাঁর বিশ্বখ্যাতি স্বপরিচালিত শেষ হয়ে গেল দুনিয়া-মাতানো টক শো ‘দ্য অপরাহ উইনফ্রে শো’র জন্য। ১৯৮৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, শুরু হওয়া এ শো ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১-তে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ২৫-০৫-২০১১ তারিখ বুধবার তিনি পর্দা টেনে দিলেন দ্য অপরাহ উইনফ্রে অনুষ্ঠানটির ইতি টানেন একটি স্মরণীয় ও সংবেদনশীল বক্তৃতার মধ্য দিয়ে মানুষকে ভালোবাসো। ১৯৫৪ সালের ২৬ নভেম্বর, শ্রীলংকার জাফনায় তামিল টাইগার’স গেরিলা নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের জন্ম, শ্রীলংকার আর্মীর গুলিতে মৃত্যু-১৭-০৫-২০০৯ তারিখ। গত তিন দশকে ৭০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। ১৯৭২ সালে ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ অর্থাৎ আত্মগোপনে চলে যায়। ১৯৫৫ সালের ১ মে, কলকাতায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী কুমারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ২০ মে, ২০১১ শপথ নেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন রাজ্যের সিয়াটলে উইলিয়াম হেনরি গেটস থ্রি-বিল গেটসের জন্ম। এটি ১৯৬৮ সালের কথা, লেকসাইড স্কুলটি ছিল সেই বিরল প্রকৃতির নগণ্যসংখ্যক স্কুলগুলোর একটি যারা শিক্ষাথীদের প্রথম প্রজন্মের কমপিউটার শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিল। বিল গেটস নামেই বেশি পরিচিত। তিনি স্বপ্ন দেখেন স্বপ্ন দেখান। ১৯৫৫ সালে লন্ডনে ভার্চুয়াল সংস্কৃতির স্রষ্টা স্যার টিমোথি জন ‘টিম’ বার্নার্স-লি’র জন্ম। তিনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, সংক্ষেপে িি।ি এ তিনটি ডবিøউয়ের মাধ্যমেই ইন্টারনেট থেকে আমাদের মনিটরে ভেসে আসে কোটি কোটি পৃষ্ঠা। তিনি ওয়েবের জন্ম দিয়েই থেমে নেই।
১৯৫৭ সালের ১০ মার্চ, সৌদি আরবের রিয়াদে আল-কায়দা প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের জন্ম, মৃত্যু-০২-০৫-২০১১ তারিখ পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন। তাঁর লাশ সাগরে বাসিয়ে দিয়েছেন। এ অভিযানের আদ্যোপান্ত সরাসরি দেখলেন প্রেসিডেন্ট ওবামা বারাক হোসেন। তাঁর বাবা মুহাম্মদ বিন লাদেন ছিলেন ধনবান ব্যক্তি। তাঁর ৫৪ সন্তানের মধ্যে ওসামা বিন লাদেন ছিলেন ১৭তম। ১৯৬৯ সালে এক বিমান দুঘর্টনায় ওসামার বাবার মৃত্যু হয়। পৈতৃক সম্পত্তি পান আট কোটি ডলার মূল্যের। ওসামা ১৭ বছর বয়সে দূর সম্পর্কের এক সিরীয় বোনকে প্রথম বিয়ে করেন। তারপর আরও অন্তত চার নারীকে বিয়ে করেন। ওসামার ২৬ জন সন্তান রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বিন লাদেন ঃ আফগানিস্থানে শুরু, পাকিস্তানে শেষ। যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১১-০৯-২০০১ তারিখ আল-কায়েদার ভয়াবহ সেই বিমান হামলায় প্রায় তিন হাজারের বেশি লোক মারা যান। ১৯৫৮ সালের ১৬ আগষ্ট, মিশিগানের বে সিটিতে গায়িগা-অভিনেত্রী ও লেখিকা ম্যাডোনা লুইস ভ্যারোনিকা কিকোনির জন্ম। (নারী সংগীতজগতের তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। ফোর্বস সাময়িকীর ওয়েবসাইট জরিপে তিনি এক নম্বর আসন দখল করেন। ম্যাডোনা ২০০৬ সালের জুন থেকে ২০০৭ সালের মে পর্যন্ত সাত কোটি ২০ লাখ ডলার আয় করেছেন)। ১৯৫৮ সালের ২৯ আগষ্ট, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ছোট্ট শহর গ্যারিতে পপসম্রাট মাইকেল জোসেফ জ্যাকসন জন্মগ্রহণ করেন, অকালেই প্রস্থান মহাতারকার মৃত্যু-২৫-০৬-২০০৯ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসের শহরতলি হোমবাই হিলসের ভাড়াবাড়িতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁকে ইউসিএলএ মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। দুই ঘন্টা পর সেখান থেকে স্থানীয় সময় দুপুর দুইটা ২৬ মিনিটে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।
১৯৬১ সালের ৪ আগষ্ট, হাওয়াইয়ের হনলুলুতে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামার জন্ম। ওবামার পুরো নাম বারাক হোসাইন ওবামা জুনিয়র। ওবামা হচ্ছেন প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান, যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বড় কোনো দলের মনোনয়ন পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৬১ সালের ৩০ অক্টোবর, আর্জেন্টিনার প্রবাদ প্রতিম ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনার জন্ম। সে ১৯৮৬-র সেই মাঠ কাঁপানো তরুণ। ২০০৪ সালের ২০ এপ্রিল, ৪৩-বছর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে বর্তমানে ভাল, ফুটবলে যাদু দেখানোর মত মাদক নেয়ার ইতিহাস তাঁর সুদীর্ঘ। ১৯৬২ সালে দুঃসাহসী অস্ট্রেলীয় ন্যাচারলিষ্ট ক্রকোডাইল হান্টার স্টিভ আরউইনের জন্ম, মৃত্যু-০৪-০৯-২০০৬ তারিখ, পোর্ট ডগলাসের কাছে একটি আন্ডারওয়াটার প্রামাণ্য চিত্র চলচ্চিত্রায়নের সময় তিনি নিহত হন। ১৯৬৫ সালের ২ জুন, সিডনিতে ক্রিকেট স্টার স্টিভ ওয়াহ’র জন্ম, (মহানায়কের বিদায়)-২০০৪ সালে। ১৯৭১ সালের ৩ জুলাই, অস্ট্রেলিয়ার টাউন্সভিল, কুইনসল্যান্ড-এ সাংবাদিক, প্রোগ্রামার এবং হ্যাকার (লেখাপড়াঃ পদার্থবিদ্যা ও গণিত) ও উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক জুলিয়ান পল অ্যাসাঞ্জের জন্ম। ১৯৭৩ সালের ২১ আগষ্ট, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোয় সের্গেই মিখাইলোভিচ ব্রিনের জন্ম। ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে ল্যারি পেইজ বা লরেন্স ‘ল্যারি’ পেইজের জন্ম। ল্যারি পেইজ ও সের্গেই ব্রিনের প্রথম দেখা হয় ১৯৯৫ সালে, সেখান থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব। সের্গেই ব্রিন ও ল্যারি পেইজ এরা দুজনে তথ্যের বাতিঘর। ১৯৮৪ সালের ১৪ মে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক বিপ্লবের রুপকার মার্ক এলিয়ট জাকারবার্গের জন্ম। তিনি ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন গেম ও যোগাযোগের প্রোগ্রাম নিয়ে। ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ টাইম ম্যাগাজিনের জরিপে এ বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রæয়ারি, ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাকাল। ২৬ বছরেই বিশ্বসেরা। ১৯৮৪ সালের ৭ জুলাই, বি-বাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মানিকপুর গ্রামে বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট খেলোয়ার মোহাম্মদ আশরাফুলের জন্ম। ১৯৮৭ সালের ২৪ জুন, আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ফুটবলার লিওনেল আন্দ্রেস মেসির জন্ম। ফুটবল বিশ্বে তিনি মেসি নামে পরিচিত। ১৯৮৯ সালের ২২ ফেব্রæয়ারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলেয়া সবুরের জন্ম। ড. আলেয়া সবুর ১৮ বছর বয়সে বিশ্বের প্রথম অধ্যাপক। ১৯৯৬ সালের ১২ জুলাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিমালয় পর্বতারোহী জর্ডান রোমেরোর জন্ম। ২০১০ সালের ২২ মে, শনিবার সকালে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ এভারেষ্ট জয়ী হিসেবে রেকর্ড গড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বছর বয়সী কিশোর জর্ডান রোমেরো। সাগরপৃষ্ঠ থেকে ২৯,০৩৫ ফুট (আট হাজার ৮৫০ মিটার) উঁচু বিশ্বের এ সবোচ্চ পর্বতচুড়ায় আরোহণ করে জর্ডান। তার সঙ্গে বাবা পল রোমেরো, বাবার বান্ধবী কারেন ল্যান্ডগ্রেন ও তিনজন শেরপা গাইড এভারেষ্টের চুড়ায় পৌঁছান।